
জাকির আহমদ খান কামাল
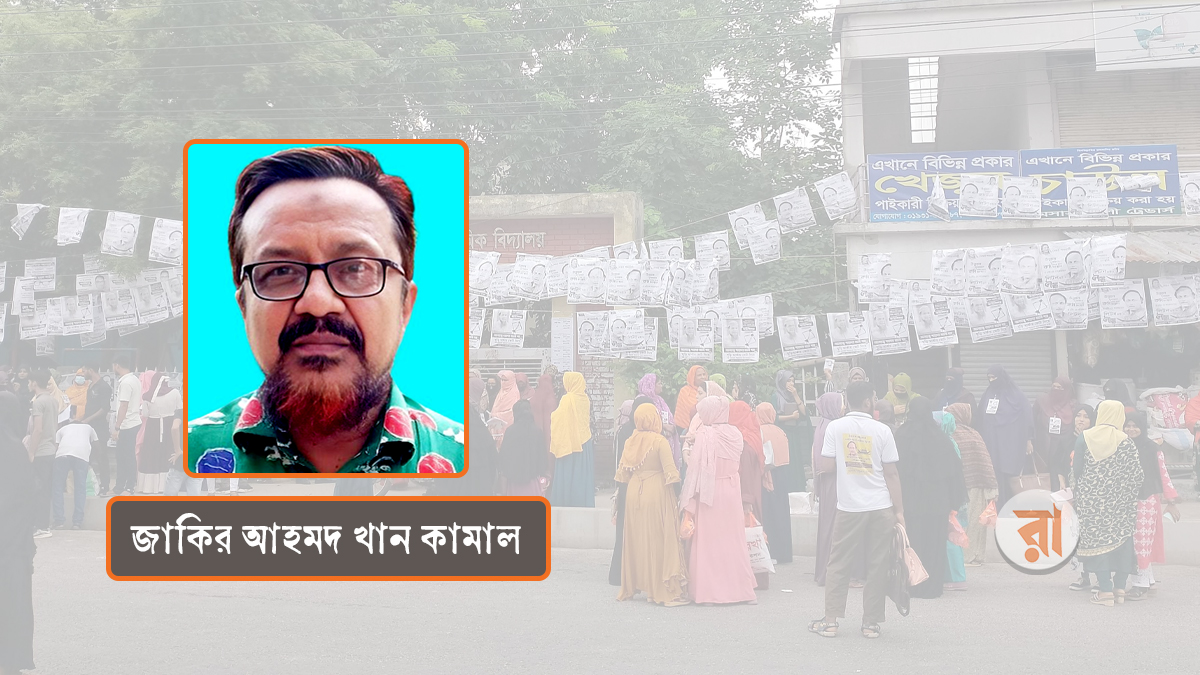
জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস— এই ধারণাটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের সংবিধানেও বলা হয়েছে, ‘সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’। কিন্তু বাস্তবে জনগণ কার? এ প্রশ্নটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক জনশুমারিতে দেশের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১৭ থেকে সাড়ে ১৭ কোটি ধরা হয়েছে। তবে প্রবাসী শ্রমিক, বিদেশে বসবাসকারীদের যোগ করলে এই সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি বা তার চেয়ে একটু বেশি। এখানেই রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি সুবিধাজনক ফাঁক তৈরি হয়।
সহজে স্মরণযোগ্য ও প্রভাবসৃষ্টিকারী সংখ্যা হিসেবে ‘১৮ কোটি মানুষ’ ব্যবহার করা হয়, যা জনসংখ্যার একটি প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য ধারণা তৈরি করা হয়। কিন্তু বাস্তবতায় রাজনৈতিক দলের দাবি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি মূলত প্রতীকী ভাষা— জনসাধারণের প্রতি তাদের নৈতিক অধিকার, দায়িত্ববোধ ও সমর্থন লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।
যেকোনো রাজনৈতিক দলই চায় জনগণের সম্পূর্ণ অংশ তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক। তাই ‘১৮ কোটি মানুষ আমাদের’— এ কথাটি প্রকৃত সমর্থকের সংখ্যা নয়, বরং প্রতীকী মালিকানার ঘোষণা। তবে এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রশ্ন সামনে আসে— জনগণের নামে দাবি করা হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলো কি সত্যিই সব মানুষের চাহিদা, অধিকার ও সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?
যদি প্রতিটি দলই নিজেদের সর্বজনস্বীকৃত বলে বিবেচনা করে, তবে গণতান্ত্রিক আচরণ, বিরোধীপক্ষের ভূমিকা, বহুমতের প্রতি সম্মান— এসব মৌলিক নীতি কোথায় থাকে?
জনসংখ্যাগত বাস্তবতা ও রাজনৈতিক দাবি— দুইয়ের পার্থক্য বোঝা তাই জরুরি। কিন্তু রাজনৈতিক ভাষণে এটিকে ‘আমাদের সব মানুষ’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় জনআবেগ সৃষ্টি ও সমর্থন জোরালো করতে। একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব হলো তথ্যভিত্তিক অবস্থান বোঝা এবং রাজনৈতিক বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা।
পরিশেষে বলা যায়, দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা পরিসংখ্যান দ্বারা নির্ধারিত হয়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় নয়। আর জনগণ কার— এ দাবি নয়, কাজের মাধ্যমেই প্রমাণিত হওয়া উচিত।
রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই দাবি করে, জনগণ তাদের পক্ষে। নির্বাচনের সময় তারা জনগণের কাছে গিয়ে তাদের ভোট চায় এবং নির্বাচিত হওয়ার পর তারা জনগণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক সময়ই জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
বাস্তবতা বিবেচনায় তাই জনগণ আসলে কার— এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, অন্যদিকে জনগণও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময়ই ক্ষমতাসীন দল জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিরোধী দলগুলোও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে জনগণের কাছে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তারা সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়।
এ পরিস্থিতিতে জনগণ আসলে কার— এ প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। জনগণ কি রাজনৈতিক দলগুলোর হাতের পুতুল? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম?
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে শত সহস্র তাজা প্রাণের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্বাচনহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। সেই সুবাদে আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেছে নির্বাচন কমিশন।
চূড়ান্ত হিসাবে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৯০৭ জন, নারী ভোটার ছয় কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন এক হাজার ২৩৪ জন।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের গণভোটও হবে।
আগামী সংসদ নির্বাচনে সরকারের কাছে জনপ্রত্যাশা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর সুষ্ঠু নির্বাচন পরিবেশ তৈরি করা, যা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে। জনগণ সঠিকভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
তবে এটি স্পষ্ট, জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে সঠিকভাবে। তবেই জনগণ হবে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস এবং দেশ হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও কলাম লেখক
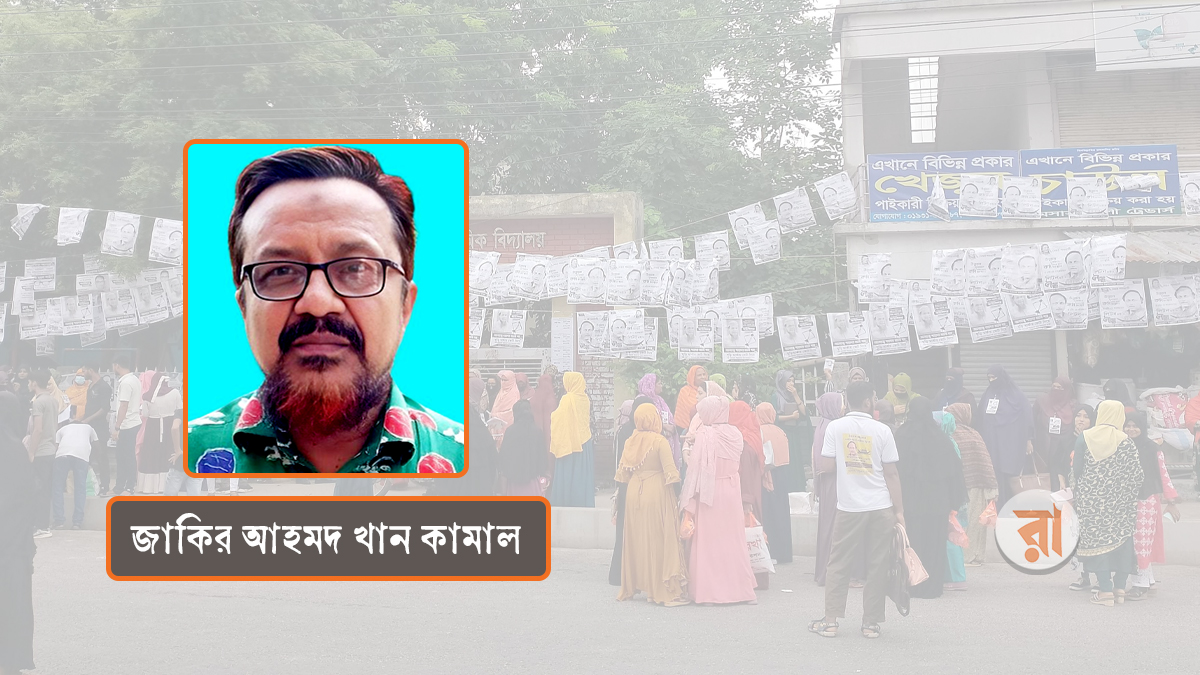
জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস— এই ধারণাটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশের সংবিধানেও বলা হয়েছে, ‘সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’। কিন্তু বাস্তবে জনগণ কার? এ প্রশ্নটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক জনশুমারিতে দেশের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ১৭ থেকে সাড়ে ১৭ কোটি ধরা হয়েছে। তবে প্রবাসী শ্রমিক, বিদেশে বসবাসকারীদের যোগ করলে এই সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি বা তার চেয়ে একটু বেশি। এখানেই রাজনৈতিক বক্তব্যের একটি সুবিধাজনক ফাঁক তৈরি হয়।
সহজে স্মরণযোগ্য ও প্রভাবসৃষ্টিকারী সংখ্যা হিসেবে ‘১৮ কোটি মানুষ’ ব্যবহার করা হয়, যা জনসংখ্যার একটি প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য ধারণা তৈরি করা হয়। কিন্তু বাস্তবতায় রাজনৈতিক দলের দাবি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি মূলত প্রতীকী ভাষা— জনসাধারণের প্রতি তাদের নৈতিক অধিকার, দায়িত্ববোধ ও সমর্থন লাভের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে।
যেকোনো রাজনৈতিক দলই চায় জনগণের সম্পূর্ণ অংশ তাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক। তাই ‘১৮ কোটি মানুষ আমাদের’— এ কথাটি প্রকৃত সমর্থকের সংখ্যা নয়, বরং প্রতীকী মালিকানার ঘোষণা। তবে এর মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক প্রশ্ন সামনে আসে— জনগণের নামে দাবি করা হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক দলগুলো কি সত্যিই সব মানুষের চাহিদা, অধিকার ও সমস্যার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে?
যদি প্রতিটি দলই নিজেদের সর্বজনস্বীকৃত বলে বিবেচনা করে, তবে গণতান্ত্রিক আচরণ, বিরোধীপক্ষের ভূমিকা, বহুমতের প্রতি সম্মান— এসব মৌলিক নীতি কোথায় থাকে?
জনসংখ্যাগত বাস্তবতা ও রাজনৈতিক দাবি— দুইয়ের পার্থক্য বোঝা তাই জরুরি। কিন্তু রাজনৈতিক ভাষণে এটিকে ‘আমাদের সব মানুষ’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় জনআবেগ সৃষ্টি ও সমর্থন জোরালো করতে। একজন সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব হলো তথ্যভিত্তিক অবস্থান বোঝা এবং রাজনৈতিক বক্তব্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করা।
পরিশেষে বলা যায়, দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা পরিসংখ্যান দ্বারা নির্ধারিত হয়, রাজনৈতিক বক্তৃতায় নয়। আর জনগণ কার— এ দাবি নয়, কাজের মাধ্যমেই প্রমাণিত হওয়া উচিত।
রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই দাবি করে, জনগণ তাদের পক্ষে। নির্বাচনের সময় তারা জনগণের কাছে গিয়ে তাদের ভোট চায় এবং নির্বাচিত হওয়ার পর তারা জনগণের সেবা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক সময়ই জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
বাস্তবতা বিবেচনায় তাই জনগণ আসলে কার— এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। একদিকে যেমন রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করে, অন্যদিকে জনগণও নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ কী, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময়ই ক্ষমতাসীন দল জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। বিরোধী দলগুলোও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে জনগণের কাছে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে তারা সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়।
এ পরিস্থিতিতে জনগণ আসলে কার— এ প্রশ্নটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। জনগণ কি রাজনৈতিক দলগুলোর হাতের পুতুল? নাকি তারা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম?
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তবে শত সহস্র তাজা প্রাণের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্বাচনহীনতার সংস্কৃতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি। সেই সুবাদে আগামী ফেব্রুয়ারিতে হতে যাচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। গত ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করেছে নির্বাচন কমিশন।
চূড়ান্ত হিসাবে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৯০৭ জন, নারী ভোটার ছয় কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন। এর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন এক হাজার ২৩৪ জন।
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা করেছেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। একই দিনে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের গণভোটও হবে।
আগামী সংসদ নির্বাচনে সরকারের কাছে জনপ্রত্যাশা একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও উৎসবমুখর সুষ্ঠু নির্বাচন পরিবেশ তৈরি করা, যা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করবে। জনগণ সঠিকভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
তবে এটি স্পষ্ট, জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে সঠিকভাবে। তবেই জনগণ হবে প্রকৃত ক্ষমতার উৎস এবং দেশ হবে প্রকৃত গণতান্ত্রিক।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও কলাম লেখক
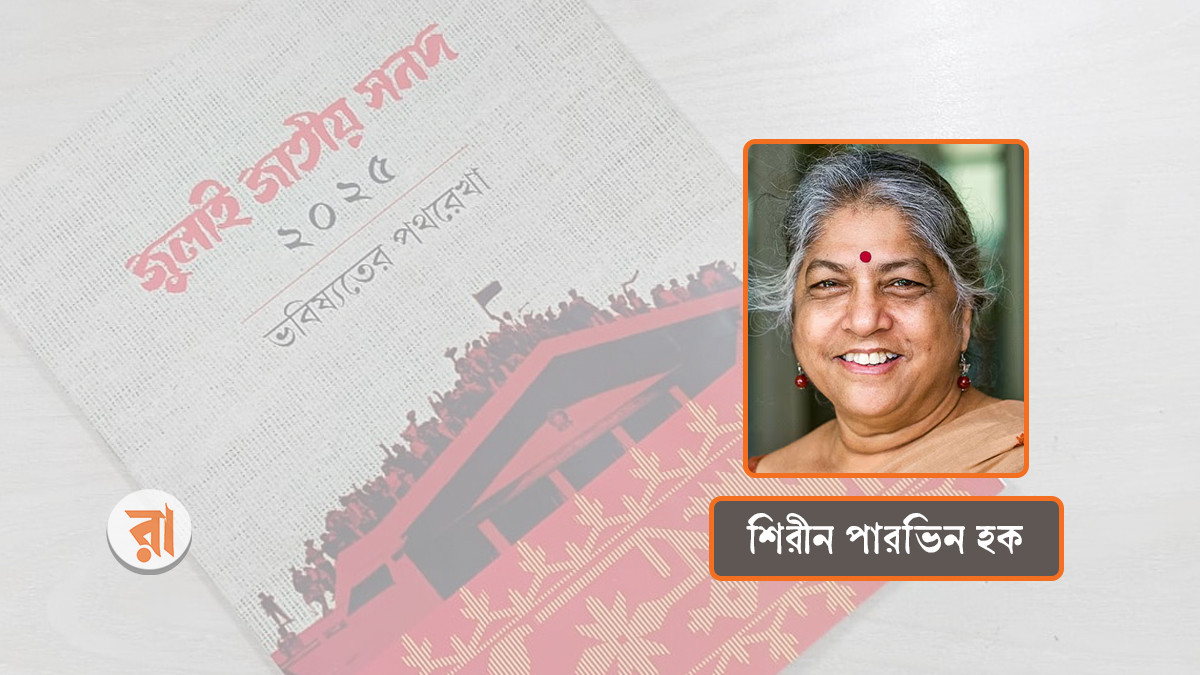
একটি কমিশন আমাদের সময় দেয়নি— সংবিধান কমিশন। আমি জানি না কেন তারা সময় দেয়নি। হয়তো তাদের ধারণা ছিল, সংবিধান সংস্কারে নারীদের আবার কী বলার থাকতে পারে! তারা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না-ই করতে পারতেন, কিন্তু সময় দেওয়াটা ছিল শোভন আচরণের অংশ। সেই সৌজন্যটুকু আমরা পাইনি।
১২ দিন আগে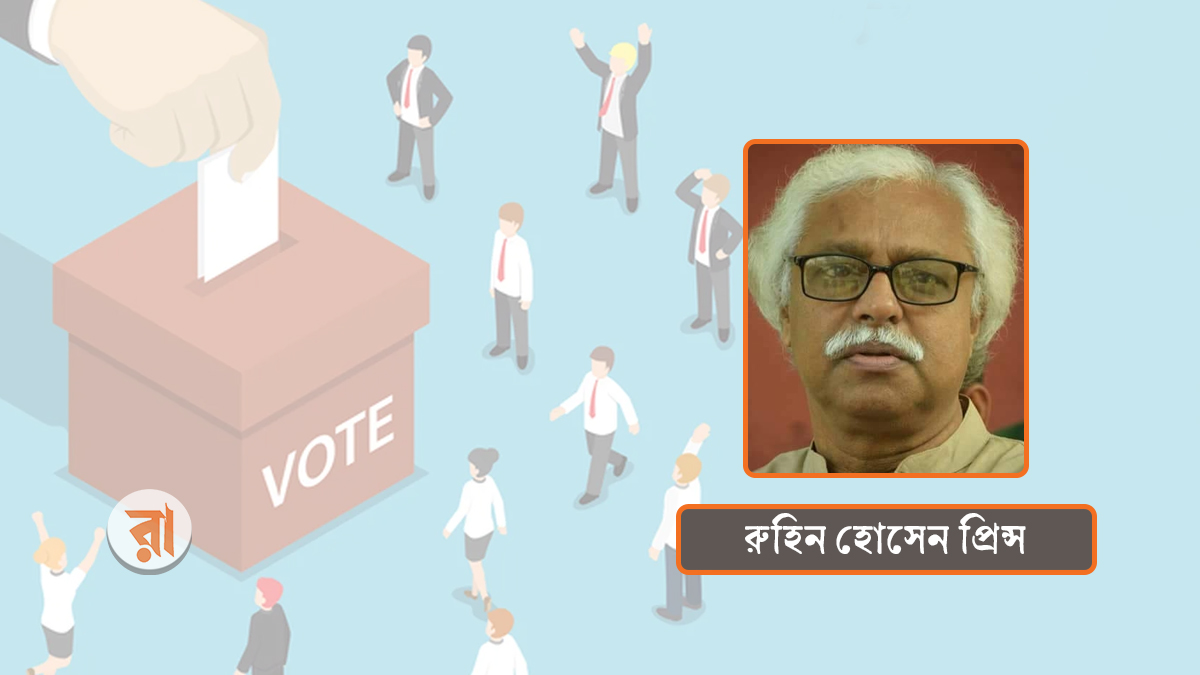
এবারের নির্বাচনে সাম্প্রদায়িক প্রচার-প্রচারণা যে ভয়াবহ রূপ লাভ করবে, সেটা এরই মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছে। সরকার নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে আচরণবিধি ঠিক রেখে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার সার্বিক দায়-দায়িত্ব নিলে অনেক কিছু রোধ করা যেত।
১২ দিন আগে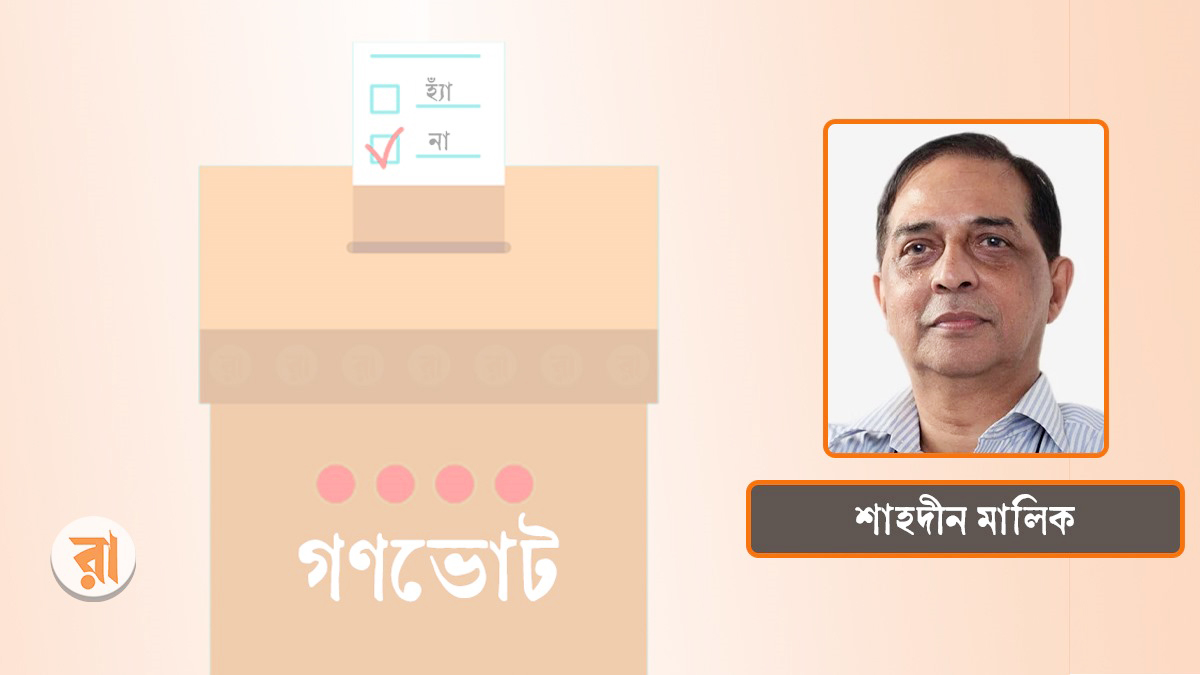
প্রকৃত অর্থে এগুলো একটি রাজনৈতিক কাঠামোর প্রশ্ন। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা দ্রব্যমূল্যের মতো বিষয় নয়। তেমন হলে সাধারণ মানুষের স্বার্থ যুক্ত থাকত। কিন্তু এটি উচ্চমধ্যবিত্তের প্রাতিষ্ঠানিক ধারণা। কীভাবে সাধারণ মানুষ এতে ভোট দিবে পক্ষে-বিপক্ষে, সেটি আমিও বুঝতে পারছি না।
২২ দিন আগে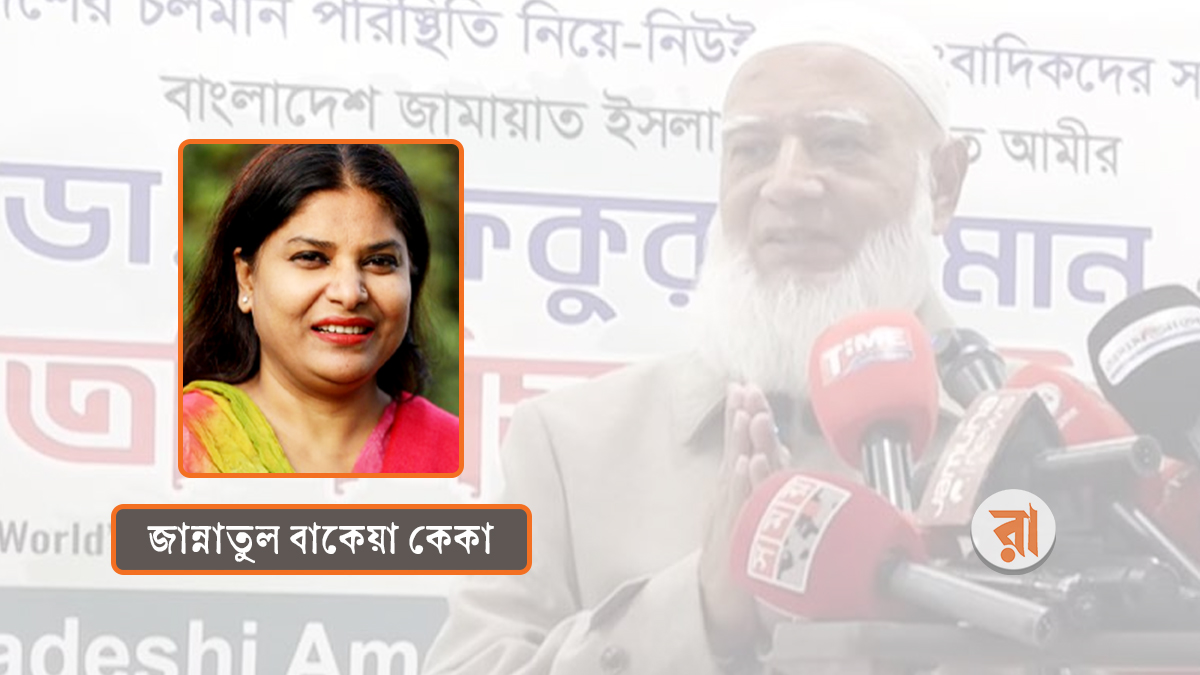
নেটিজেনদের অনেকেই বলছেন, ভোটকে সামনে রেখে এটা জামায়াতের একটা চাল। কারণ ক্ষমা চাওয়ার দাবি তো দীর্ঘ দিনের। তাহলে মার্কিন মুল্লুকে গিয়ে কেন ক্ষমা চাইতে হলো। দেশের বাইরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক ও সমালোচনা শুরু হয়েছে, বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হচ্ছে।
২৪ অক্টোবর ২০২৫