
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক

গত দেড় দশকে শিক্ষা খাতে অপরিসীম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, একদলীয় সাংস্কৃতিক বয়ান নির্মাণসহ, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সুবিধাভোগীদের এক সাগরে পরিণত হয়েছিল। যার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ঘন ঘন অপরিকল্পিতভাবে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট নানা প্রকল্পের অর্থায়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পরিবর্তন এবং সংশ্লিষট লুটপাটের মধ্যে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে শিক্ষানীতির প্রতিফলন ছিল না, ছিল না যুগোপযোগী শিক্ষা নীতিও। এছাড়া ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, বাণিজ্য ও লুট-পাটের আখড়ায় পরিণত ছিল শিক্ষাখাত। এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার সাথে উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল ও একমুখী ছিল।
দেশে একটি যথার্থ যুগোপযুগী শিক্ষানীতি এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন না থাকার মূল্য এখন চুকাতে হচ্ছে দেশের শিক্ষাখাতকে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় শিক্ষাখাতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যয়কারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দুর্বলতাকে। অর্থাৎ শিক্ষায় রাষ্ট্রের বিনিয়োগ অপ্রতুল এবং তা আত্মঘাতী। এমন একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা যদি গত একবছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে পরিস্থিতি উত্তরণে কোনো সুদূরপ্রসারী দর্শনগত পরিবর্তন বা কাঠামোগত বদলের ন্যূনতম চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি। যা হয়েছে, তা এক ধরনের রঙ বদলের খেলা। একদলের (আওয়ামী) প্রশাসক বা মুখ বদলে প্রধানত অন্য যে দলের প্রভাব (জামাত/বিএনপি) বেশি এমন প্রশাসক বসানো। ফলে শিক্ষাখাত ভয়াবহ এক বিস্ফোরম্মুখ পরস্থিতিতে ধুকছে!
অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষাখাতের খেরোখাতা: অর্জন?
শিক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে নেটওয়ার্ক গত এক বছরে চেষ্টা কিছু কম করেনি। প্রথমত, গত আগস্টে আমরা কেমন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমন প্রশাসক চাই তা তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা, পরবর্তী শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম যে, অভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসকরা হবেন সৎ, বিদ্বান ও দল নিরপেক্ষ, হবেন একেকজন স্বপ্নদ্রষ্টা। সেরকম তো কিছু ঘটেইনি, আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে শিক্ষার্থী - শিক্ষকদের হাতে শুরু হওয়া গণ-অভ্যুত্থানের সরকার শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের কল্যাণকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। শিক্ষাখাতের মূল কাঠামোতে তেমন কোনো মূলগত বা গুণগত পরিবর্তনও করেনি। উল্টো অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা উপদেষ্টাদের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের তালিকা বেশ লম্বা।
প্রথমত, অভ্যুত্থানের পরপরই অল্প সংখ্যক সংগবদ্ধ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অটোপাসের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির উৎস এবং এই সরকারের অন্যতম ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই ঘটনায় সংঘবন্ধ চাপের কাছে নতিস্বীকারে মন্ত্রণালয়ের প্রধান ব্যক্তির অতি নমনীয়তা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের ইতিহাসে একটি ক্ষতিকর উদাহরণ তৈরি করে।
দ্বিতীয়ত, ২০২৪ এর আগস্টে ২০২৩ এ চালু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম বাতিল করে ২০১২ এর শিক্ষাক্রমকেই পরিমার্জন করে ২০২৫ এর জন্য নতুন বই আনার সিদ্ধান্ত হয় যা বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার কমিটি গঠিত হয় এবং তা ব্যাপক সমালোচনা মধ্যে পড়ে। যৌক্তিক সমালোচনা করা যেত যে কেন কমিটিতে শিক্ষা বিষয়ক গবেষক বা আলেমদের (যদিও কওমী মাদ্রাসার বই এই কমিটির কার্যপরিধিতে ছিল না) রাখা হয়নি। কিন্তু কমিটির দুজন সদস্যকে নিয়ে ইচ্ছাকৃত ঘৃণা ও ‘ইসলামবিদ্বেষী’ বলে বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলামীর হুমকিতে পুরো কমিটিই বাতিল করেন তখনকার শিক্ষা উপদেষ্টা। সরকারের এই আচরণ এসব বিদ্বেষপূর্ণ হস্তক্ষেপকারীদের সাহস যুগিয়ে সাধারণ নাগরিকদের যে বার্তা দেয় তা হলো, একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠির চাপে সরকার নতজানু থাকছে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসকরা নিরাপত্তাহীনতার ভয় দেখিয়ে ওই একই ধর্মীয় গোষ্ঠির কথা পালনে বাধ্য করেন শিক্ষার্থীদের। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাত্র ১০-১৫ জনের চাপে পড়ে) প্রশাসন নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়নি বলে একটি আলোচনা সভা বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষার্থীরা। তাহলে আর এত দামে কেনা জুলাই অভ্যুত্থানের কোন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা হলো?
তৃতীয়ত, গত ১৬ বছরে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, সর্বাগ্রে তাদের দলীয় পরিচয় এবং আনুগত্য দেখিয়ে তখনকার সরকারের ক্ষমতাবলে হয়ে উঠেছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচারী। সেই সাথে অনুগতদের নিয়ে একটি সুবিধাভোগী বলয় তৈরি করেছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের পরপরই তাদের ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দের আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট তৈরি হয়েছিল বলেই দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদত্যাগ করেছিলেন বা শিক্ষার্থীদের চাপে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হয়েছিল এবং অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত তৎপর না হওয়ায়, ব্যক্তিপর্যায়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের হাতে শিক্ষক হেনস্থার ঘটনা ঘটে যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এসব ঘটনাকে স্বার্থান্বেষীদের কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে।
চতুর্থত, পরিতাপের বিষয়, অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী জমায়েত থেকে অপছন্দের গোষ্ঠী ও দলের বিরুদ্ধে কেবল হিংসাত্মক কথাবার্তাই বলা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে সেসব মানুষের ওপর হামলাও চালানো হয়েছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গবদ্ধ হিংস্রতায় নিহত হয়েছেন তিনজন মানুষ। এইসব ঘৃণ্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার এখনো হয় নাই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আক্রমণকারীর পুণর্বাসনও হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও দপ্তরে ছোট ছোট অজস্র হিংস্রতার ঘটনা ঘটেই চলেছে। মাজার, মন্দির, শিল্প-স্থাপনা ভাংচুর থেকে শুরু করে বাউল ও আহমেদিয়াদের ওপরও আক্রমণ হয়েছে। নানা স্থাপনা, ভাস্কর্য এবং শিল্পকর্ম ভাঙা হয়েছে যার সাথে অভ্যুত্থানের শক্তি শিক্ষার্থীদের নাম জড়িয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালগুলোর প্রশাসকদের পদগুলিতে (উপচার্য, উপ উপাচার্য, কোষাধক্ষ্য, প্রভোস্ট, ডিন, প্রক্টর ইত্যাদি) যাদেরকে বসানো হয়েছে তাদের সম্পর্কে উপদেষ্টা নিজেই বলেছেন যে এদের বেশির ভাগই ‘মৃদু বিএনপি’ বা আসলে জামাত-বিএনপি। শিক্ষক নেটওয়ার্ক অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছে যে সেই একই দলীয় পরিচয় দিয়েই প্রশাসক নিয়োগ হচ্ছে যা অভ্যুত্থানের আকাংক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব দলীয় শিক্ষকরা দলীয় সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক উন্নতির কথা ভাবছেন না। বঞ্চিত ক্যাটাগরিতে এখন পদ-পদবী দখল এবং পদোন্নতির মহা-উৎসব শুরু হয়েছে।
ষষ্ঠত, রাস্তায় ও পর্যটন অঞ্চলেই শুধু নয় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, বাচিক ও শারীরিক, সাইবার নিগ্রহ এবং চরম হেনস্তা চলেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্রী. যাদের অনেকেই জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারির মুখ, তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সাথে শিক্ষকদের দ্বারা সাইবার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন সেই শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী দ্বারা ভাষিক যৌন নিপীড়নের শিকার শিক্ষার্থী সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন অপরাধীর সহযোগীদের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয় তার পাশে দাঁড়ায়নি। অভিযোগ তদন্তের কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি। এই অভিযোগটি এমনকি যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলেও পৌছায়নি। নারীর অধিকার বা হিস্যা আদায়ের দাবীতে রাস্তায় আন্দোলনকারী, অভ্যুত্থানের সামনের মুখ নরসিংদীর কলেজ শিক্ষিকা নাদিরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে হেফাজতের হেট ক্যাম্পেইনের মুখে আবারো পিছু হটেছে শিক্ষা মন্ত্রনালয় তিন বার বদলি করেছে নাদিরাকে। উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সামনে বারবার এই ধরনের আত্মসমর্পন এই প্রশ্ন সামনে আনে যে হেফাজতে ইসলামীসহ আরো কিছু ধর্মভিত্তিক দল (যারা অভ্যুত্থানের মধ্যেও হাসিনার পক্ষে ছিল) তারা এখনো নারী অভ্যুত্থানকারীদের বিপদে ফেলছে। কোথায় তাহলে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার, যেটা ছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের পর আমাদের প্রধানতম চাওয়া?
সপ্তমত, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানাবিধ ফি’র নামে শিক্ষার্থীদের শোষণ ও বঞ্চনা শেষ হয়নি। ইউআইইউ এর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে আবার পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে যা সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষককে অভ্যত্থানে যোগ দেবার ‘অপরাধে’ হয়রানি ও চাকুরিচ্যুত করেছে প্রশাসন। বেতনের দাবীতে জড়ো হওয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে পুলিশ। শ্রমিকদের ওপর হামলা করেছে এর কোনো প্রতিবাদ অভ্যুত্থানকারী শিক্ষার্থীদের মূল শক্তির কাছ থেকে আসেনি যা ভয়াবহভাবে হতাশার। বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত বা পুলিশে এক বছর প্রশিক্ষণের পরেও যাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে কোনো যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে, তাদের পক্ষেও দাড়ায়নি বৈষম্যবিরোধীরা।
অষ্টমত, আওয়ামী আমলে সরকারীভাবে জেলায় জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হলেও সংখ্যার তুলনায় মানের সঙ্কট রয়েই গেছে। জনবল ও সম্পদের অভাব এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগোতে দিচ্ছে না। গবেষণায় বরাদ্দ যৎসামান্য হওয়ায় সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ‘আন্ডারগ্র্যাডকলেজ’-এর ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, নতুন জ্ঞান সৃজনের কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পালন করতে পারছে না। কুয়েটের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির চাপে হামলা-আক্রমণ আমাদের সামনে নিয়ে আসে তথাকথিত ‘রাজনীতিহীন’ ক্যাম্পাসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির গভীর শেকড়।
নবমত, স্বায়ত্বশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির দলীয় লেজুড়বৃত্তির ফলে গত কয়েকদশক ধরে শিক্ষক নিয়োগ বা ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনে সবকিছুর উর্ধ্বে দলীয় বিবেচনা প্রধান হয়ে উঠেছিলো। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের পর একটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক/ছাত্র সংঙ্গঠনের প্রভাব না থাকলেও ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে এক ভিন্ন রকমের নীতি পুলিশী (মরাল পুলিশিং) শুরু হয়েছে, যার প্রধান শিকার নারী শিক্ষার্থী ও ভিন্ন মতের শিক্ষকরা যা আশংকাজনক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইচ্ছামতো নাম বদলের সংস্কৃতি। খুলনা ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-বদলকাণ্ডে বিপদজনক জনতুষ্টিবাদী ঝোঁক, শিক্ষাবিমুখতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায়।
দশমত, ১৯৭৩-এর আদেশের বাইরের নানা প্রকৃতির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সব ক্ষমতা উপাচার্যের নিকট কেন্দ্রীভূত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রকমের আইন দিয়ে চলছে, গণতান্ত্রিক উপাদানের ঘাটতি আছে এবং আছে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীভূত প্রশাসনব্যবস্থা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ প্রচুর। পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি গত ১ বছরে দেখা যায়নি। পুরনো ব্যবস্থা নতুন চেহারার নিচে টিকে আছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা আত্মগোপনে যাবার পর অন্যান্য শিক্ষকদের দলবাজি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর এই ধরনের প্রবণতা ব্যবহার করে প্রশাসন আরো কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে।
সঙ্কট নির্দিষ্টকরণ
আমরা তাহলে এখন কী চাই? এই সংকটজনক অবস্থার পরিবর্তন চাই। তাই সংকটগুলো চিহ্নিত করেছিলাম ১ বছর আগে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই সংকট এখনো রয়ে গিয়েছে। আমরা কোথাও অগ্রগতির চিহ্ন দেখছি না।
শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ শিক্ষায় বরাদ্দের হারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। একদিকে শিক্ষা গবেষণার তহবিলের বরাদ্দ নেই, নেই উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা, অন্যদিকে হীন দলীয় রাজনীতি গবেষণামনষ্ক শিক্ষকদের জন্য নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যেক্ষেত্রে গবেষণাবিমুখ ও রাজনীতিপ্রবণ শিক্ষকদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ উন্নয়নের নানান উপায়।
সরকারি কর্তৃত্ব আওয়ামী লীগ পালানোর পর শিক্ষার্থীদের গণরুম গেস্টরুম উঠে যাওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছুটা সুবাতাস বইলেও শিক্ষকদের জন্য পরিস্থিতি খুব বদলায়নি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউজিসির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় যদিও এরা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা কার্যক্রম এবং সনদ প্রদানের অনুমোদন পেয়েছে। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালগুলোর পক্ষ থেকে এবং শিক্ষকদের নানান বৈষম্যের শিকার হতে হয় এখানে।
নয়া উদারবাদী নীতি ও ইউজিসি মানোন্নয়নের নামে সর্বজনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করতে ও সরকারি বরাদ্দ কমাতে নীতিগত চাপ প্রয়োগ করছে। বিভাগগুলোতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতার বাইরে, তেমন কোন অর্থ বরাদ্দ না দিয়ে অন্যান্য ব্যয় স্ব স্ব বিভাগকে বহন করতে বলা হয়, এতে করে বিভাগগুলোকে ইভিনিং বা উইকএন্ড প্রোগ্রামের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে শিক্ষকদের শিক্ষার মানের দিকে খেয়াল করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে পারলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র হারিয়ে ওই সব প্রোগ্রমের শিক্ষার্থীদের গুনতে হচ্ছে বিশাল শিক্ষা ব্যয়। একই সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাবি অথচ দরিদ্রদের পড়ার সুযোগ ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে, শিক্ষা পণ্যায়িত হয়ে উঠেছে। গবেষণার বরাদ্দ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা হচ্ছে না।
স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার: তিয়াত্তরের আদেশ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করলেও মূলত দলীয় রাজনীতি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পাস সরকারদলীয় শিক্ষকনেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানভিত্তিক না হয়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক করে তুলেছিলো সে পরিস্থিতি এখনো বিদ্যমান আছে।
ভর্তি ও নিয়োগ পাঠদান ও গবেষণা: নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অকার্যকর গুচ্ছ পদ্ধতিসহ নানান নিরীক্ষায় কিছু শিক্ষকের পকেটভারি হলেও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের হয়রানি বাড়ে একদিকে, অন্যদিকে এমসিকিউনির্ভর ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়-উপযোগী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী খুঁজে না পাওয়াও ক্লাসরুমের গড় মান পড়ে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো দলীয় বিবেচনায় ‘ভোটার’ নিয়োগের প্রবণতায় মেধা বা যোগ্যতা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আবার শিক্ষার্থীদের পিএইচডি এমফিল গবেষণার জন্য সুষ্ঠু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অনুপস্থিতিতে গবেষণা ও পিএইচডির মানও নিশ্চিত করা যায় নাই।
শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ছাত্র রাজনীতি: পাবলিক বিশ্বববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে বসবাসের ও অধ্যয়নের সুব্যবস্থা নেই। জুলাই এর পর একদলের মাস্তানতন্ত্র উচ্ছেদ হলেও বিদ্যায়তনিক গণতন্ত্র এখনো অনেক দূরে। ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ পরিচয়ে এক নতুন আধিপত্যকামী শক্তির দেখা মিলছে যাদের দ্বারা প্রান্তিক মত এবং কণ্ঠস্বর দমন-পীড়নের স্বীকার হচ্ছে।।
উচ্চ টিউশন ফি ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমরূপ বা হোমোজেনাস নয়। তাদের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। অল্প কয়েকটির মান উন্নত (যদিও সেখানে টিউশন ফি অত্যন্ত উচ্চ) হলেও বেশিরভাগের মান সাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত মুনাফামুখী, এবং এখানে গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। প্রবল সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন করে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শুধু ইংরেজি রেখেছে, যা শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।
সমাধানপ্রস্তাব
শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ: শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে রাষ্ট্রকে। আগামী ৪ (চার) বছরের মধ্যে শিক্ষায় জিডিপির শতকরা ০৭ (সাত) ভাগ বরাদ্দে পৌছানোর লক্ষমাত্রা নিয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই বরাদ্দের সুনিদ্দিষ্ট অংশ গবেষণায় এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হতে হবে।
প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও চাকরির সুবিধা দিতে হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের দায়িত্বে থাকা এনসিটিবিকে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।
শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চিন্তার স্বাধীনতা, বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা, প্রশ্ন ও মত প্রকাশের পরিসর এবং বিশ্লেষণের বিস্তারের ক্ষেত্র নিয়ে তৈরী হবে এমন চাই।
ইউজিসির কৌশলপত্র ও নয়া উদারবাদী নীতি: নব্যউদারবাদী মতাদর্শের আলোকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রণীত বাণিজ্যিকীকরণের নীতি ও পরিচালনার নানা পরামর্শ থেকে সরে আসতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাকে দরিদ্র মানুষদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। বছর বছর ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাড়ানো কিংবা নানান নামে ভর্তির সময় অর্থ আদায় বন্ধ করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আইন ও নীতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা গুরুত্বপূর্ণ তবে সকল স্তরে দলীয় আধিপত্যবিস্তারের রাজনীতি বন্ধ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর ভেতরেই একাডেমিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
প্রশাসনের পদে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট, সিনেট ও অন্যান্য নির্বাচনে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট, সিনেট ইত্যাদি পরিষদে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি কমাতে বা বাদ দিতে হবে।
তিয়াত্তরের আদেশের আওতাভুক্ত এবং এর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য স্বায়ত্বশাসনের আদর্শের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রকরণভেদ অনুযায়ী যথাযথ আইন ও নীতি চূড়ান্ত করতে হবে। সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
সিদ্ধান্তগ্রহণের সব ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে না রেখে, ক্ষমতাবিভাজন করতে হবে। ভিসি নিয়োগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে সিনেটের ক্ষমতা রাখতে হবে।
সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
ভর্তি ও নিয়োগ
ভর্তিপরীক্ষা পদ্ধতি ধাপে ধাপে পরিবর্তন করে প্রশ্নের ধরন পাল্টাতে হবে এপ্টিচ্যুড টেস্টে যেতে হবে। প্রথম বর্ষে সবাইকে হলে সিট দিয়ে দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে সিট বণ্টন হতে পারে। শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের প্রথম পর্যায়, প্রভাষক পদে নিয়োগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে নিয়োগপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। চাহিদায় প্রাধান্যসমেত নিয়োগপ্রক্রিয়ায় ভিসি-প্রোভিসির তুলনায় বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কেবল মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রদান থেকে সরে আসতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত পরীক্ষামূলক ক্লাসে সিনিয়র শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
বিগত সময়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনায় নিয়োগদানকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
শিক্ষক নিয়োগে স্বল্পকালীন ভিজিটিং প্রফেসরশিপের অর্থায়ন করা দরকার যাতে বিদেশী অধ্যাপক বা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী অধ্যাপকরা এক সিমেস্টারের জন্য হলেও পড়ানোর সুযোগ পান। বিভাগকেন্দ্রিক শিক্ষক-সিন্ডিকেট যা শিক্ষার্থীদের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও অনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখে তার অবসান ঘটাতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাসের আকার সীমিত রাখা জরুরি। পড়াশোনা ও পরীক্ষাকে পাঠমুখীকরণ এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে।
নতুন বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে যথার্থতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনো জলাভূমি, বনভূমি, কৃষি জমি বা ইকোলজিকালি ক্রিটিকাল জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিবর্ধন বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে পরিবেশ বান্ধব হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতার জন্য আলাদা কাঠামোর ব্যবস্থা করা দরকার।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলোকে উপযোগী করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।
স্নাতকোত্তর পর্বের জন্য কেবল নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে হবে। গবেষণা-সংশ্লিষ্টতা বাড়িয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিকে বিশ্বের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢেলে সাজাতে হবে। একাধিক মাস্টার্স করার সুযোগ চাহিদা সাপেক্ষে তৈরি করা আবশ্যক।
উচ্চতর গবেষণায় সংস্কার
আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি যা বৈশ্বিক র্যাংকিংয়েও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পূর্ণকালীন বৃত্তিসহ এমফিল-পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের ভর্তিকেন্দ্র গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি স্নাতকোত্তর গবেষক বাড়াতে হবে।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য যে সরকারি তহবিল রয়েছে, তা বাতিল করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হবে।
গবেষণার অনুদান প্রাপ্তিতে দলগত পরিচয়ের প্রাধান্য বন্ধ করে নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, গবেষণায় চৌর্য্যবৃত্তি ধরার সফটওয়্যারসহ বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ও উন্নত আন্তর্জাতিক জার্নালের এক্সেস ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বৈশ্বিক গবেষণা তহবিল আনার আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে, সাফল্যের জন্য প্রনোদনা, মূল্যায়ন ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দিতে হবে।
[বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষে ১৯ জুলাই ২০২৫ শনিবার নেটওয়ার্কের সম্মেলনে এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

গত দেড় দশকে শিক্ষা খাতে অপরিসীম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, একদলীয় সাংস্কৃতিক বয়ান নির্মাণসহ, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সুবিধাভোগীদের এক সাগরে পরিণত হয়েছিল। যার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে ঘন ঘন অপরিকল্পিতভাবে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট নানা প্রকল্পের অর্থায়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম পরিবর্তন এবং সংশ্লিষট লুটপাটের মধ্যে। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে শিক্ষানীতির প্রতিফলন ছিল না, ছিল না যুগোপযোগী শিক্ষা নীতিও। এছাড়া ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, বাণিজ্য ও লুট-পাটের আখড়ায় পরিণত ছিল শিক্ষাখাত। এর মধ্যে উচ্চ শিক্ষার সাথে উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সংযোগ অত্যন্ত দুর্বল ও একমুখী ছিল।
দেশে একটি যথার্থ যুগোপযুগী শিক্ষানীতি এবং উচ্চশিক্ষা কমিশন না থাকার মূল্য এখন চুকাতে হচ্ছে দেশের শিক্ষাখাতকে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় শিক্ষাখাতে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যয়কারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দুর্বলতাকে। অর্থাৎ শিক্ষায় রাষ্ট্রের বিনিয়োগ অপ্রতুল এবং তা আত্মঘাতী। এমন একটি প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা যদি গত একবছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই যে পরিস্থিতি উত্তরণে কোনো সুদূরপ্রসারী দর্শনগত পরিবর্তন বা কাঠামোগত বদলের ন্যূনতম চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়নি। যা হয়েছে, তা এক ধরনের রঙ বদলের খেলা। একদলের (আওয়ামী) প্রশাসক বা মুখ বদলে প্রধানত অন্য যে দলের প্রভাব (জামাত/বিএনপি) বেশি এমন প্রশাসক বসানো। ফলে শিক্ষাখাত ভয়াবহ এক বিস্ফোরম্মুখ পরস্থিতিতে ধুকছে!
অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষাখাতের খেরোখাতা: অর্জন?
শিক্ষায় অন্তর্বর্তী সরকারের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে নেটওয়ার্ক গত এক বছরে চেষ্টা কিছু কম করেনি। প্রথমত, গত আগস্টে আমরা কেমন বিশ্ববিদ্যালয় ও কেমন প্রশাসক চাই তা তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা, পরবর্তী শিক্ষা উপদেষ্টা এবং প্রধান উপদেষ্টাকে জানিয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম যে, অভ্যুত্থানোত্তর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসকরা হবেন সৎ, বিদ্বান ও দল নিরপেক্ষ, হবেন একেকজন স্বপ্নদ্রষ্টা। সেরকম তো কিছু ঘটেইনি, আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে শিক্ষার্থী - শিক্ষকদের হাতে শুরু হওয়া গণ-অভ্যুত্থানের সরকার শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের কল্যাণকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। শিক্ষাখাতের মূল কাঠামোতে তেমন কোনো মূলগত বা গুণগত পরিবর্তনও করেনি। উল্টো অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা উপদেষ্টাদের প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপের তালিকা বেশ লম্বা।
প্রথমত, অভ্যুত্থানের পরপরই অল্প সংখ্যক সংগবদ্ধ এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে অটোপাসের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির উৎস এবং এই সরকারের অন্যতম ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই ঘটনায় সংঘবন্ধ চাপের কাছে নতিস্বীকারে মন্ত্রণালয়ের প্রধান ব্যক্তির অতি নমনীয়তা বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের ইতিহাসে একটি ক্ষতিকর উদাহরণ তৈরি করে।
দ্বিতীয়ত, ২০২৪ এর আগস্টে ২০২৩ এ চালু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষাক্রম বাতিল করে ২০১২ এর শিক্ষাক্রমকেই পরিমার্জন করে ২০২৫ এর জন্য নতুন বই আনার সিদ্ধান্ত হয় যা বাস্তবায়নে পাঠ্যপুস্তক সংস্কার কমিটি গঠিত হয় এবং তা ব্যাপক সমালোচনা মধ্যে পড়ে। যৌক্তিক সমালোচনা করা যেত যে কেন কমিটিতে শিক্ষা বিষয়ক গবেষক বা আলেমদের (যদিও কওমী মাদ্রাসার বই এই কমিটির কার্যপরিধিতে ছিল না) রাখা হয়নি। কিন্তু কমিটির দুজন সদস্যকে নিয়ে ইচ্ছাকৃত ঘৃণা ও ‘ইসলামবিদ্বেষী’ বলে বিদ্বেষ ছড়ানো শুরু হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে হেফাজতে ইসলামীর হুমকিতে পুরো কমিটিই বাতিল করেন তখনকার শিক্ষা উপদেষ্টা। সরকারের এই আচরণ এসব বিদ্বেষপূর্ণ হস্তক্ষেপকারীদের সাহস যুগিয়ে সাধারণ নাগরিকদের যে বার্তা দেয় তা হলো, একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠির চাপে সরকার নতজানু থাকছে। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসকরা নিরাপত্তাহীনতার ভয় দেখিয়ে ওই একই ধর্মীয় গোষ্ঠির কথা পালনে বাধ্য করেন শিক্ষার্থীদের। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (মাত্র ১০-১৫ জনের চাপে পড়ে) প্রশাসন নিরাপত্তা দিতে রাজি হয়নি বলে একটি আলোচনা সভা বাতিল করতে বাধ্য হয় শিক্ষার্থীরা। তাহলে আর এত দামে কেনা জুলাই অভ্যুত্থানের কোন আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা হলো?
তৃতীয়ত, গত ১৬ বছরে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন, সর্বাগ্রে তাদের দলীয় পরিচয় এবং আনুগত্য দেখিয়ে তখনকার সরকারের ক্ষমতাবলে হয়ে উঠেছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং স্বৈরাচারী। সেই সাথে অনুগতদের নিয়ে একটি সুবিধাভোগী বলয় তৈরি করেছিলেন। গণঅভ্যুত্থানের পরপরই তাদের ব্যাপারে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দের আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট তৈরি হয়েছিল বলেই দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদত্যাগ করেছিলেন বা শিক্ষার্থীদের চাপে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। এমতাবস্থায় প্রশাসনিক নেতৃত্বের ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হয়েছিল এবং অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত তৎপর না হওয়ায়, ব্যক্তিপর্যায়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের হাতে শিক্ষক হেনস্থার ঘটনা ঘটে যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এসব ঘটনাকে স্বার্থান্বেষীদের কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে।
চতুর্থত, পরিতাপের বিষয়, অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের অসহিষ্ণু, আক্রমণাত্মক ও নৈরাজ্যবাদী জমায়েত থেকে অপছন্দের গোষ্ঠী ও দলের বিরুদ্ধে কেবল হিংসাত্মক কথাবার্তাই বলা হয়নি, ক্ষেত্রবিশেষে সেসব মানুষের ওপর হামলাও চালানো হয়েছে। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গবদ্ধ হিংস্রতায় নিহত হয়েছেন তিনজন মানুষ। এইসব ঘৃণ্য অপরাধের সুষ্ঠু বিচার এখনো হয় নাই। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে আক্রমণকারীর পুণর্বাসনও হয়েছে সংশ্লিষ্ট ক্যাম্পাসে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষকে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও দপ্তরে ছোট ছোট অজস্র হিংস্রতার ঘটনা ঘটেই চলেছে। মাজার, মন্দির, শিল্প-স্থাপনা ভাংচুর থেকে শুরু করে বাউল ও আহমেদিয়াদের ওপরও আক্রমণ হয়েছে। নানা স্থাপনা, ভাস্কর্য এবং শিল্পকর্ম ভাঙা হয়েছে যার সাথে অভ্যুত্থানের শক্তি শিক্ষার্থীদের নাম জড়িয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালগুলোর প্রশাসকদের পদগুলিতে (উপচার্য, উপ উপাচার্য, কোষাধক্ষ্য, প্রভোস্ট, ডিন, প্রক্টর ইত্যাদি) যাদেরকে বসানো হয়েছে তাদের সম্পর্কে উপদেষ্টা নিজেই বলেছেন যে এদের বেশির ভাগই ‘মৃদু বিএনপি’ বা আসলে জামাত-বিএনপি। শিক্ষক নেটওয়ার্ক অত্যন্ত হতাশার সাথে লক্ষ্য করছে যে সেই একই দলীয় পরিচয় দিয়েই প্রশাসক নিয়োগ হচ্ছে যা অভ্যুত্থানের আকাংক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব দলীয় শিক্ষকরা দলীয় সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক উন্নতির কথা ভাবছেন না। বঞ্চিত ক্যাটাগরিতে এখন পদ-পদবী দখল এবং পদোন্নতির মহা-উৎসব শুরু হয়েছে।
ষষ্ঠত, রাস্তায় ও পর্যটন অঞ্চলেই শুধু নয় দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা, বাচিক ও শারীরিক, সাইবার নিগ্রহ এবং চরম হেনস্তা চলেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ জন ছাত্রী. যাদের অনেকেই জুলাই অভ্যুত্থানের সামনের সারির মুখ, তাদেরকে মিথ্যা অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, একই সাথে শিক্ষকদের দ্বারা সাইবার নিপীড়নের শিকার হয়েছেন সেই শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী দ্বারা ভাষিক যৌন নিপীড়নের শিকার শিক্ষার্থী সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন অপরাধীর সহযোগীদের হাতে। বিশ্ববিদ্যালয় তার পাশে দাঁড়ায়নি। অভিযোগ তদন্তের কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি। এই অভিযোগটি এমনকি যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলেও পৌছায়নি। নারীর অধিকার বা হিস্যা আদায়ের দাবীতে রাস্তায় আন্দোলনকারী, অভ্যুত্থানের সামনের মুখ নরসিংদীর কলেজ শিক্ষিকা নাদিরা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে হেফাজতের হেট ক্যাম্পেইনের মুখে আবারো পিছু হটেছে শিক্ষা মন্ত্রনালয় তিন বার বদলি করেছে নাদিরাকে। উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সামনে বারবার এই ধরনের আত্মসমর্পন এই প্রশ্ন সামনে আনে যে হেফাজতে ইসলামীসহ আরো কিছু ধর্মভিত্তিক দল (যারা অভ্যুত্থানের মধ্যেও হাসিনার পক্ষে ছিল) তারা এখনো নারী অভ্যুত্থানকারীদের বিপদে ফেলছে। কোথায় তাহলে আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচার, যেটা ছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতনের পর আমাদের প্রধানতম চাওয়া?
সপ্তমত, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানাবিধ ফি’র নামে শিক্ষার্থীদের শোষণ ও বঞ্চনা শেষ হয়নি। ইউআইইউ এর আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে আবার পুলিশ বলপ্রয়োগ করেছে যা সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষককে অভ্যত্থানে যোগ দেবার ‘অপরাধে’ হয়রানি ও চাকুরিচ্যুত করেছে প্রশাসন। বেতনের দাবীতে জড়ো হওয়া প্রাথমিক শিক্ষকদের ওপর হামলা করেছে পুলিশ। শ্রমিকদের ওপর হামলা করেছে এর কোনো প্রতিবাদ অভ্যুত্থানকারী শিক্ষার্থীদের মূল শক্তির কাছ থেকে আসেনি যা ভয়াবহভাবে হতাশার। বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত বা পুলিশে এক বছর প্রশিক্ষণের পরেও যাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে কোনো যৌক্তিক কারণ না দেখিয়ে, তাদের পক্ষেও দাড়ায়নি বৈষম্যবিরোধীরা।
অষ্টমত, আওয়ামী আমলে সরকারীভাবে জেলায় জেলায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হলেও সংখ্যার তুলনায় মানের সঙ্কট রয়েই গেছে। জনবল ও সম্পদের অভাব এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগোতে দিচ্ছে না। গবেষণায় বরাদ্দ যৎসামান্য হওয়ায় সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় কেবল ‘আন্ডারগ্র্যাডকলেজ’-এর ভূমিকাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে, নতুন জ্ঞান সৃজনের কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পালন করতে পারছে না। কুয়েটের ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির চাপে হামলা-আক্রমণ আমাদের সামনে নিয়ে আসে তথাকথিত ‘রাজনীতিহীন’ ক্যাম্পাসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতির গভীর শেকড়।
নবমত, স্বায়ত্বশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোতে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির দলীয় লেজুড়বৃত্তির ফলে গত কয়েকদশক ধরে শিক্ষক নিয়োগ বা ছাত্রাবাসে শিক্ষার্থীদের জীবনযাপনে সবকিছুর উর্ধ্বে দলীয় বিবেচনা প্রধান হয়ে উঠেছিলো। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের পর একটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক/ছাত্র সংঙ্গঠনের প্রভাব না থাকলেও ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে এক ভিন্ন রকমের নীতি পুলিশী (মরাল পুলিশিং) শুরু হয়েছে, যার প্রধান শিকার নারী শিক্ষার্থী ও ভিন্ন মতের শিক্ষকরা যা আশংকাজনক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইচ্ছামতো নাম বদলের সংস্কৃতি। খুলনা ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-বদলকাণ্ডে বিপদজনক জনতুষ্টিবাদী ঝোঁক, শিক্ষাবিমুখতা ও সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পায়।
দশমত, ১৯৭৩-এর আদেশের বাইরের নানা প্রকৃতির পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সব ক্ষমতা উপাচার্যের নিকট কেন্দ্রীভূত, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রকমের আইন দিয়ে চলছে, গণতান্ত্রিক উপাদানের ঘাটতি আছে এবং আছে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন কেন্দ্রীভূত প্রশাসনব্যবস্থা। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকের স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ প্রচুর। পরিস্থিতির খুব একটা উন্নতি গত ১ বছরে দেখা যায়নি। পুরনো ব্যবস্থা নতুন চেহারার নিচে টিকে আছে। বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা আত্মগোপনে যাবার পর অন্যান্য শিক্ষকদের দলবাজি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর এই ধরনের প্রবণতা ব্যবহার করে প্রশাসন আরো কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে।
সঙ্কট নির্দিষ্টকরণ
আমরা তাহলে এখন কী চাই? এই সংকটজনক অবস্থার পরিবর্তন চাই। তাই সংকটগুলো চিহ্নিত করেছিলাম ১ বছর আগে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একই সংকট এখনো রয়ে গিয়েছে। আমরা কোথাও অগ্রগতির চিহ্ন দেখছি না।
শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ শিক্ষায় বরাদ্দের হারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন। একদিকে শিক্ষা গবেষণার তহবিলের বরাদ্দ নেই, নেই উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা, অন্যদিকে হীন দলীয় রাজনীতি গবেষণামনষ্ক শিক্ষকদের জন্য নানান প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে, যেক্ষেত্রে গবেষণাবিমুখ ও রাজনীতিপ্রবণ শিক্ষকদের জন্য রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ উন্নয়নের নানান উপায়।
সরকারি কর্তৃত্ব আওয়ামী লীগ পালানোর পর শিক্ষার্থীদের গণরুম গেস্টরুম উঠে যাওয়ায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিছুটা সুবাতাস বইলেও শিক্ষকদের জন্য পরিস্থিতি খুব বদলায়নি। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউজিসির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সরকারি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয় যদিও এরা বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। আবার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা কার্যক্রম এবং সনদ প্রদানের অনুমোদন পেয়েছে। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ করা হয় বিশ্ববিদ্যালগুলোর পক্ষ থেকে এবং শিক্ষকদের নানান বৈষম্যের শিকার হতে হয় এখানে।
নয়া উদারবাদী নীতি ও ইউজিসি মানোন্নয়নের নামে সর্বজনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করতে ও সরকারি বরাদ্দ কমাতে নীতিগত চাপ প্রয়োগ করছে। বিভাগগুলোতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতনভাতার বাইরে, তেমন কোন অর্থ বরাদ্দ না দিয়ে অন্যান্য ব্যয় স্ব স্ব বিভাগকে বহন করতে বলা হয়, এতে করে বিভাগগুলোকে ইভিনিং বা উইকএন্ড প্রোগ্রামের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে একদিকে শিক্ষকদের শিক্ষার মানের দিকে খেয়াল করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে পারলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র হারিয়ে ওই সব প্রোগ্রমের শিক্ষার্থীদের গুনতে হচ্ছে বিশাল শিক্ষা ব্যয়। একই সাথে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাবি অথচ দরিদ্রদের পড়ার সুযোগ ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠছে, শিক্ষা পণ্যায়িত হয়ে উঠেছে। গবেষণার বরাদ্দ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে তার স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা হচ্ছে না।
স্বায়ত্তশাসনের অপব্যবহার: তিয়াত্তরের আদেশ পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করলেও মূলত দলীয় রাজনীতি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। ক্যাম্পাস সরকারদলীয় শিক্ষকনেতৃবৃন্দের নিয়ন্ত্রাণাধীন ছিল যা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানভিত্তিক না হয়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক করে তুলেছিলো সে পরিস্থিতি এখনো বিদ্যমান আছে।
ভর্তি ও নিয়োগ পাঠদান ও গবেষণা: নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অকার্যকর গুচ্ছ পদ্ধতিসহ নানান নিরীক্ষায় কিছু শিক্ষকের পকেটভারি হলেও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের হয়রানি বাড়ে একদিকে, অন্যদিকে এমসিকিউনির্ভর ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়-উপযোগী কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী খুঁজে না পাওয়াও ক্লাসরুমের গড় মান পড়ে যাচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো দলীয় বিবেচনায় ‘ভোটার’ নিয়োগের প্রবণতায় মেধা বা যোগ্যতা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিতে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। আবার শিক্ষার্থীদের পিএইচডি এমফিল গবেষণার জন্য সুষ্ঠু প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অনুপস্থিতিতে গবেষণা ও পিএইচডির মানও নিশ্চিত করা যায় নাই।
শিক্ষার্থীদের আবাসন ও ছাত্র রাজনীতি: পাবলিক বিশ্বববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে বসবাসের ও অধ্যয়নের সুব্যবস্থা নেই। জুলাই এর পর একদলের মাস্তানতন্ত্র উচ্ছেদ হলেও বিদ্যায়তনিক গণতন্ত্র এখনো অনেক দূরে। ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ পরিচয়ে এক নতুন আধিপত্যকামী শক্তির দেখা মিলছে যাদের দ্বারা প্রান্তিক মত এবং কণ্ঠস্বর দমন-পীড়নের স্বীকার হচ্ছে।।
উচ্চ টিউশন ফি ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমরূপ বা হোমোজেনাস নয়। তাদের মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। অল্প কয়েকটির মান উন্নত (যদিও সেখানে টিউশন ফি অত্যন্ত উচ্চ) হলেও বেশিরভাগের মান সাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত মুনাফামুখী, এবং এখানে গবেষণার পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। প্রবল সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়কেন্দ্রিক দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগে নির্ভরশীল। এছাড়াও, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃভাষাকে অবমূল্যায়ন করে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শুধু ইংরেজি রেখেছে, যা শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে।
সমাধানপ্রস্তাব
শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ: শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বিনিয়োগ করতে হবে রাষ্ট্রকে। আগামী ৪ (চার) বছরের মধ্যে শিক্ষায় জিডিপির শতকরা ০৭ (সাত) ভাগ বরাদ্দে পৌছানোর লক্ষমাত্রা নিয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এই বরাদ্দের সুনিদ্দিষ্ট অংশ গবেষণায় এবং শিক্ষাদান ও শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হতে হবে।
প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সকল শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ও চাকরির সুবিধা দিতে হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের দায়িত্বে থাকা এনসিটিবিকে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।
শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চিন্তার স্বাধীনতা, বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা, প্রশ্ন ও মত প্রকাশের পরিসর এবং বিশ্লেষণের বিস্তারের ক্ষেত্র নিয়ে তৈরী হবে এমন চাই।
ইউজিসির কৌশলপত্র ও নয়া উদারবাদী নীতি: নব্যউদারবাদী মতাদর্শের আলোকে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রণীত বাণিজ্যিকীকরণের নীতি ও পরিচালনার নানা পরামর্শ থেকে সরে আসতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চশিক্ষাকে দরিদ্র মানুষদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। বছর বছর ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বাড়ানো কিংবা নানান নামে ভর্তির সময় অর্থ আদায় বন্ধ করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার আইন ও নীতি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চা গুরুত্বপূর্ণ তবে সকল স্তরে দলীয় আধিপত্যবিস্তারের রাজনীতি বন্ধ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর ভেতরেই একাডেমিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।
প্রশাসনের পদে থাকা শিক্ষকদের শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট, সিনেট ও অন্যান্য নির্বাচনে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড থেকে শুরু করে সিন্ডিকেট, সিনেট ইত্যাদি পরিষদে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি কমাতে বা বাদ দিতে হবে।
তিয়াত্তরের আদেশের আওতাভুক্ত এবং এর বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য স্বায়ত্বশাসনের আদর্শের আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা প্রকরণভেদ অনুযায়ী যথাযথ আইন ও নীতি চূড়ান্ত করতে হবে। সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
সিদ্ধান্তগ্রহণের সব ক্ষমতা উপাচার্যের হাতে না রেখে, ক্ষমতাবিভাজন করতে হবে। ভিসি নিয়োগে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে সিনেটের ক্ষমতা রাখতে হবে।
সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল প্রকার নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
ভর্তি ও নিয়োগ
ভর্তিপরীক্ষা পদ্ধতি ধাপে ধাপে পরিবর্তন করে প্রশ্নের ধরন পাল্টাতে হবে এপ্টিচ্যুড টেস্টে যেতে হবে। প্রথম বর্ষে সবাইকে হলে সিট দিয়ে দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে উপরের দিকে মেধা ও চাহিদার ভিত্তিতে সিট বণ্টন হতে পারে। শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের প্রথম পর্যায়, প্রভাষক পদে নিয়োগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে এ বিষয়ে নিয়োগপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। চাহিদায় প্রাধান্যসমেত নিয়োগপ্রক্রিয়ায় ভিসি-প্রোভিসির তুলনায় বিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কেবল মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রদান থেকে সরে আসতে হবে। নিয়োগসংক্রান্ত পরীক্ষামূলক ক্লাসে সিনিয়র শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
বিগত সময়ে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনায় নিয়োগদানকারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।
শিক্ষক নিয়োগে স্বল্পকালীন ভিজিটিং প্রফেসরশিপের অর্থায়ন করা দরকার যাতে বিদেশী অধ্যাপক বা বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী অধ্যাপকরা এক সিমেস্টারের জন্য হলেও পড়ানোর সুযোগ পান। বিভাগকেন্দ্রিক শিক্ষক-সিন্ডিকেট যা শিক্ষার্থীদের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও অনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখে তার অবসান ঘটাতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন
বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাসের আকার সীমিত রাখা জরুরি। পড়াশোনা ও পরীক্ষাকে পাঠমুখীকরণ এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে গড়ে তুলতে হবে।
নতুন বিভাগ বা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে যথার্থতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোনো জলাভূমি, বনভূমি, কৃষি জমি বা ইকোলজিকালি ক্রিটিকাল জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বা পরিবর্ধন বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে পরিবেশ বান্ধব হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতার জন্য আলাদা কাঠামোর ব্যবস্থা করা দরকার।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলোকে উপযোগী করে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।
স্নাতকোত্তর পর্বের জন্য কেবল নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে হবে। গবেষণা-সংশ্লিষ্টতা বাড়িয়ে মাস্টার্স ডিগ্রিকে বিশ্বের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ঢেলে সাজাতে হবে। একাধিক মাস্টার্স করার সুযোগ চাহিদা সাপেক্ষে তৈরি করা আবশ্যক।
উচ্চতর গবেষণায় সংস্কার
আমাদের বিশ্ববিদ্যালগুলোর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রি যা বৈশ্বিক র্যাংকিংয়েও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পিছিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পূর্ণকালীন বৃত্তিসহ এমফিল-পিএইচডি প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। আন্তর্জাতিক মানের ভর্তিকেন্দ্র গড়ে তুলে দেশি-বিদেশি স্নাতকোত্তর গবেষক বাড়াতে হবে।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিদেশে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য যে সরকারি তহবিল রয়েছে, তা বাতিল করে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন স্নাতকোত্তর গবেষণার জন্য ব্যয় করতে হবে।
গবেষণার অনুদান প্রাপ্তিতে দলগত পরিচয়ের প্রাধান্য বন্ধ করে নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও আদান প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে, গবেষণায় চৌর্য্যবৃত্তি ধরার সফটওয়্যারসহ বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় সফটওয়ার ও উন্নত আন্তর্জাতিক জার্নালের এক্সেস ও প্রকাশনার জন্য শিক্ষকদের প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বৈশ্বিক গবেষণা তহবিল আনার আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে, সাফল্যের জন্য প্রনোদনা, মূল্যায়ন ও প্রশাসনিক সহযোগিতা দিতে হবে।
[বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের পক্ষে ১৯ জুলাই ২০২৫ শনিবার নেটওয়ার্কের সম্মেলনে এ বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে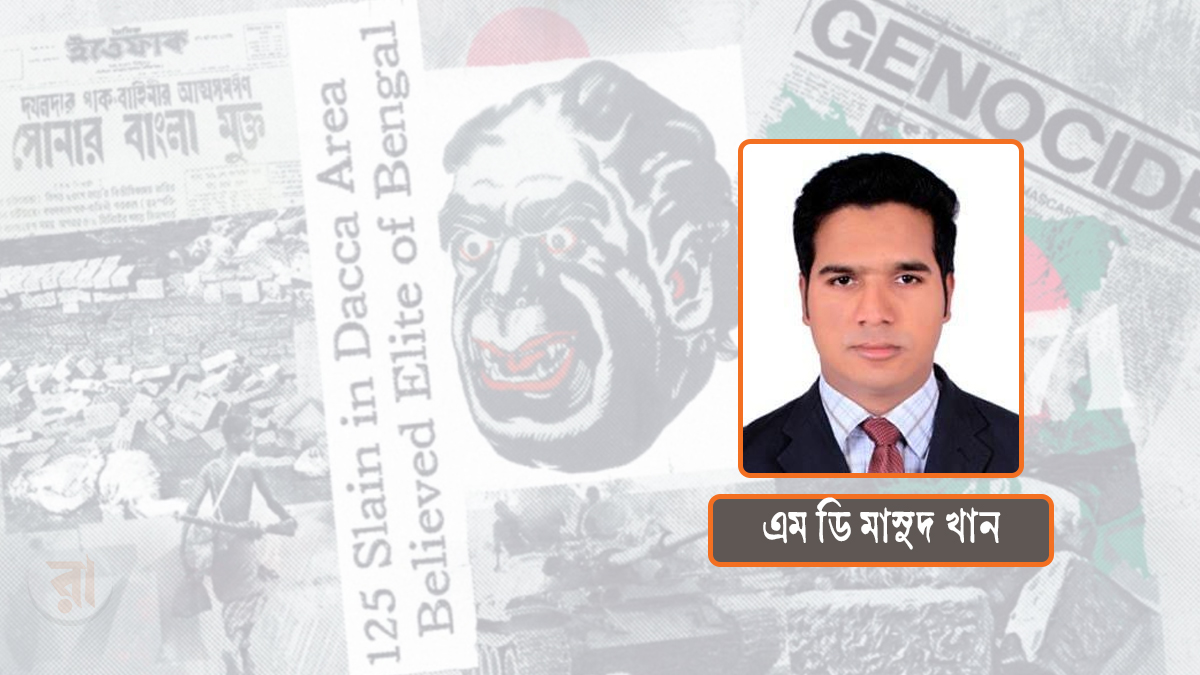
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে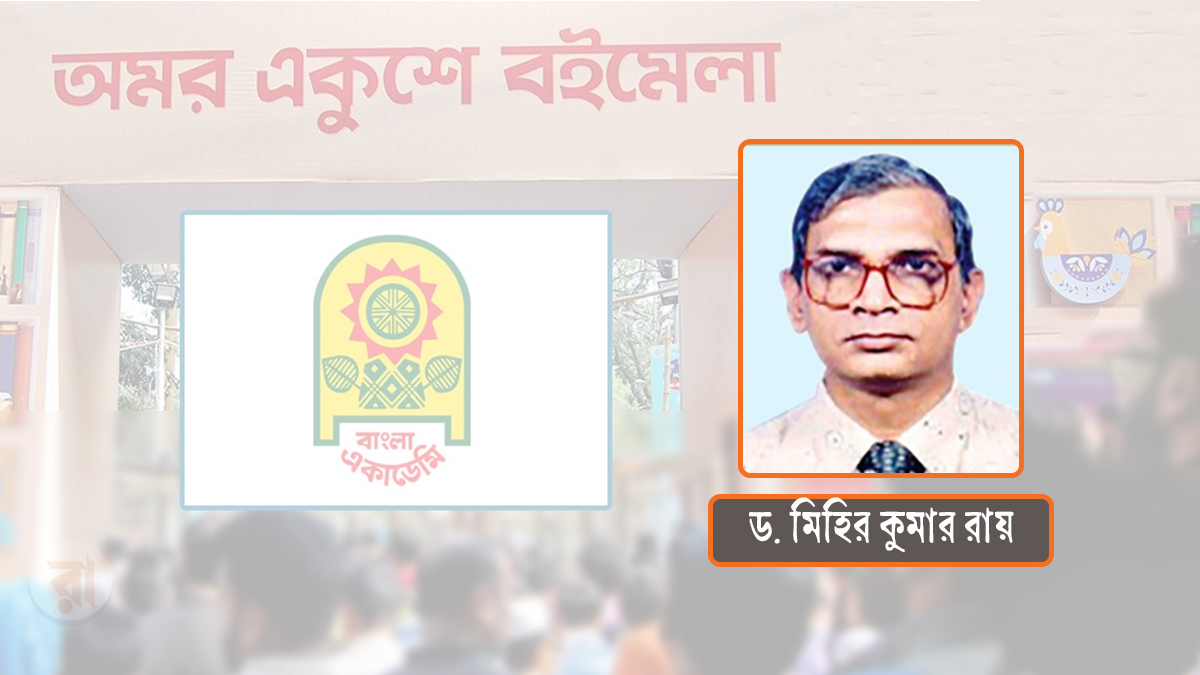
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে