
রাজু আলীম

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন যে বিতর্কটি জোরালো হয়ে উঠেছে, সেটি ‘পিআর নির্বাচন’—প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা। ধারণাটি নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এটি হঠাৎ যেভাবে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, তাতে মনে হচ্ছে এটি কেবল নির্বাচন সংস্কারের প্রস্তাব নয়, বরং এক রাজনৈতিক কৌশল। বিশেষত বিএনপি, জামায়াতসহ কয়েকটি দলের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ‘পিআর’ এখন ভোটের পদ্ধতির আলোচনা ছাড়িয়ে ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার নতুন কৌশলে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অবস্থান এই বিষয়ে একেবারেই পরিষ্কার। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, “বাংলাদেশে পিআর মানে বিভ্রান্তি ছড়ানো।” তাঁর মতে, দেশের সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থার অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে জানে না, অথচ কিছু মহল পরিকল্পিতভাবে এটি সামনে এনে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে জটিল করতে চাইছে। তাঁর ভাষায়, “এটা নতুন এক ধরণের প্যাঁচ, যাতে নির্বাচনের সময়সূচি ও কাঠামো নিয়ে আবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।” বিএনপির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই বিতর্কের মূল লক্ষ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নিজেদের মতো সাজানো।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও বলেছেন, “এই পিআর নিয়ে কথা বলে জনগণকে ভুল পথে নেওয়া হচ্ছে।” তাঁর দাবি, এটি আসলে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরির নতুন প্রচারণা। যখন দেশে ভোটের পরিবেশ গড়ে তোলার কথা, তখন এমন প্রস্তাব নির্বাচনকে আরও জটিল করছে। বিএনপির অন্যান্য নেতারাও একে ‘বিলম্বের কৌশল’ বলছেন। কারণ, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করতে হলে সাংবিধানিক সংশোধন, আইনি কাঠামো, প্রশাসনিক প্রস্তুতি—সবকিছুতেই সময় ও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুপস্থিত।
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী আনুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে সরব। তাদের দাবি, এই ব্যবস্থায় ছোট দলগুলোরও সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হবে, ফলে জাতীয় রাজনীতিতে ভারসাম্য আসবে। কিন্তু বিএনপি ও অনেক বিশ্লেষকের মতে, জামায়াতের এই অবস্থান আসলে নিজেদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা। যেহেতু জামায়াত এখনো ক্ষমতার কাঠামোয় প্রবেশ করতে চায়, তাই পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে তালিকা-ভিত্তিক সংসদ সদস্য নির্বাচনের সুযোগ তাদের জন্য বড় সুবিধা এনে দিতে পারে। বিএনপির যুক্তি, এটি গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য ‘রাজনৈতিক শর্টকাট’।
প্রশ্ন উঠছে—এই সময়ে হঠাৎ পিআর নিয়ে এমন বিতর্ক কেন? ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ এখন পুনর্গঠনের পর্যায়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন কবে, কীভাবে এবং কোন কাঠামোতে হবে—তা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তার ফাঁকে নানা প্রস্তাব উঠে আসছে, যার একটি পিআর পদ্ধতি। কিন্তু বাংলাদেশের ভোটাররা এখনো সরাসরি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত। তালিকা-ভিত্তিক ভোট বা দলীয় তালিকার ধারণা সাধারণ ভোটারের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতাই এখন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে।
পিআর পদ্ধতির মূল ধারণা হলো—মোট ভোটের অনুপাত অনুযায়ী সংসদে আসন বণ্টন করা, যাতে ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। তত্ত্বগতভাবে এটি ন্যায্য। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায়, যেখানে দলীয় গণতন্ত্র দুর্বল এবং মনোনয়ন নির্ভর করে নেতৃত্বের ইচ্ছার ওপর, সেখানে এই পদ্ধতি কার্যত ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করবে। দলের প্রধানরা তালিকা তৈরি করবেন, আর সেই তালিকা থেকেই সংসদ সদস্য হবেন। এতে সাধারণ ভোটারের ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়বে। মির্জা ফখরুলের ভাষায়, “এটা গণতন্ত্র নয়, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মনোনয়ন রাজনীতি।”
অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা নির্বাচন সংস্কার নিয়ে কথা বলেছেন। কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রচলিত ব্যবস্থা অথবা পিআর পদ্ধতিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া এ ধরনের সংস্কার বাস্তবায়ন অসম্ভব। দলগুলোর মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এখন এতটাই গভীর যে কোনো পরিবর্তনই গণসমর্থন পাবে না।
নির্বাচন কমিশনের অবস্থানও স্পষ্ট। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, “আরপিওতে পিআর নেই, আরপিও সামনে রেখেই কমিশনকে এগোতে হচ্ছে।” অর্থাৎ সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী প্রচলিত ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতিতেই ভোটের প্রস্তুতি চলছে। এতে জামায়াতের ক্ষোভ দেখা গেছে। তাদের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, “প্রধান নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তা একটা দলের মতো কথা কেন বলবেন?” তাঁর দাবি, রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে “এক মাসের মধ্যেই পিআর বাস্তবায়ন করা সম্ভব।”
কিন্তু নির্বাচন বিশেষজ্ঞ জেসমিন টুলি বলছেন, পিআর বাস্তবায়নে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, তারপর তার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন, বিধিমালা তৈরি এবং মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, এবং “বছর দেড়েকের আগে শেষ করা সম্ভব নয়।” তাঁর মতে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবস্থা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট—যেখানে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থী জয়ী হন। যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিছু দেশ আনুপাতিক ব্যবস্থায় গিয়েছে, তবে বাংলাদেশের মতো দলনির্ভর ও বিভক্ত রাজনীতিতে এটি কার্যকর করার আগে বিশাল প্রস্তুতি ও গণসংলাপ প্রয়োজন। এখনো সেই প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি।
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক দল নিজেদের অবস্থান পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জামায়াত আনুপাতিক ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলছে, কারণ এতে ছোট দলের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বাড়ে। কিন্তু বিএনপি প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতিতেই অনড়। এই বিভাজনের ফলে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কোনো লক্ষণ নেই।
এখন যে বাস্তবতা, তাতে ‘পিআর নির্বাচন’ নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ‘পিআর রাজনীতি’। এটি যেন নতুন ধরনের প্রচারণা, যেখানে প্রতিটি দল নিজেদের স্বার্থমাফিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। কেউ বলছে এটি গণতন্ত্রের বিকল্প, কেউ বলছে এটি গণতন্ত্রের বিকৃতি। কিন্তু জনগণ—যাদের হাতে ক্ষমতা থাকার কথা—তারা এখনো এই আলোচনার বাইরে।
সবশেষে প্রশ্ন থেকেই যায়—এই বিতর্কের উদ্দেশ্য কি সত্যিই নির্বাচন সংস্কার, নাকি এটি আরেকটি রাজনৈতিক চাল? সংবিধান পরিবর্তন ছাড়াই পিআর চালু করা সম্ভব নয়, এবং ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে পিআর বিতর্ক কার্যত সময়ক্ষেপণের উপায় হয়ে উঠছে, যা নির্বাচনের প্রস্তুতিকে অনিশ্চিত করছে।
পিআর পদ্ধতি তাত্ত্বিকভাবে গণতান্ত্রিক বিকল্প হতে পারে—যদি তা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে, স্বচ্ছ আইনি কাঠামো ও রাজনৈতিক ঐকমত্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু যদি এটি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের হাতিয়ার হয়, তবে এটি গণতন্ত্রের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনবে। এখন প্রয়োজন, এই পিআর প্যাঁচ থেকে নির্বাচনকে মুক্ত রাখা—যেন ভোট হয় জনগণের হাতে, তালিকার হাতে নয়।
লেখক: কবি ও সাংবাদিক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন যে বিতর্কটি জোরালো হয়ে উঠেছে, সেটি ‘পিআর নির্বাচন’—প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা। ধারণাটি নতুন নয়, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এটি হঠাৎ যেভাবে আলোচনার কেন্দ্রে এসেছে, তাতে মনে হচ্ছে এটি কেবল নির্বাচন সংস্কারের প্রস্তাব নয়, বরং এক রাজনৈতিক কৌশল। বিশেষত বিএনপি, জামায়াতসহ কয়েকটি দলের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ‘পিআর’ এখন ভোটের পদ্ধতির আলোচনা ছাড়িয়ে ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার নতুন কৌশলে পরিণত হয়েছে।
বিএনপির অবস্থান এই বিষয়ে একেবারেই পরিষ্কার। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, “বাংলাদেশে পিআর মানে বিভ্রান্তি ছড়ানো।” তাঁর মতে, দেশের সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থার অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে জানে না, অথচ কিছু মহল পরিকল্পিতভাবে এটি সামনে এনে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে জটিল করতে চাইছে। তাঁর ভাষায়, “এটা নতুন এক ধরণের প্যাঁচ, যাতে নির্বাচনের সময়সূচি ও কাঠামো নিয়ে আবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।” বিএনপির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এই বিতর্কের মূল লক্ষ্য নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে নিজেদের মতো সাজানো।
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও বলেছেন, “এই পিআর নিয়ে কথা বলে জনগণকে ভুল পথে নেওয়া হচ্ছে।” তাঁর দাবি, এটি আসলে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরির নতুন প্রচারণা। যখন দেশে ভোটের পরিবেশ গড়ে তোলার কথা, তখন এমন প্রস্তাব নির্বাচনকে আরও জটিল করছে। বিএনপির অন্যান্য নেতারাও একে ‘বিলম্বের কৌশল’ বলছেন। কারণ, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা চালু করতে হলে সাংবিধানিক সংশোধন, আইনি কাঠামো, প্রশাসনিক প্রস্তুতি—সবকিছুতেই সময় ও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রয়োজন, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অনুপস্থিত।
অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী আনুপাতিক পদ্ধতির পক্ষে সরব। তাদের দাবি, এই ব্যবস্থায় ছোট দলগুলোরও সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হবে, ফলে জাতীয় রাজনীতিতে ভারসাম্য আসবে। কিন্তু বিএনপি ও অনেক বিশ্লেষকের মতে, জামায়াতের এই অবস্থান আসলে নিজেদের রাজনৈতিক পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা। যেহেতু জামায়াত এখনো ক্ষমতার কাঠামোয় প্রবেশ করতে চায়, তাই পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে তালিকা-ভিত্তিক সংসদ সদস্য নির্বাচনের সুযোগ তাদের জন্য বড় সুবিধা এনে দিতে পারে। বিএনপির যুক্তি, এটি গণতন্ত্রের স্বার্থে নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য ‘রাজনৈতিক শর্টকাট’।
প্রশ্ন উঠছে—এই সময়ে হঠাৎ পিআর নিয়ে এমন বিতর্ক কেন? ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ এখন পুনর্গঠনের পর্যায়ে। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন কবে, কীভাবে এবং কোন কাঠামোতে হবে—তা অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তার ফাঁকে নানা প্রস্তাব উঠে আসছে, যার একটি পিআর পদ্ধতি। কিন্তু বাংলাদেশের ভোটাররা এখনো সরাসরি প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত। তালিকা-ভিত্তিক ভোট বা দলীয় তালিকার ধারণা সাধারণ ভোটারের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্যতাই এখন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে।
পিআর পদ্ধতির মূল ধারণা হলো—মোট ভোটের অনুপাত অনুযায়ী সংসদে আসন বণ্টন করা, যাতে ছোট দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। তত্ত্বগতভাবে এটি ন্যায্য। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায়, যেখানে দলীয় গণতন্ত্র দুর্বল এবং মনোনয়ন নির্ভর করে নেতৃত্বের ইচ্ছার ওপর, সেখানে এই পদ্ধতি কার্যত ক্ষমতাকে আরও কেন্দ্রীভূত করবে। দলের প্রধানরা তালিকা তৈরি করবেন, আর সেই তালিকা থেকেই সংসদ সদস্য হবেন। এতে সাধারণ ভোটারের ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়বে। মির্জা ফখরুলের ভাষায়, “এটা গণতন্ত্র নয়, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মনোনয়ন রাজনীতি।”
অন্তর্বর্তী সরকারের কয়েকজন উপদেষ্টা নির্বাচন সংস্কার নিয়ে কথা বলেছেন। কেউ কেউ ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রচলিত ব্যবস্থা অথবা পিআর পদ্ধতিও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐকমত্য ছাড়া এ ধরনের সংস্কার বাস্তবায়ন অসম্ভব। দলগুলোর মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এখন এতটাই গভীর যে কোনো পরিবর্তনই গণসমর্থন পাবে না।
নির্বাচন কমিশনের অবস্থানও স্পষ্ট। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, “আরপিওতে পিআর নেই, আরপিও সামনে রেখেই কমিশনকে এগোতে হচ্ছে।” অর্থাৎ সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী প্রচলিত ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট (FPTP) পদ্ধতিতেই ভোটের প্রস্তুতি চলছে। এতে জামায়াতের ক্ষোভ দেখা গেছে। তাদের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, “প্রধান নির্বাচন কমিশন কর্মকর্তা একটা দলের মতো কথা কেন বলবেন?” তাঁর দাবি, রাজনৈতিক দলগুলো একমত হলে “এক মাসের মধ্যেই পিআর বাস্তবায়ন করা সম্ভব।”
কিন্তু নির্বাচন বিশেষজ্ঞ জেসমিন টুলি বলছেন, পিআর বাস্তবায়নে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, তারপর তার ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন, বিধিমালা তৈরি এবং মাঠপর্যায়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, এবং “বছর দেড়েকের আগে শেষ করা সম্ভব নয়।” তাঁর মতে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।
বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যবস্থা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট—যেখানে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রার্থী জয়ী হন। যুক্তরাজ্যসহ অনেক দেশ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিছু দেশ আনুপাতিক ব্যবস্থায় গিয়েছে, তবে বাংলাদেশের মতো দলনির্ভর ও বিভক্ত রাজনীতিতে এটি কার্যকর করার আগে বিশাল প্রস্তুতি ও গণসংলাপ প্রয়োজন। এখনো সেই প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি।
২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক দল নিজেদের অবস্থান পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ও জামায়াত আনুপাতিক ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলছে, কারণ এতে ছোট দলের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ বাড়ে। কিন্তু বিএনপি প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতিতেই অনড়। এই বিভাজনের ফলে রাজনৈতিক ঐকমত্যের কোনো লক্ষণ নেই।
এখন যে বাস্তবতা, তাতে ‘পিআর নির্বাচন’ নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি হচ্ছে ‘পিআর রাজনীতি’। এটি যেন নতুন ধরনের প্রচারণা, যেখানে প্রতিটি দল নিজেদের স্বার্থমাফিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছে। কেউ বলছে এটি গণতন্ত্রের বিকল্প, কেউ বলছে এটি গণতন্ত্রের বিকৃতি। কিন্তু জনগণ—যাদের হাতে ক্ষমতা থাকার কথা—তারা এখনো এই আলোচনার বাইরে।
সবশেষে প্রশ্ন থেকেই যায়—এই বিতর্কের উদ্দেশ্য কি সত্যিই নির্বাচন সংস্কার, নাকি এটি আরেকটি রাজনৈতিক চাল? সংবিধান পরিবর্তন ছাড়াই পিআর চালু করা সম্ভব নয়, এবং ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে পিআর বিতর্ক কার্যত সময়ক্ষেপণের উপায় হয়ে উঠছে, যা নির্বাচনের প্রস্তুতিকে অনিশ্চিত করছে।
পিআর পদ্ধতি তাত্ত্বিকভাবে গণতান্ত্রিক বিকল্প হতে পারে—যদি তা জনগণের মতামতের ভিত্তিতে, স্বচ্ছ আইনি কাঠামো ও রাজনৈতিক ঐকমত্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। কিন্তু যদি এটি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের হাতিয়ার হয়, তবে এটি গণতন্ত্রের জন্য নতুন বিপদ ডেকে আনবে। এখন প্রয়োজন, এই পিআর প্যাঁচ থেকে নির্বাচনকে মুক্ত রাখা—যেন ভোট হয় জনগণের হাতে, তালিকার হাতে নয়।
লেখক: কবি ও সাংবাদিক

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে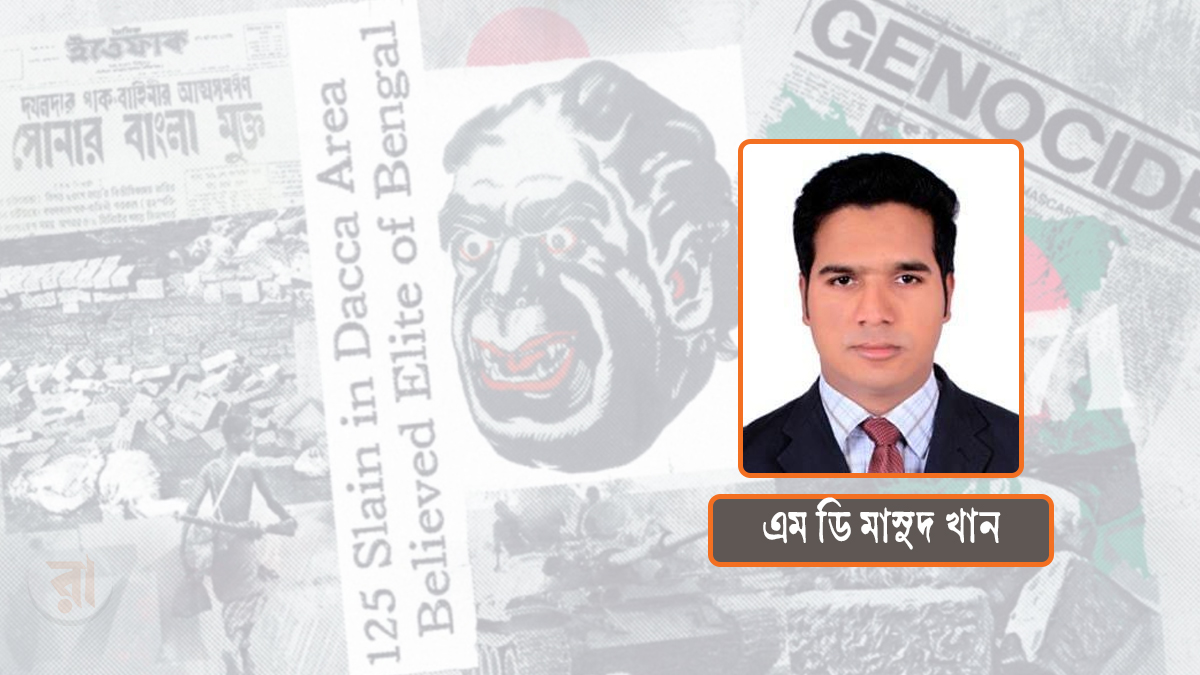
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে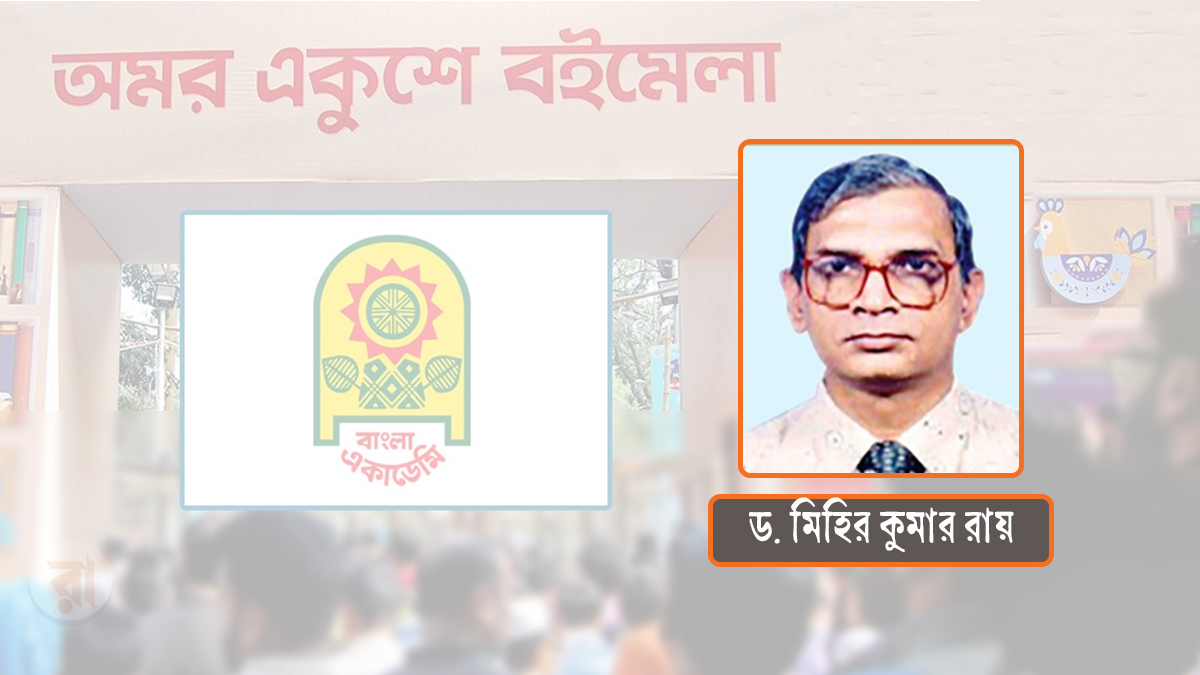
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে