
মো. কাফি খান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা এক বিশাল ও অপরিহার্য অংশ। এই শ্রমিক— যারা মূলত কৃষিক্ষেত্র, নির্মাণ, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থালি কাজ ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত— দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাদের অবদানকে উপেক্ষা করা সামগ্রিক অর্থনীতির একটি অসম্পূর্ণ চিত্রায়ণ করবে। আসুন, কিছু খাঁটি তথ্য ও পরিসংখ্যানের আলোকে এই অবদানের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা যাক।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২’ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এই বিপুলসংখ্যক কর্মজীবী দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকার প্রধান উৎস। এই খাতটি বিশেষত নারী, অভিবাসী ও তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।
নদীভাঙনে জমি হারানো রিনা বেগমের মতো লাখ লাখ মানুষ শহরে এসে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে তাদের জীবনধারণ করছেন। যদি এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত না থাকত, তবে দেশের দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেত।
বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান প্রায় ৪০ থেকে ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ২০০৯ সালের একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১২ অর্থবছরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জিডিপির আকার ছিল ৪৩ শতাংশ। কৃষি, মৎস্য, বাণিজ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পে এই খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, যেখানে মূলধন বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম।
অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজারগুলো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে। রাস্তার বিক্রেতা থেকে শুরু করে ছোট কারিগর পর্যন্ত যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, তারা প্রায়শই সুপারমার্কেট বা বড় ব্যবসার তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করে। দর্জির দোকানে স্বল্প খরচে পোশাক তৈরি করা অথবা স্থানীয় বাজারে তাজা সবজি কেনা— এ সবই অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির মাধ্যমে সম্ভব হয়, যা জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্মস্থান। স্বল্প পুঁজি ও নমনীয় কাঠামোর কারণে অনেকেই এখানে ছোট আকারের ব্যবসা শুরু করতে এবং নিজেদের উদ্ভাবনী ধারণা পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। ট্রেনে চানাচুর বিক্রি করা থেকে শুরু করে গ্রামীণ অঞ্চলে বাঁশের হস্তশিল্প তৈরি— এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে উদ্যোক্তার বিকাশ ও স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জীবন্ত রাখে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাত একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক আনুষ্ঠানিক ব্যবসা তাদের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য সহায়ক পরিষেবার জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রায়ই আনুষ্ঠানিক খাতের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ব্যবহার করে। এই আন্তঃনির্ভরশীলতা উভয় খাতের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে না, তবে তাদের উৎপাদিত অনেক পণ্য ও সেবা (যেমন— হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য) পর্যটনের মাধ্যমে বা ছোট পরিসরে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রায়ই ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মস্থলের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাদের কাজের পরিবেশ সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। আইনি সুরক্ষার অভাব ও দুর্বল প্রয়োগের কারণে তারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান তৈরি, জাতীয় উৎপাদনে অংশীদারি, সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছেন। তবে এই শ্রমিকদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের কাজের পরিবেশের উন্নয়ন এবং আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে তাদের সংযোগ বাড়ানো টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। নীতি নির্ধারকদের উচিত এমন পদক্ষেপ নেওয়া, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে এবং এই বিশাল কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।
বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ও জরুরি বিষয়। তাদের উন্নতি কেবল তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যও অত্যাবশ্যক। সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই বিশাল কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক ও ব্যাপক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা তাদের ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবে। বিদ্যমান শ্রম আইনের আওতায় এই শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
বাস্তবায়ন: জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বাড়ানো, যারা নিয়মিতভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রগুলো পরিদর্শন করবেন এবং শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। শ্রমিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং আইনি সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সম্ভাব্য সংশোধনীর প্রয়োজন), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন এবং সুপারিশ (যেমন— অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শোভন কাজ সংক্রান্ত সুপারিশ, ২০১৫)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন স্কিম, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা এবং বেকারত্ব ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা। দুর্যোগকালীন (যেমন— বন্যা, খরা) তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা।
বাস্তবায়ন: সরকারি বাজেট বাড়ানো এবং বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে একটি টেকসই সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠন করা। এই তহবিল বিতরণের প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করা এবং সরাসরি শ্রমিকদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। মোবাইল ব্যাংকিং ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে।
রেফারেন্স: জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র, ২০১৫; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও নীতিমালা (যেমন— বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা, যা তাদের উন্নত মানের কাজ পেতে বা নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে। তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা ও বাজার-চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া।
বাস্তবায়ন: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা। মোবাইল ট্রেনিং ভ্যান ব্যবহার করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্ব-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা।
রেফারেন্স: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১; বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও কার্যক্রম।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা (যেমন— সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট, বিমা) পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। তাদের আর্থিক সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করা।
বাস্তবায়ন: ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা, যেন তারা ন্যায্য সুদ হারে ঋণ প্রদান করে এবং শ্রমিকদের শোষণ না করে। মোবাইল ব্যাংকিং ও অন্যান্য ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে শ্রমিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা; বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (যেমন— ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক) এর কার্যক্রম ও নীতিমালা।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রগুলোতে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি চালু করা।
বাস্তবায়ন: নির্মাণ ক্ষেত্র, কারখানা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থলে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং এর নিয়মিত তদারকি করা। ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক স্থাপন করে শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
রেফারেন্স: জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন (যেমন— ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি) গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা।
বাস্তবায়ন: শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আইনি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেন তারা কার্যকরভাবে তাদের সদস্যদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে (যেমন— সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি) শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
রেফারেন্স: ট্রেড ইউনিয়ন আইন; আইএলও কনভেনশন নম্বর ৮৭ (সংগঠনের স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সুরক্ষা)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করা, যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।
বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা। গবেষণার ফলাফল নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে সহজলভ্য করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভে; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম।
আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (যেমন— শ্রম ও কর্মসংস্থান, অর্থ, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ) এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা।
স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ, নীতি বাস্তবায়ন এবং তাদের চাহিদা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করা।
বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো।
শ্রমিকদের অংশগ্রহণ: নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে সংশোধন আনা।
পরিশেষে বলা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন, কার্যকর বাস্তবায়ন ও সব স্তরের অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।
শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্থনীতির ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান ও আনুমানিক ৪০ থেকে ৬৪ শতাংশ জিডিপি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে আসে। যেখানে আনুষ্ঠানিক খাত তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে এবং জিডিপির একটি বৃহত্তর অংশ (প্রায় ৩৬ থেকে ৬০ শতাংশ) অবদান রাখে। তবে কর্মসংস্থানের বিশাল আকার ও অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসরে অংশগ্রহণের কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সামগ্রিক অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মসংস্থানই তৈরি করে না, বরং বিশেষ করে কৃষি ও সেবা খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে জাতীয় উৎপাদনের একটি বড় অংশও সরবরাহ করে।
লেখক: কোম্পানি সচিব, সিটি ব্যাংক পিএলসি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা এক বিশাল ও অপরিহার্য অংশ। এই শ্রমিক— যারা মূলত কৃষিক্ষেত্র, নির্মাণ, পরিবহন, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গৃহস্থালি কাজ ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত— দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাদের অবদানকে উপেক্ষা করা সামগ্রিক অর্থনীতির একটি অসম্পূর্ণ চিত্রায়ণ করবে। আসুন, কিছু খাঁটি তথ্য ও পরিসংখ্যানের আলোকে এই অবদানের একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা যাক।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ‘লেবার ফোর্স সার্ভে ২০২২’ অনুযায়ী, দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এই বিপুলসংখ্যক কর্মজীবী দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবিকার প্রধান উৎস। এই খাতটি বিশেষত নারী, অভিবাসী ও তরুণদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি ভূমিকা রাখে।
নদীভাঙনে জমি হারানো রিনা বেগমের মতো লাখ লাখ মানুষ শহরে এসে অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের মাধ্যমে তাদের জীবনধারণ করছেন। যদি এই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত না থাকত, তবে দেশের দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেত।
বিভিন্ন গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান প্রায় ৪০ থেকে ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ২০০৯ সালের একটি প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০১২ অর্থবছরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জিডিপির আকার ছিল ৪৩ শতাংশ। কৃষি, মৎস্য, বাণিজ্য ও ক্ষুদ্র শিল্পে এই খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি, যেখানে মূলধন বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম।
অপ্রাতিষ্ঠানিক বাজারগুলো স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে। রাস্তার বিক্রেতা থেকে শুরু করে ছোট কারিগর পর্যন্ত যারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, তারা প্রায়শই সুপারমার্কেট বা বড় ব্যবসার তুলনায় কম দামে পণ্য বিক্রি করে। দর্জির দোকানে স্বল্প খরচে পোশাক তৈরি করা অথবা স্থানীয় বাজারে তাজা সবজি কেনা— এ সবই অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির মাধ্যমে সম্ভব হয়, যা জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্মস্থান। স্বল্প পুঁজি ও নমনীয় কাঠামোর কারণে অনেকেই এখানে ছোট আকারের ব্যবসা শুরু করতে এবং নিজেদের উদ্ভাবনী ধারণা পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। ট্রেনে চানাচুর বিক্রি করা থেকে শুরু করে গ্রামীণ অঞ্চলে বাঁশের হস্তশিল্প তৈরি— এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে উদ্যোক্তার বিকাশ ও স্থানীয় পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে জীবন্ত রাখে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাত একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অনেক আনুষ্ঠানিক ব্যবসা তাদের কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ বা অন্যান্য সহায়ক পরিষেবার জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রায়ই আনুষ্ঠানিক খাতের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা ব্যবহার করে। এই আন্তঃনির্ভরশীলতা উভয় খাতের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে না, তবে তাদের উৎপাদিত অনেক পণ্য ও সেবা (যেমন— হস্তশিল্প, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য) পর্যটনের মাধ্যমে বা ছোট পরিসরে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে।
অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রায়ই ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও কর্মস্থলের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাদের কাজের পরিবেশ সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। আইনি সুরক্ষার অভাব ও দুর্বল প্রয়োগের কারণে তারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন।
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান তৈরি, জাতীয় উৎপাদনে অংশীদারি, সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য ও সেবা সরবরাহ এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছেন। তবে এই শ্রমিকদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের কাজের পরিবেশের উন্নয়ন এবং আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সঙ্গে তাদের সংযোগ বাড়ানো টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। নীতি নির্ধারকদের উচিত এমন পদক্ষেপ নেওয়া, যা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে এবং এই বিশাল কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে।
বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি বিশাল অংশ জুড়ে থাকা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ও জরুরি বিষয়। তাদের উন্নতি কেবল তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কল্যাণের জন্যই অপরিহার্য নয়, বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যও অত্যাবশ্যক। সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই বিশাল কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য একটি পৃথক ও ব্যাপক আইনি কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা তাদের ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, এবং সামাজিক সুরক্ষার অধিকার নিশ্চিত করবে। বিদ্যমান শ্রম আইনের আওতায় এই শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তির সুযোগও পর্যালোচনা করা যেতে পারে।
বাস্তবায়ন: জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ বাড়ানো, যারা নিয়মিতভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রগুলো পরিদর্শন করবেন এবং শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। শ্রমিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে (এনজিও) শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং আইনি সহায়তা প্রদানে উৎসাহিত করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সম্ভাব্য সংশোধনীর প্রয়োজন), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) কনভেনশন এবং সুপারিশ (যেমন— অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে শোভন কাজ সংক্রান্ত সুপারিশ, ২০১৫)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা, পেনশন স্কিম, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা এবং বেকারত্ব ভাতার মতো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা। দুর্যোগকালীন (যেমন— বন্যা, খরা) তাদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করা।
বাস্তবায়ন: সরকারি বাজেট বাড়ানো এবং বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারির মাধ্যমে একটি টেকসই সামাজিক সুরক্ষা তহবিল গঠন করা। এই তহবিল বিতরণের প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করা এবং সরাসরি শ্রমিকদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। মোবাইল ব্যাংকিং ও অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভাতা প্রদান কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে।
রেফারেন্স: জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলপত্র, ২০১৫; বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও নীতিমালা (যেমন— বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা, যা তাদের উন্নত মানের কাজ পেতে বা নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে। তথ্যপ্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা ও বাজার-চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেওয়া।
বাস্তবায়ন: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা। মোবাইল ট্রেনিং ভ্যান ব্যবহার করে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্ব-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা।
রেফারেন্স: জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১; বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও কার্যক্রম।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা (যেমন— সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট, বিমা) পাওয়ার সুযোগ তৈরি করা। তাদের আর্থিক সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচি পরিচালনা করা।
বাস্তবায়ন: ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা, যেন তারা ন্যায্য সুদ হারে ঋণ প্রদান করে এবং শ্রমিকদের শোষণ না করে। মোবাইল ব্যাংকিং ও অন্যান্য ডিজিটাল আর্থিক প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার বাড়িয়ে শ্রমিকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ নীতিমালা; বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা (যেমন— ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক) এর কার্যক্রম ও নীতিমালা।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রগুলোতে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচি চালু করা।
বাস্তবায়ন: নির্মাণ ক্ষেত্র, কারখানা এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কর্মস্থলে নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা এবং এর নিয়মিত তদারকি করা। ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য ক্লিনিক স্থাপন করে শ্রমিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
রেফারেন্স: জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন (যেমন— ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি) গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করা।
বাস্তবায়ন: শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আইনি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেন তারা কার্যকরভাবে তাদের সদস্যদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে পারে। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে (যেমন— সরকার, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি) শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
রেফারেন্স: ট্রেড ইউনিয়ন আইন; আইএলও কনভেনশন নম্বর ৮৭ (সংগঠনের স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সুরক্ষা)।
নীতি: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করা, যা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য।
বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ওপর নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করা। গবেষণার ফলাফল নীতি নির্ধারক এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে সহজলভ্য করা।
রেফারেন্স: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভে; বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম।
আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (যেমন— শ্রম ও কর্মসংস্থান, অর্থ, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ) এবং সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা।
স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ, নীতি বাস্তবায়ন এবং তাদের চাহিদা পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উৎসাহিত করা।
বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতা: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো।
শ্রমিকদের অংশগ্রহণ: নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন: গৃহীত নীতি ও কর্মসূচির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং প্রয়োজনে সংশোধন আনা।
পরিশেষে বলা যায়, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন, কার্যকর বাস্তবায়ন ও সব স্তরের অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।
শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্থনীতির ৮৫ শতাংশ কর্মসংস্থান ও আনুমানিক ৪০ থেকে ৬৪ শতাংশ জিডিপি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকে আসে। যেখানে আনুষ্ঠানিক খাত তুলনামূলকভাবে কমসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে এবং জিডিপির একটি বৃহত্তর অংশ (প্রায় ৩৬ থেকে ৬০ শতাংশ) অবদান রাখে। তবে কর্মসংস্থানের বিশাল আকার ও অর্থনীতির বিস্তৃত পরিসরে অংশগ্রহণের কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের সামগ্রিক অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মসংস্থানই তৈরি করে না, বরং বিশেষ করে কৃষি ও সেবা খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে জাতীয় উৎপাদনের একটি বড় অংশও সরবরাহ করে।
লেখক: কোম্পানি সচিব, সিটি ব্যাংক পিএলসি
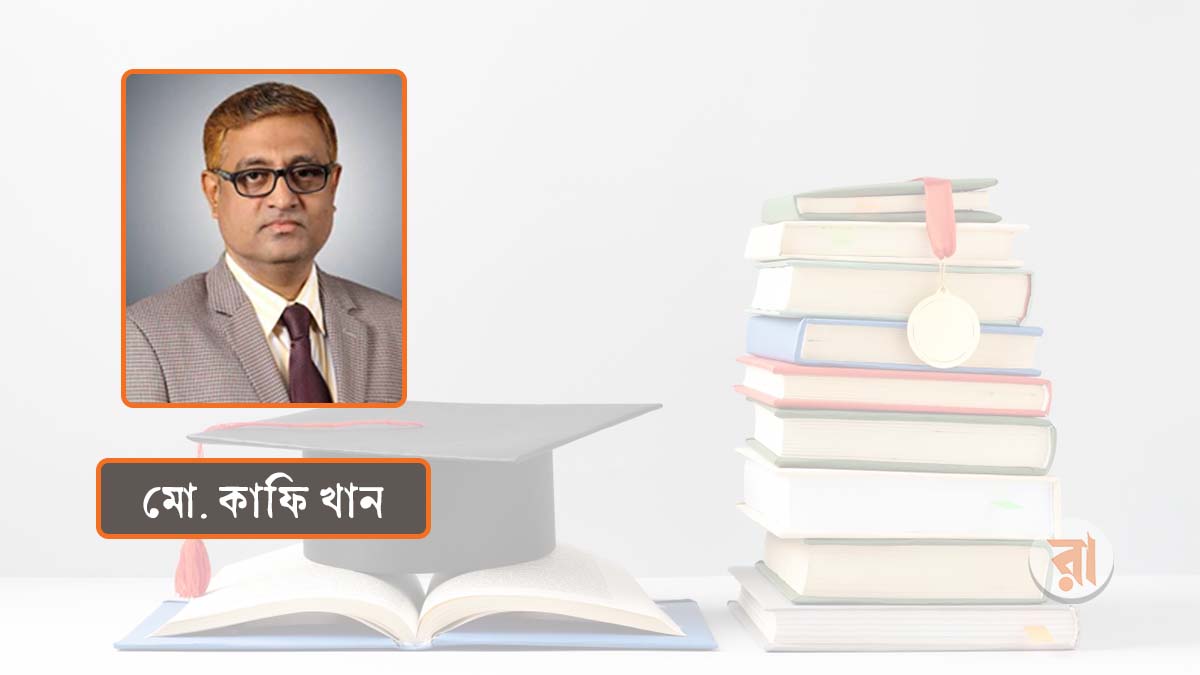
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই একাডেমিক মেরিটোক্রেসিকে (বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, মূল্যায়ন ও নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে শুধু যোগ্যতা ও কাজের মানের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত পরিচয়, রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবিরের ভিত্তিতে নয়) যথাযথভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
৪ দিন আগে
একজন উপদেষ্টার কাছ থেকে আমরা আশা করি নীতিগত সততা, সংস্কারের সাহস এবং মেধাবীদের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা। কিন্তু এখানে দেখা গেল উল্টো চিত্র— সংস্কারের প্রস্তাবকে শাস্তি দিয়ে দমন করা হলো। নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়; নীরবতা এখানে পক্ষ নেওয়া। আর সেই পক্ষটি দুর্নীতির সুবিধাভোগীদের।
৫ দিন আগে
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বা সংস্কার অনিবার্য। সেই সংস্কারের স্পিরিট বা চেতনা আমি এখন বিএনপির রাজনীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই দেশের এ বাস্তবতায় জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিএনপির সঙ্গেই পথ চলাকে আমি শ্রেয় মনে করেছি এবং যোগদানের সিদ্ধান
৫ দিন আগে
বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজার আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে এখনো পিছিয়ে। বছরে ৩০-৪০ লাখ দেশীয় পর্যটক এলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নগণ্য। তুলনায় থাইল্যান্ড বছরে প্রায় চার কোটি বিদেশি পর্যটক থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে। আর মালদ্বীপ মাত্র ২০ লাখ পর্যটক থেকেই তার জিডিপ
৭ দিন আগে