
সাইমন মোহসিন

দেড় দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার পুনরারম্ভ হয়েছে। এই সূচনা দক্ষিণ এশীয় ভূ-রাজনীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ পুনর্বিন্যাসকে নির্দেশ করে। ২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র সচিব-স্তরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঐতিহাসিক টানাপড়েন অতিক্রম করে সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয় পক্ষের পারস্পরিক স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ইঙ্গিত বহন করে।
আলোচনায় অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে বিস্তারিত বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষ আলোচনায় সতর্ক কূটনৈতিক ভাষা প্রয়োগ করেছে। এই সতর্কতা ঐতিহাসিক অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের সঙ্গে সমকালীন পারস্পরিক স্বার্থ অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রতি উভয়পক্ষের তীক্ষ্ণ মনোনিবেশকে আখ্যায়িত করে।
অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অপরিহার্যতাই এই পুনরুজ্জীবিত সম্পৃক্ততার মূল চালিকাশক্তি। উভয় দেশই সহযোগিতার বাস্তবসম্মত ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। করাচি ও চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি শিপিং পরিষেবার পুনরারম্ভ এবং পাকিস্তানি বিমান সংস্থা ফ্লাই জিন্নাহ ও এয়ার সিয়ালের মাধ্যমে বিমান সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়নে উভয় পক্ষের অঙ্গীকারই প্রকাশ করে। এই অঙ্গীকার বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির আনুপাতিক বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতার বিচারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ উভয়ই তৈরি করেছে।
একই সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বিনিময় ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। এই বৈঠকের আগে পাকিস্তানের গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে নিরাপত্তা সহযোগিতায় সমান্তরাল অগ্রগতি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ উদ্বেগসমূহ মোকাবিলায় দুদেশের ইচ্ছাকেই নির্দেশ করে।
পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার সবচেয়ে সংবেদনশীল দিক ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত ইতিহাস, যা এখনো এই সম্পর্কের কূটনৈতিক পরিধি নির্ধারণ করে চলেছে। বাংলাদেশের দাবি— একাত্তরের জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, আনুমানিক ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন।
এই তিনটি বিষয় ঢাকার পক্ষ থেকে মৌলিক শর্ত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এই আলোচনায়। তবে পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিতে এ বিষয়গুলো ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, যদিও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর স্বীকার করেছে যে এসব বিষয় আলোচনায় উঠেছে। সরকারি বিবৃতিতে এগুলোর অনুপস্থিতি ইসলামাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এই ইস্যুগুলোতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপকেই নির্দেশ করে।
চলমান কূটনৈতিক অগ্রগতি উভয় পক্ষকে অব্যাহত সংলাপের সুযোগ করে দিলেও পাকিস্তানের জন্য এমন কোনো ইস্যুতে এখনই কোনো ধরনের সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়, যা দেশটির বৈদেশিক রিজার্ভের ওপর তাৎক্ষণিক আর্থিক প্রভাব ফেলবে কিংবা দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিচারে এমন বিষয় এখনই কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা, কিংবা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আলোচনায় বিষয়গুলো এখনই গুরুত্বারোপ করা হবে— এমনটি কূটনৈতিক সম্পর্কের এ পর্যায়ে প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়।
ঐতিহাসিক নজিরগুলো ভবিষ্যৎ আলোচনার সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করে। বিশেষত ১৯৭৪ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন তার সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত অন্যায়ের জন্য ‘গভীর অনুশোচনা’ প্রকাশ করেছিল। ওই অনুশোচনাপত্রে সতর্কতার সঙ্গে প্রণীত শব্দচয়ন বন্দি প্রত্যাবাসন ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সার্কে যোগদানের জন্য পর্যাপ্ত রাজনৈতিক অবকাশ তৈরি করেছিল।
এটি সত্য যে বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার জন্য এক অকপট ও প্রত্যক্ষ ক্ষমার দাবি বাংলাদেশের প্রাপ্য। তবে ১৯৭৪ সালের প্রদত্ত পরিমার্জিত কূটনৈতিক শব্দবন্ধ আপাতদৃষ্টিতে অসমাধানযোগ্য অবস্থানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে।
সমসাময়িক সময়ে অনুরূপ পদক্ষেপের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক আস্থা বাড়ানোর মতো ব্যবস্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। এর মধ্যে যৌথ ঐতিহাসিক গবেষণা উদ্যোগ, স্মারক প্রকল্প, বা ১৯৭১ সাল নিয়ে শিক্ষামূলক বিনিময় কর্মসূচি হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ সময়ের সঙ্গে আরও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ও সম্পর্কোন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করবে।
উভয় দেশের কৌশলগত বিবেচনা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে অঞ্চলের ক্ষমতা-সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখে। পাকিস্তানের এই সম্পৃক্ততা ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের বিবর্তনের মধ্যে আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্য আনার বৃহত্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বহু-মেরুকৃত আঞ্চলিক পরিবেশে বাংলাদেশ তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন সর্বাধিক করতে চায়।
সার্ক নিয়ে পারস্পরিক সমর্থন বর্তমান স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ করে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন পথ তৈরির সম্ভাবনা রাখে। ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে বিকাশমান নিরাপত্তা সহযোগিতা অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির কৌশলগত হিসাব-নিকাশেও প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষত ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে।
অগ্রগতির পথে প্রয়োজন সূক্ষ্ম কূটনৈতিক কৌশল, যা সম্পর্কোন্নয়নের জন্য অপরিহার্যতা এবং বাস্তবভিত্তিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা উভয়ই স্বীকার করে। ধাপে ধাপে অগ্রগতি সম্ভব। সমান্তরাল পন্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত স্বার্থ নিশ্চিত করে— এমন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্কের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।
পাশাপাশি ঐতিহাসিক ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য নিয়মিত সংলাপের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও প্রয়োজন। নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা অবশিষ্ট ব্যবধান দূর করতে সহায়ক হতে পারে, বিশেষত ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য ভাষ্য প্রণয়নের ক্ষেত্রে। পারস্পরিক সহযোগিতা ক্ষেত্রের জন্য কার্যকর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ও একটি উচ্চ পর্যায়ের ঐতিহাসিক সংলাপ কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বাস্তবায়ন হতে পারে।
এই কূটনৈতিক সংযোগের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে সমকালীন সহযোগিতা ও ঐতিহাসিক পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে। বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির বিচারে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বিকশিত হতে পারে। তবে সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে উভয় দেশের সম্মিলিত অতীত স্মৃতির মধ্যে বিদ্যমান অসমতাগুলো সমাধানের মাধ্যমে।
পাকিস্তানকে এই কঠিন প্রশ্নগুলো ধাপে ধাপে মোকাবেলা করতে হবে। যদি আমরা অনুমান করে নিই যে পাকিস্তানের শীর্ষ নেতারা এই ইস্যুগুলো সমাধান করতে আগ্রহী, এই উত্তরণ স্থায়ী স্বাভাবিকীকরণের রূপ নেবে নাকি অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বোঝার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে— তা বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান ও কূটনীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সামর্থ্যই নির্ধারণ করবে। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতায় গুরুত্বারোপ করা আঞ্চলিক অংশীদারদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই আলোচনা প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।
এই সূক্ষ্ম কূটনৈতিক প্রক্রিয়াটি কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের বিষয় নয়। এটি একটি সম্ভাব্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যে কীভাবে রাষ্ট্রগুলো ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার ও সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির সংযোগস্থল বিন্যাস করতে পারে।
সংঘাত-পরবর্তী সম্পর্কের উন্নয়নে সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই দুই সরকারের আগামী পর্যায়ের সম্পৃক্ততায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করবে। আর এর প্রভাব উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও সুদূরপ্রসারী।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান কূটনৈতিক উত্তরণের এই প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ও সমকালীন বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রচনার এক জটিল পরীক্ষা। উভয় দেশের সক্ষমতা নির্ধারণ করবে এটি কেবল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার নমুনা, নাকি সংঘাত-পরবর্তী সম্পর্কের একটি মডেল হয়ে উঠবে। এই পুনর্মিলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গতিপথকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করবে।
লেখক: রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

দেড় দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার পুনরারম্ভ হয়েছে। এই সূচনা দক্ষিণ এশীয় ভূ-রাজনীতির একটি তাৎপর্যপূর্ণ পুনর্বিন্যাসকে নির্দেশ করে। ২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র সচিব-স্তরের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ঐতিহাসিক টানাপড়েন অতিক্রম করে সহযোগিতার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উভয় পক্ষের পারস্পরিক স্বীকৃতি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ইঙ্গিত বহন করে।
আলোচনায় অর্থনৈতিক, কৌশলগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রসমূহে বিস্তারিত বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে। তা সত্ত্বেও উভয় পক্ষ আলোচনায় সতর্ক কূটনৈতিক ভাষা প্রয়োগ করেছে। এই সতর্কতা ঐতিহাসিক অমীমাংসিত বিষয়গুলো সমাধানের সঙ্গে সমকালীন পারস্পরিক স্বার্থ অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় জটিল সামঞ্জস্য বজায় রাখার প্রতি উভয়পক্ষের তীক্ষ্ণ মনোনিবেশকে আখ্যায়িত করে।
অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অপরিহার্যতাই এই পুনরুজ্জীবিত সম্পৃক্ততার মূল চালিকাশক্তি। উভয় দেশই সহযোগিতার বাস্তবসম্মত ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে। করাচি ও চট্টগ্রামের মধ্যে সরাসরি শিপিং পরিষেবার পুনরারম্ভ এবং পাকিস্তানি বিমান সংস্থা ফ্লাই জিন্নাহ ও এয়ার সিয়ালের মাধ্যমে বিমান সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা বাণিজ্যিক অবকাঠামো উন্নয়নে উভয় পক্ষের অঙ্গীকারই প্রকাশ করে। এই অঙ্গীকার বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির আনুপাতিক বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতার বিচারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের জন্য চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ উভয়ই তৈরি করেছে।
একই সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বিনিময় ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। এই বৈঠকের আগে পাকিস্তানের গোয়েন্দা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মাধ্যমে নিরাপত্তা সহযোগিতায় সমান্তরাল অগ্রগতি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ উদ্বেগসমূহ মোকাবিলায় দুদেশের ইচ্ছাকেই নির্দেশ করে।
পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের আলোচনার সবচেয়ে সংবেদনশীল দিক ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত ইতিহাস, যা এখনো এই সম্পর্কের কূটনৈতিক পরিধি নির্ধারণ করে চলেছে। বাংলাদেশের দাবি— একাত্তরের জন্য পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা, আনুমানিক ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলার আর্থিক ক্ষতিপূরণ এবং আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন।
এই তিনটি বিষয় ঢাকার পক্ষ থেকে মৌলিক শর্ত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে এই আলোচনায়। তবে পাকিস্তান সরকারের বিবৃতিতে এ বিষয়গুলো ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, যদিও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর স্বীকার করেছে যে এসব বিষয় আলোচনায় উঠেছে। সরকারি বিবৃতিতে এগুলোর অনুপস্থিতি ইসলামাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এই ইস্যুগুলোতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপকেই নির্দেশ করে।
চলমান কূটনৈতিক অগ্রগতি উভয় পক্ষকে অব্যাহত সংলাপের সুযোগ করে দিলেও পাকিস্তানের জন্য এমন কোনো ইস্যুতে এখনই কোনো ধরনের সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়, যা দেশটির বৈদেশিক রিজার্ভের ওপর তাৎক্ষণিক আর্থিক প্রভাব ফেলবে কিংবা দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক বাস্তবতা বিচারে এমন বিষয় এখনই কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করা, কিংবা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আলোচনায় বিষয়গুলো এখনই গুরুত্বারোপ করা হবে— এমনটি কূটনৈতিক সম্পর্কের এ পর্যায়ে প্রত্যাশা করা সমীচীন নয়।
ঐতিহাসিক নজিরগুলো ভবিষ্যৎ আলোচনার সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করে। বিশেষত ১৯৭৪ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন তার সামরিক বাহিনী দ্বারা সংঘটিত অন্যায়ের জন্য ‘গভীর অনুশোচনা’ প্রকাশ করেছিল। ওই অনুশোচনাপত্রে সতর্কতার সঙ্গে প্রণীত শব্দচয়ন বন্দি প্রত্যাবাসন ও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সার্কে যোগদানের জন্য পর্যাপ্ত রাজনৈতিক অবকাশ তৈরি করেছিল।
এটি সত্য যে বাংলাদেশের মানুষকে ১৯৭১ সালে যে অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার জন্য এক অকপট ও প্রত্যক্ষ ক্ষমার দাবি বাংলাদেশের প্রাপ্য। তবে ১৯৭৪ সালের প্রদত্ত পরিমার্জিত কূটনৈতিক শব্দবন্ধ আপাতদৃষ্টিতে অসমাধানযোগ্য অবস্থানগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে।
সমসাময়িক সময়ে অনুরূপ পদক্ষেপের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক আস্থা বাড়ানোর মতো ব্যবস্থা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। এর মধ্যে যৌথ ঐতিহাসিক গবেষণা উদ্যোগ, স্মারক প্রকল্প, বা ১৯৭১ সাল নিয়ে শিক্ষামূলক বিনিময় কর্মসূচি হতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ সময়ের সঙ্গে আরও তাৎপর্যপূর্ণ সংযোগ ও সম্পর্কোন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি তৈরি করবে।
উভয় দেশের কৌশলগত বিবেচনা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে অঞ্চলের ক্ষমতা-সমীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রাখে। পাকিস্তানের এই সম্পৃক্ততা ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের বিবর্তনের মধ্যে আঞ্চলিক অংশীদারিত্বের বৈচিত্র্য আনার বৃহত্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান বহু-মেরুকৃত আঞ্চলিক পরিবেশে বাংলাদেশ তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন সর্বাধিক করতে চায়।
সার্ক নিয়ে পারস্পরিক সমর্থন বর্তমান স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ করে আঞ্চলিক সহযোগিতার নতুন পথ তৈরির সম্ভাবনা রাখে। ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে বিকাশমান নিরাপত্তা সহযোগিতা অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির কৌশলগত হিসাব-নিকাশেও প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষত ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে।
অগ্রগতির পথে প্রয়োজন সূক্ষ্ম কূটনৈতিক কৌশল, যা সম্পর্কোন্নয়নের জন্য অপরিহার্যতা এবং বাস্তবভিত্তিক রাজনীতির সীমাবদ্ধতা উভয়ই স্বীকার করে। ধাপে ধাপে অগ্রগতি সম্ভব। সমান্তরাল পন্থায় পারস্পরিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত স্বার্থ নিশ্চিত করে— এমন ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্কের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।
পাশাপাশি ঐতিহাসিক ইস্যুগুলো সমাধানের জন্য নিয়মিত সংলাপের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাও প্রয়োজন। নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা অবশিষ্ট ব্যবধান দূর করতে সহায়ক হতে পারে, বিশেষত ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য ভাষ্য প্রণয়নের ক্ষেত্রে। পারস্পরিক সহযোগিতা ক্ষেত্রের জন্য কার্যকর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ও একটি উচ্চ পর্যায়ের ঐতিহাসিক সংলাপ কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বাস্তবায়ন হতে পারে।
এই কূটনৈতিক সংযোগের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে সমকালীন সহযোগিতা ও ঐতিহাসিক পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে। বর্তমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির বিচারে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সহযোগিতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বিকশিত হতে পারে। তবে সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নির্ভর করবে উভয় দেশের সম্মিলিত অতীত স্মৃতির মধ্যে বিদ্যমান অসমতাগুলো সমাধানের মাধ্যমে।
পাকিস্তানকে এই কঠিন প্রশ্নগুলো ধাপে ধাপে মোকাবেলা করতে হবে। যদি আমরা অনুমান করে নিই যে পাকিস্তানের শীর্ষ নেতারা এই ইস্যুগুলো সমাধান করতে আগ্রহী, এই উত্তরণ স্থায়ী স্বাভাবিকীকরণের রূপ নেবে নাকি অমীমাংসিত ঐতিহাসিক বোঝার দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে— তা বাংলাদেশের নীতিগত অবস্থান ও কূটনীতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার সামর্থ্যই নির্ধারণ করবে। দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতায় গুরুত্বারোপ করা আঞ্চলিক অংশীদারদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই আলোচনা প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।
এই সূক্ষ্ম কূটনৈতিক প্রক্রিয়াটি কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কোন্নয়নের বিষয় নয়। এটি একটি সম্ভাব্য উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যে কীভাবে রাষ্ট্রগুলো ঐতিহাসিক ন্যায়বিচার ও সমকালীন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির সংযোগস্থল বিন্যাস করতে পারে।
সংঘাত-পরবর্তী সম্পর্কের উন্নয়নে সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই দুই সরকারের আগামী পর্যায়ের সম্পৃক্ততায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করবে। আর এর প্রভাব উপমহাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আরও সুদূরপ্রসারী।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান কূটনৈতিক উত্তরণের এই প্রক্রিয়া ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা ও সমকালীন বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য রচনার এক জটিল পরীক্ষা। উভয় দেশের সক্ষমতা নির্ধারণ করবে এটি কেবল আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার নমুনা, নাকি সংঘাত-পরবর্তী সম্পর্কের একটি মডেল হয়ে উঠবে। এই পুনর্মিলনের সাফল্য বা ব্যর্থতা দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গতিপথকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করবে।
লেখক: রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৭ দিন আগে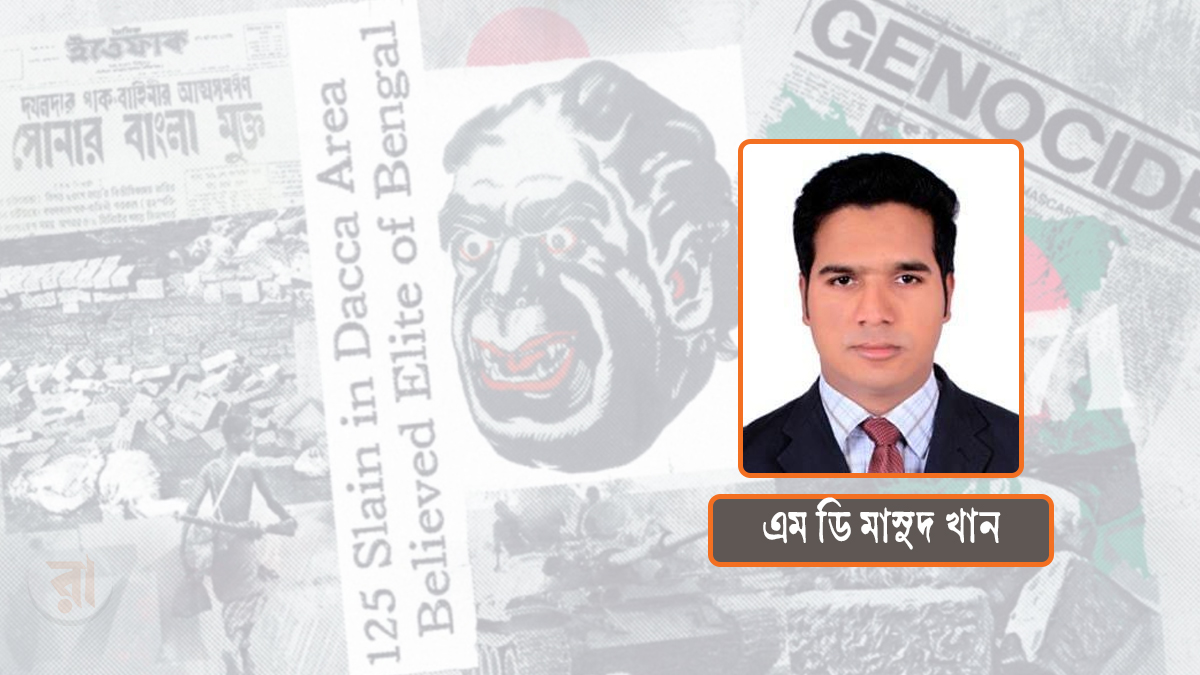
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে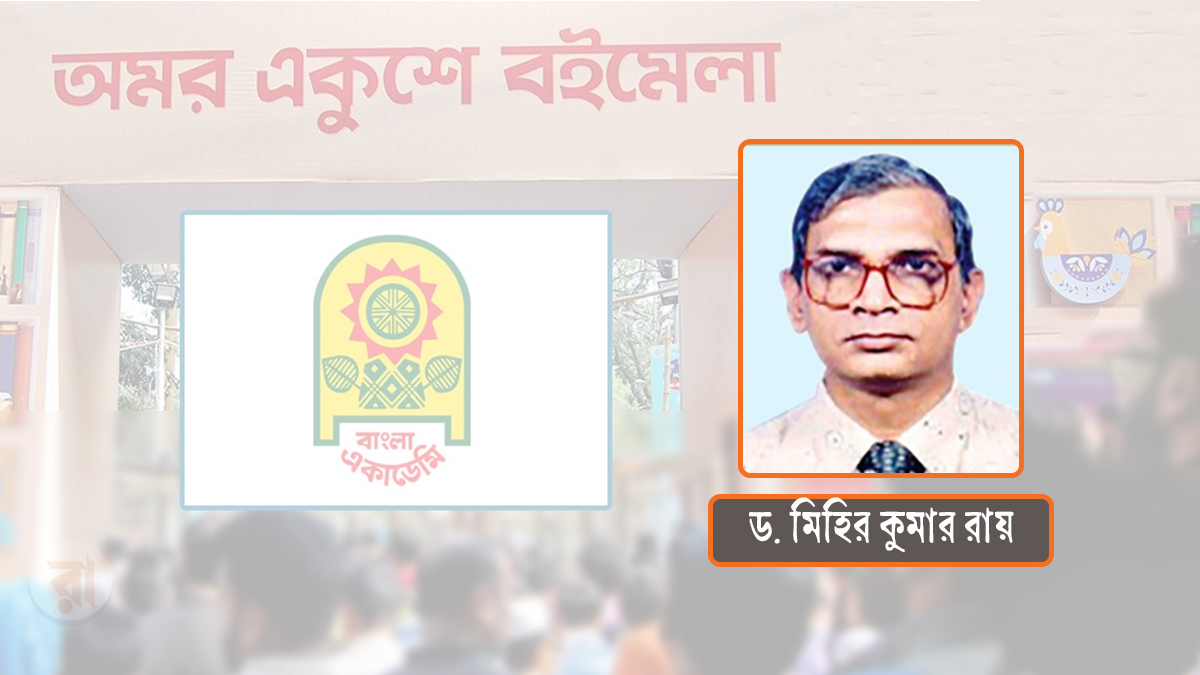
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১১ দিন আগে