
মো. কাফি খান

একটি জাতির উন্নয়নের ভিত্তি তার জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে, জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা (Demographic Stability) অর্জন করা এখন আর কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্থিতিশীলতা বলতে শুধু জন্ম ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায় না, বরং একটি দেশের বয়সভিত্তিক কাঠামো, ভৌগোলিক বণ্টন এবং জীবনযাত্রার মানের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করা। এই ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রধান শহরগুলোতে সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা থেকে সরে এসে দেশের জনমিতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ করা অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ধরনের নীতি গ্রহণ করে তাদের উন্নয়নকে সুষম করেছে, যা থেকে বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
বাংলাদেশ বর্তমানে এক অনন্য “জনসংখ্যার ডিভিডেন্ড” (Demographic Dividend) উপভোগ করছে, যেখানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। যদি এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া না যায়, তাহলে এই ডিভিডেন্ড বোঝা বা বিপদে পরিণত হতে পারে। জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে সরকার শ্রমবাজার, আবাসন এবং অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।
একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর চাপ কমে আসে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বাসস্থান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা সরকারকে এসব খাতে সম্পদ সুষমভাবে বণ্টন করতে সাহায্য করে, যা সকলের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।
বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যার সুষম বণ্টন এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে পরিবেশের ওপর চাপ কমে। এতে বনভূমি, জলাশয় এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা সহজ হয়, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটের মতো প্রধান শহরগুলোতে সকল অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই কেন্দ্রীকরণ গ্রাম এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলো থেকে শহরের দিকে ব্যাপক অভিবাসনের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে বড় শহরগুলোতে যানজট, আবাসন সংকট, পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে গ্রামীণ অঞ্চলগুলো মেধা ও শ্রমশক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই জনমিতিক বৈষম্য দূর করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ একটি কার্যকর কৌশল। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
দক্ষিণ কোরিয়া: একসময় দক্ষিণ কোরিয়া সিউল এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। এই সমস্যা মোকাবিলায় দেশটি ষাটের দশক থেকে “সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন” (Balanced Regional Development) নীতি গ্রহণ করে। এর আওতায় তারা প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তরের পাশাপাশি নতুন শহর (New Towns) গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় ও পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলো সিউলের বাইরে স্থানান্তর করে। দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, সুদূরপ্রসারী এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব।
চীন: চীন তার বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। তাদের ‘হুকুও’ (Hukou) বা পারিবারিক নিবন্ধন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে, সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উপকূল থেকে দূরে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones) ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা। এসব অঞ্চলে বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ আর শুধু বড় শহরে জড়ো হওয়ার পরিবর্তে নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের এই মডেল প্রমাণ করে যে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ জনমিতিক ভারসাম্য আনয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।
ব্রাজিল: ব্রাজিল তার বিশাল ভূখণ্ডে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। দেশের উত্তরাঞ্চলে জনসংখ্যা কম ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, যেখানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রিও ডি জেনেইরো এবং সাও পাওলোর মতো মেগাসিটিগুলোতে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ। এই বৈষম্য নিরসনের জন্য ব্রাজিল বিভিন্ন সময়ে “জাতীয় আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি” (National Policy for Regional Development) গ্রহণ করেছে। এই নীতির মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে অবকাঠামো, শিল্প এবং সামাজিক সেবা খাতে বিনিয়োগ করা হয়। ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণই যথেষ্ট নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সুদূরপ্রসারী নীতি ও বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।
সিঙ্গাপুর: সিঙ্গাপুর যদিও একটি ছোট দেশ, কিন্তু তাদের জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে। সিঙ্গাপুর তাদের আবাসিক ব্যবস্থা (HDB Flats) এবং কর্মসংস্থান পরিকল্পনা এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব পুরো দ্বীপজুড়ে সুষমভাবে বণ্টিত হয়। তাদের “নিউ টাউন” (New Town) পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি নতুন শহরেই আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়, যা জনগণের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে। এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় না।
মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া তার জনসংখ্যা বণ্টন নিয়ে সচেতন। দেশটি তার “লং টার্ম প্ল্যান” (Long Term Plan) এবং “জাতীয় জনসংখ্যা নীতি” (National Population Policy) এর মাধ্যমে জনসংখ্যাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করেছে। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো। বিশেষ করে, মালয়েশিয়া সরকার কুয়ালালামপুরের ওপর চাপ কমাতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে নতুন শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলেছে।
জার্মানি: জার্মানির ফেডারেল কাঠামো এবং “যৌথ ফেডারেল/রাজ্য টাস্ক ফোর্স ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ রিজিওনাল ইকোনমিক স্ট্রাকচার” (GRW) উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যগুলোকে সহায়তা করা হয়। এটি শুধু আঞ্চলিক বৈষম্যই কমায় না, দেশের সকল অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
জাপান: জাপান বর্তমানে বৃদ্ধজনসংখ্যা (Aging Population) এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের কারণে সৃষ্ট জনমিতিক সমস্যার মুখোমুখি। এই সমস্যা মোকাবিলায় “লোকাল রিভাইটালাইজেশন কো-অপারেটর” (Local Revitalization Cooperator) কর্মসূচি চালু করেছে, যেখানে তরুণ পেশাজীবীদের গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে তিন বছর কাজ করার জন্য বেতন ও আবাসন সুবিধা দেওয়া হয়। লক্ষ্য হলো গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তরুণদের শহরে ফেরার প্রবণতা কমানো।
ফ্রান্স: ফ্রান্স ঐতিহ্যগতভাবে একটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ছিল। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিক প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলোকে (Regions, Departments, Communes) আরও বেশি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছে। এটি স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে এবং জাতীয় সরকারের ওপর চাপ কমিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়া তার প্রধান দ্বীপ জাভার অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং দেশের অন্যান্য দ্বীপের কম জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনতে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই “ট্রান্সমাইগ্রেশন প্রোগ্রাম” (Transmigration Program) চালু করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাভা থেকে লাখ লাখ মানুষকে সুমাত্রা, কালিমান্তান ও পাপুয়ার মতো কম জনবহুল দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও এই কর্মসূচির কিছু সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব ছিল, এটি জনসংখ্যার বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং নতুন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র তৈরি করেছে।
কিউবা: কিউবা তার স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিশ্বে সুপরিচিত। তারা একটি শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে প্রতিটি পরিবারকে একজন পারিবারিক চিকিৎসক এবং একজন নার্স সেবা দেন। এই ব্যবস্থাটি শহরে বা গ্রামীণ অঞ্চলে সব জায়গাতেই কার্যকর, যার ফলে জনসংখ্যার ভৌগোলিক বণ্টন নির্বিশেষে সব নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা পায়। এটি শহরের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কমায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
সমন্বিত পরিকল্পনা: শুধুমাত্র প্রশাসনিক দপ্তর স্থানান্তরের চেয়ে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ বেশি কার্যকর।
আঞ্চলিক বিনিয়োগ: পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোতে নতুন শিল্প পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে হবে, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।
শিক্ষার প্রসার: গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকার বাইরে স্থাপন করতে হবে।
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: উন্নত সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণকে সফল করতে পারে।
বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা অর্জন একটি বহুমুখী চ্যালেঞ্জ, যার সমাধান লুকিয়ে আছে সমন্বিত পরিকল্পনা, সুষম নীতি এবং কার্যকর সুশাসনের মধ্যে। এই তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ একটি মূল কৌশল হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া এবং কিউবার মতো দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রধান শহরগুলোর ওপর থেকে চাপ কমিয়ে জনমিতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে সুযোগের সমতা তৈরি করা গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও সুষম ও টেকসই হবে। এর মাধ্যমে কেবল শহুরে জীবনের সংকটই হ্রাস পাবে না, বরং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে।
লেখক: কোম্পানি সচিব, সিটি ব্যাংক পিএলসি

একটি জাতির উন্নয়নের ভিত্তি তার জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে, জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা (Demographic Stability) অর্জন করা এখন আর কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি কৌশল নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সুশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই স্থিতিশীলতা বলতে শুধু জন্ম ও মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায় না, বরং একটি দেশের বয়সভিত্তিক কাঠামো, ভৌগোলিক বণ্টন এবং জীবনযাত্রার মানের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা নিশ্চিত করা। এই ভারসাম্য অর্জনের জন্য প্রধান শহরগুলোতে সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা থেকে সরে এসে দেশের জনমিতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে সুযোগ-সুবিধা বিকেন্দ্রীকরণ করা অপরিহার্য। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ধরনের নীতি গ্রহণ করে তাদের উন্নয়নকে সুষম করেছে, যা থেকে বাংলাদেশ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
বাংলাদেশ বর্তমানে এক অনন্য “জনসংখ্যার ডিভিডেন্ড” (Demographic Dividend) উপভোগ করছে, যেখানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। যদি এই কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া না যায়, তাহলে এই ডিভিডেন্ড বোঝা বা বিপদে পরিণত হতে পারে। জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে সরকার শ্রমবাজার, আবাসন এবং অবকাঠামো খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।
একটি স্থিতিশীল জনসংখ্যার কারণে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপর চাপ কমে আসে। যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে প্রতিটি নাগরিকের জন্য মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বাসস্থান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা সরকারকে এসব খাতে সম্পদ সুষমভাবে বণ্টন করতে সাহায্য করে, যা সকলের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে।
বাংলাদেশের সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যার সুষম বণ্টন এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হলে পরিবেশের ওপর চাপ কমে। এতে বনভূমি, জলাশয় এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা সহজ হয়, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।
দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটের মতো প্রধান শহরগুলোতে সকল অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এই কেন্দ্রীকরণ গ্রাম এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলো থেকে শহরের দিকে ব্যাপক অভিবাসনের জন্ম দিয়েছে। এর ফলে বড় শহরগুলোতে যানজট, আবাসন সংকট, পরিবেশ দূষণ ও সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে গ্রামীণ অঞ্চলগুলো মেধা ও শ্রমশক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এই জনমিতিক বৈষম্য দূর করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ একটি কার্যকর কৌশল। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
দক্ষিণ কোরিয়া: একসময় দক্ষিণ কোরিয়া সিউল এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। এই সমস্যা মোকাবিলায় দেশটি ষাটের দশক থেকে “সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন” (Balanced Regional Development) নীতি গ্রহণ করে। এর আওতায় তারা প্রশাসনিক রাজধানী স্থানান্তরের পাশাপাশি নতুন শহর (New Towns) গড়ে তোলে এবং বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় ও পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলো সিউলের বাইরে স্থানান্তর করে। দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়, সুদূরপ্রসারী এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব।
চীন: চীন তার বিপুল জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করেছে। তাদের ‘হুকুও’ (Hukou) বা পারিবারিক নিবন্ধন ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার মধ্যে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে, সবচেয়ে কার্যকর পদক্ষেপ ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে উপকূল থেকে দূরে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zones) ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলা। এসব অঞ্চলে বিপুল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় মানুষ আর শুধু বড় শহরে জড়ো হওয়ার পরিবর্তে নতুন অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের এই মডেল প্রমাণ করে যে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ জনমিতিক ভারসাম্য আনয়নে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।
ব্রাজিল: ব্রাজিল তার বিশাল ভূখণ্ডে আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার। দেশের উত্তরাঞ্চলে জনসংখ্যা কম ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, যেখানে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে রিও ডি জেনেইরো এবং সাও পাওলোর মতো মেগাসিটিগুলোতে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ। এই বৈষম্য নিরসনের জন্য ব্রাজিল বিভিন্ন সময়ে “জাতীয় আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতি” (National Policy for Regional Development) গ্রহণ করেছে। এই নীতির মাধ্যমে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে অবকাঠামো, শিল্প এবং সামাজিক সেবা খাতে বিনিয়োগ করা হয়। ব্রাজিলের অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণই যথেষ্ট নয়, বরং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে সুদূরপ্রসারী নীতি ও বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন।
সিঙ্গাপুর: সিঙ্গাপুর যদিও একটি ছোট দেশ, কিন্তু তাদের জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা কৌশল থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিতে পারে। সিঙ্গাপুর তাদের আবাসিক ব্যবস্থা (HDB Flats) এবং কর্মসংস্থান পরিকল্পনা এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে জনসংখ্যার ঘনত্ব পুরো দ্বীপজুড়ে সুষমভাবে বণ্টিত হয়। তাদের “নিউ টাউন” (New Town) পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি নতুন শহরেই আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয়, যা জনগণের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে। এর ফলে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপ তৈরি হয় না।
মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া তার জনসংখ্যা বণ্টন নিয়ে সচেতন। দেশটি তার “লং টার্ম প্ল্যান” (Long Term Plan) এবং “জাতীয় জনসংখ্যা নীতি” (National Population Policy) এর মাধ্যমে জনসংখ্যাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করেছে। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক বৈষম্য কমানো। বিশেষ করে, মালয়েশিয়া সরকার কুয়ালালামপুরের ওপর চাপ কমাতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে নতুন শহর ও শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলেছে।
জার্মানি: জার্মানির ফেডারেল কাঠামো এবং “যৌথ ফেডারেল/রাজ্য টাস্ক ফোর্স ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ রিজিওনাল ইকোনমিক স্ট্রাকচার” (GRW) উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যগুলোকে সহায়তা করা হয়। এটি শুধু আঞ্চলিক বৈষম্যই কমায় না, দেশের সকল অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
জাপান: জাপান বর্তমানে বৃদ্ধজনসংখ্যা (Aging Population) এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের কারণে সৃষ্ট জনমিতিক সমস্যার মুখোমুখি। এই সমস্যা মোকাবিলায় “লোকাল রিভাইটালাইজেশন কো-অপারেটর” (Local Revitalization Cooperator) কর্মসূচি চালু করেছে, যেখানে তরুণ পেশাজীবীদের গ্রামীণ এলাকায় গিয়ে তিন বছর কাজ করার জন্য বেতন ও আবাসন সুবিধা দেওয়া হয়। লক্ষ্য হলো গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং তরুণদের শহরে ফেরার প্রবণতা কমানো।
ফ্রান্স: ফ্রান্স ঐতিহ্যগতভাবে একটি অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র ছিল। ১৯৮২ সাল থেকে শুরু হওয়া ধারাবাহিক প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারগুলোকে (Regions, Departments, Communes) আরও বেশি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা দিয়েছে। এটি স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে এবং জাতীয় সরকারের ওপর চাপ কমিয়েছে। এর ফলে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজ হয়েছে।
ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়া তার প্রধান দ্বীপ জাভার অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং দেশের অন্যান্য দ্বীপের কম জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আনতে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই “ট্রান্সমাইগ্রেশন প্রোগ্রাম” (Transmigration Program) চালু করেছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে জাভা থেকে লাখ লাখ মানুষকে সুমাত্রা, কালিমান্তান ও পাপুয়ার মতো কম জনবহুল দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও এই কর্মসূচির কিছু সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব ছিল, এটি জনসংখ্যার বণ্টনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং নতুন অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র তৈরি করেছে।
কিউবা: কিউবা তার স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিশ্বে সুপরিচিত। তারা একটি শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে প্রতিটি পরিবারকে একজন পারিবারিক চিকিৎসক এবং একজন নার্স সেবা দেন। এই ব্যবস্থাটি শহরে বা গ্রামীণ অঞ্চলে সব জায়গাতেই কার্যকর, যার ফলে জনসংখ্যার ভৌগোলিক বণ্টন নির্বিশেষে সব নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা পায়। এটি শহরের হাসপাতালগুলোর ওপর চাপ কমায় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।
বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারে।
সমন্বিত পরিকল্পনা: শুধুমাত্র প্রশাসনিক দপ্তর স্থানান্তরের চেয়ে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যসেবার বিকেন্দ্রীকরণ বেশি কার্যকর।
আঞ্চলিক বিনিয়োগ: পিছিয়ে থাকা জেলাগুলোতে নতুন শিল্প পার্ক ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করতে হবে, যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়।
শিক্ষার প্রসার: গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঢাকার বাইরে স্থাপন করতে হবে।
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন: উন্নত সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণকে সফল করতে পারে।
বাংলাদেশের জন্য জনসংখ্যাগত স্থিতিশীলতা অর্জন একটি বহুমুখী চ্যালেঞ্জ, যার সমাধান লুকিয়ে আছে সমন্বিত পরিকল্পনা, সুষম নীতি এবং কার্যকর সুশাসনের মধ্যে। এই তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণ একটি মূল কৌশল হিসেবে কাজ করে। দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ব্রাজিল, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া এবং কিউবার মতো দেশের অভিজ্ঞতা থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রধান শহরগুলোর ওপর থেকে চাপ কমিয়ে জনমিতিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলগুলোতে সুযোগের সমতা তৈরি করা গেলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও সুষম ও টেকসই হবে। এর মাধ্যমে কেবল শহুরে জীবনের সংকটই হ্রাস পাবে না, বরং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, যা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে।
লেখক: কোম্পানি সচিব, সিটি ব্যাংক পিএলসি

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে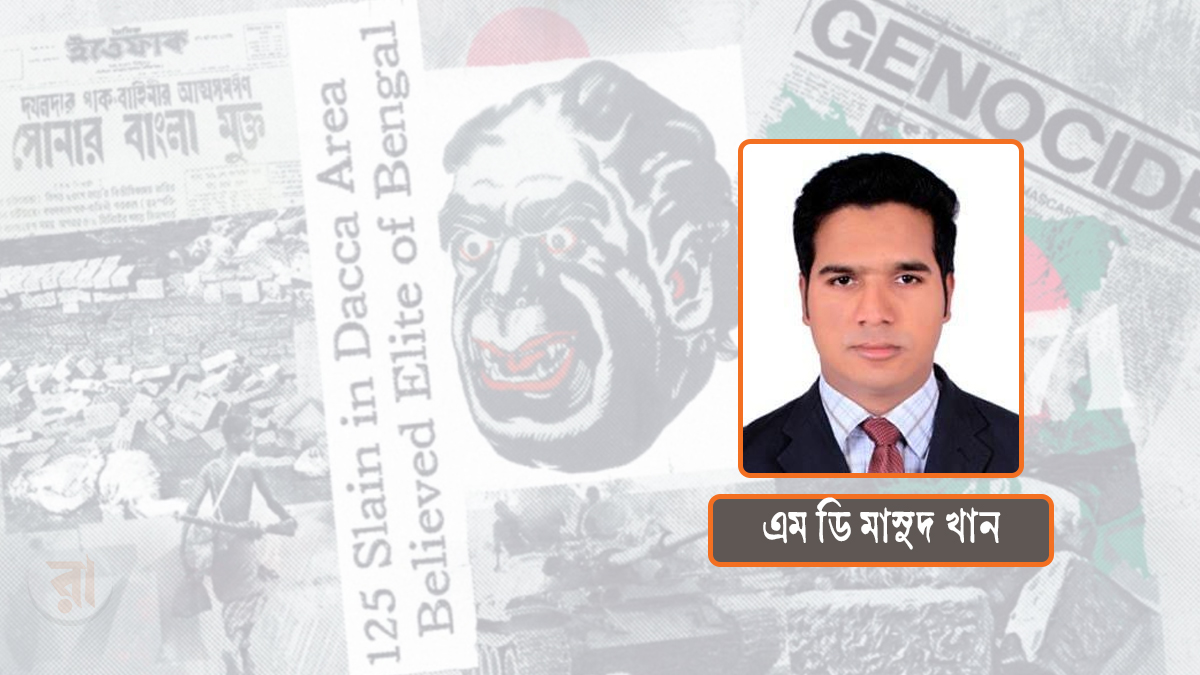
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে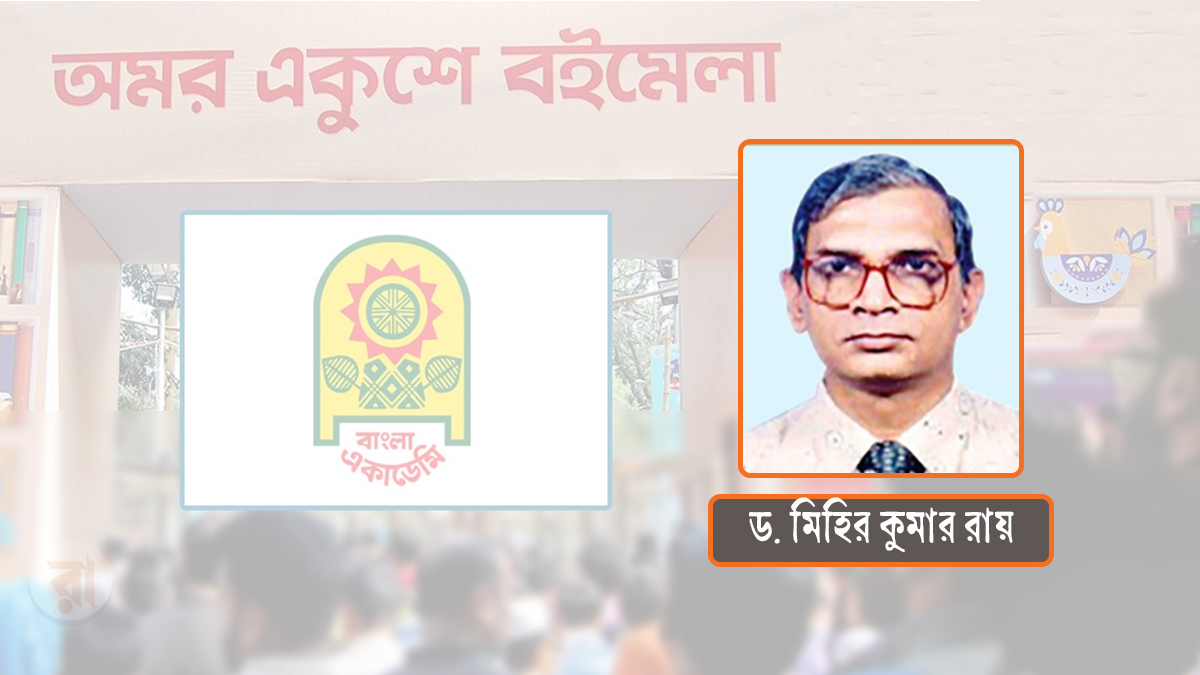
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে