
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মিলন
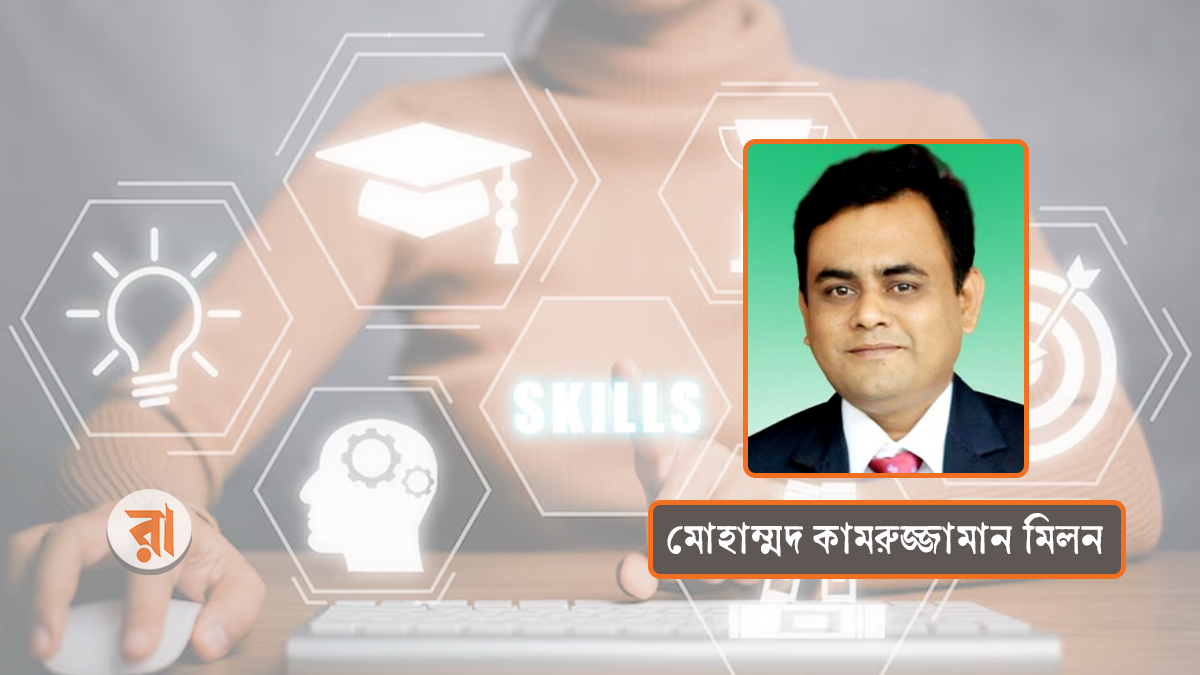
বাংলাদেশে এখন যে সংকটটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে তা কেবল বেকারত্ব নয়, বরং শিক্ষিত বেকারত্ব। প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ উপযুক্ত কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে শিল্প ও প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তারা একাধিকবার অভিযোগ করেছেন— ‘আমাদের দক্ষ কর্মীর অভাব।’
অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে দুটি সমস্যায় জর্জরিত— বেকারত্ব ও দক্ষতার ঘাটতি। এ বৈপরীত্যের মূল কারণ একটাই— আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো সনদকেন্দ্রিক, দক্ষতাকেন্দ্রিক নয়। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতি এরই মধ্যে বদলে গেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাত এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বাস্তব উদাহরণ।
গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানি— যেমন গুগল, আইবিএম, মাইক্রোসফট ও অ্যামাজন তাদের নিয়োগনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। একসময় প্রতিষ্ঠানগুলো চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করত, কিন্তু এখন তাদের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
২০১৮ সালে গুগল ‘Grow with Google’ নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করে, যেখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি ছাড়াই অংশগ্রহণ করা যায়। মাত্র ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা ডেটা অ্যানালিটিক্স, ইউএক্স ডিজাইন বা আইটি সাপোর্টে চাকরি পাচ্ছেন। গুগলের দাবি, এ প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের ৮০ শতাংশ ছয় মাসের মধ্যেই কর্মসংস্থান পেয়েছে।
একইভাবে আইবিএম তাদের ‘New Collar Jobs’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমন কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে যাদের হাতে বাস্তব প্রযুক্তিগত দক্ষতা আছে, কিন্তু ডিগ্রি নেই। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ কৃষ্ণা সরাসরি বলেছেন, ‘আমরা আর শুধু চার বছরের ডিগ্রিধারী খুঁজছি না, আমরা খুঁজছি যাদের হাতে বাস্তব দক্ষতা আছে।’
এ পরিবর্তন কোনো আকস্মিক পদক্ষেপ নয়। ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো উপলব্ধি করে, অনেক ডিগ্রিধারী প্রার্থী আসলে বাজারে অপ্রাসঙ্গিক। তারা তত্ত্ব জানে, কিন্তু প্রযুক্তি জানে না। তাই ২০১০ সালের পর থেকে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ‘Skills over Degrees’ নীতি গ্রহণ করে।
এর ফল এখন স্পষ্ট— ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আইটি খাতের প্রায় ৪৫ শতাংশ চাকরির বিজ্ঞাপনে ডিগ্রি আবশ্যিক ছিল না। ২০২৪ সালে এই হার অর্ধেক ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে আজ একজন প্রোগ্রামার বা ডেটা অ্যানালিস্টের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নয়, বরং বাস্তব দক্ষতাই মূল যোগ্যতা।
বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে একজন তরুণ তার দক্ষতা যাচাই করাতে পারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে, যেমন— কোর্সিয়া, এডএক্স বা ইউডেমি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের সার্টিফিকেটধারীরা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে গড়ে ৯০ থেকে ১২০ হাজার ডলার বেতন পাচ্ছেন।
একইভাবে গুগল ক্যারিয়ার সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা চাকরি পেতে গড়ে ছয় মাসেরও কম সময় নিচ্ছেন। এ ছাড়া গিটহাব বা কেগল প্রোফাইলের মাধ্যমে কেউ নিজের কোডিং দক্ষতা প্রমাণ করতে পারলেই মিলছে চাকরি। অর্থাৎ এখন আর প্রশ্ন নেই যে ‘তুমি কোথায় পড়েছ’, বরং প্রশ্নটা হলো ‘তুমি কী করতে পারো।’
কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো এমন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করছে যা ১০ বছর আগের শিল্প-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক প্রতিষ্ঠানে ল্যাব সুবিধা সীমিত, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা ইন্টার্নশিপ নেই। ফলাফল— শিক্ষার্থীরা কেবল বইয়ের জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বাস্তবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না।
বাংলাদেশের সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের (বেসিস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার নতুন আইটি পদ তৈরি হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ১০ হাজার। অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ পদ ফাঁকা থেকে যায়।
সমস্যার গভীরে গেলে দেখা যায় তিনটি বড় কারণ কাজ করছে। প্রথমত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম পুরোনো, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক বা ডেটা সায়েন্সের ব্যবহার সীমিত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় হাতে-কলমে কাজ শেখার সংস্কৃতি নেই। পরীক্ষার ফলাফলে মুখস্তবিদ্যা এখনো বড় প্রভাব রাখে। তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে এখনো ডিগ্রিকে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, দক্ষতাকে নয়। ফলে একজন তরুণ যদি বলে যে সে ফ্রিল্যান্সার বা ডেভেলপার, তখন অনেকেই ভাবে তার ঠিক ‘চাকরি নেই’।
এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে শেখার মতো অনেক কিছুই আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পসংযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (স্কিল ল্যাব) তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে।
দ্বিতীয়ত, ডিগ্রি অর্জনের আগে অন্তত ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা দরকার।
তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে যৌথ সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে জাতীয় ডিগ্রি পাবে, অন্যদিকে গুগল, মাইক্রোসফট বা আইবিএমের স্বীকৃত দক্ষতা অর্জন করবে।
চতুর্থত, নিয়োগদাতাদের মনোভাবও বদলাতে হবে। চাকরির বিজ্ঞাপনে ‘ন্যূনতম স্নাতক’ যোগ্যতা চাওয়ার বদলে ‘সমমানের দক্ষতা...’র উল্লেখ করা উচিত। এটি কেবল শব্দ পরিবর্তন নয়, এটি একটি নীতিগত সংস্কৃতি পরিবর্তনের সূচনা।
বিশ্ব এখন ‘স্কিল ইকোনমি’র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইইফ) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের অর্ধেক কর্মীকে নতুন করে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকবে ডেটা অ্যানালিটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার সিকিউরিটি ও ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে।
অর্থাৎ, যেসব দেশে তরুণ জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু তারা নতুন দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ, সেসব দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঝুঁকিটি এখানেই। যদি আমরা এখনই দক্ষতাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে না তুলি, তবে আজকের ‘জনমিতিক সুবিধা’ (পপুলেশন ডিভিডেন্ট) একসময় ‘জনমিতিক বোঝা’ (পপুলেশন বার্ডেন) পরিণত হবে।
শিক্ষা একটি বিনিয়োগ। কিন্তু সেই বিনিয়োগের ফল তখনই পাওয়া যায়, যখন তা উৎপাদনশীল দক্ষতায় রূপ নেয়। আজকের বিশ্বে ডিগ্রি নয়, দক্ষতাই নতুন মুদ্রা। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ যদি নিজেদের বৈশ্বিক চাকরি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নিতে চায়, তবে এখনই সময় সনদনির্ভর শিক্ষা থেকে দক্ষতানির্ভর বাস্তব শিক্ষায় রূপান্তর ঘটানোর। যে তরুণ নিজে শেখার মানসিকতা ধরে রাখে, অনলাইনে নতুন দক্ষতা অর্জন করে এবং বাস্তব প্রকল্পে অংশ নেয়, সেই তরুণই আগামী বাংলাদেশের শক্তি।
যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাত আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে— দক্ষতা থাকলে ডিগ্রি নয়, কাজই কথা বলে। তাই এখনই সময় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরি সংস্কৃতি ও সামাজিক মানসিকতাকে পুনর্গঠন করার। কারণ, এ শতাব্দীর অর্থনীতি আর ডিগ্রির ওপর দাঁড়িয়ে নেই, এটি দাঁড়িয়ে আছে শেখার সক্ষমতার ওপর।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার যদি এখন থেকেই ‘দক্ষতায় অগ্রাধিকার’ নীতি গ্রহণ করে, তবে আমাদের তরুণরাই হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি। আর যদি আমরা পুরোনো কাঠামোতে আটকে থাকি, তবে সোনার তরুণ প্রজন্ম শুধু সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে— দক্ষতা থাকবে না, সুযোগ থাকবে না।
অতএব, এখনই সময় শিক্ষা ও কর্মনীতিতে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর— চাকরি পেতে সার্টিফিকেট নয়, দরকার বাস্তব দক্ষতা।
লেখক: বিজ্ঞানী ও গবেষক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
E-mail: [email protected]
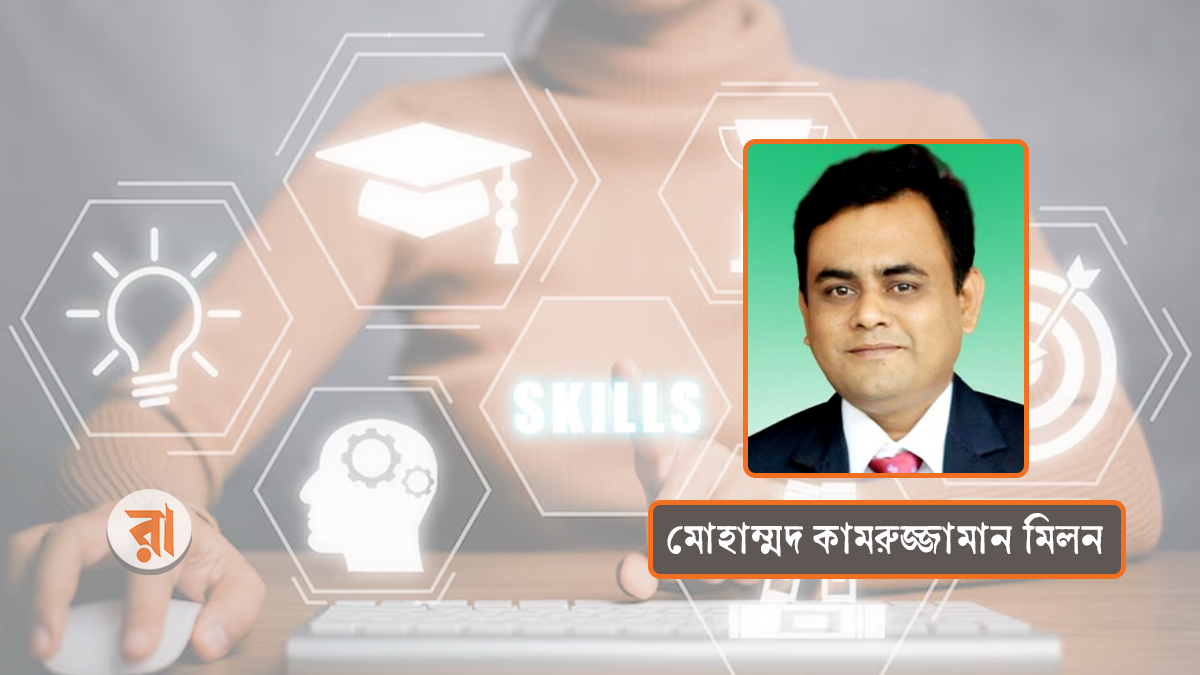
বাংলাদেশে এখন যে সংকটটি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে তা কেবল বেকারত্ব নয়, বরং শিক্ষিত বেকারত্ব। প্রতি বছর হাজার হাজার তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তাদের একটি বড় অংশ উপযুক্ত কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। অন্যদিকে শিল্প ও প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তারা একাধিকবার অভিযোগ করেছেন— ‘আমাদের দক্ষ কর্মীর অভাব।’
অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে দুটি সমস্যায় জর্জরিত— বেকারত্ব ও দক্ষতার ঘাটতি। এ বৈপরীত্যের মূল কারণ একটাই— আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো সনদকেন্দ্রিক, দক্ষতাকেন্দ্রিক নয়। কিন্তু বিশ্ব অর্থনীতি এরই মধ্যে বদলে গেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাত এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বাস্তব উদাহরণ।
গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রযুক্তি কোম্পানি— যেমন গুগল, আইবিএম, মাইক্রোসফট ও অ্যামাজন তাদের নিয়োগনীতিতে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। একসময় প্রতিষ্ঠানগুলো চার বছরের বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিকে প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করত, কিন্তু এখন তাদের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।
২০১৮ সালে গুগল ‘Grow with Google’ নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করে, যেখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি ছাড়াই অংশগ্রহণ করা যায়। মাত্র ছয় মাসের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা ডেটা অ্যানালিটিক্স, ইউএক্স ডিজাইন বা আইটি সাপোর্টে চাকরি পাচ্ছেন। গুগলের দাবি, এ প্রোগ্রামের অংশগ্রহণকারীদের ৮০ শতাংশ ছয় মাসের মধ্যেই কর্মসংস্থান পেয়েছে।
একইভাবে আইবিএম তাদের ‘New Collar Jobs’ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমন কর্মী নিয়োগ দিচ্ছে যাদের হাতে বাস্তব প্রযুক্তিগত দক্ষতা আছে, কিন্তু ডিগ্রি নেই। প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অরবিন্দ কৃষ্ণা সরাসরি বলেছেন, ‘আমরা আর শুধু চার বছরের ডিগ্রিধারী খুঁজছি না, আমরা খুঁজছি যাদের হাতে বাস্তব দক্ষতা আছে।’
এ পরিবর্তন কোনো আকস্মিক পদক্ষেপ নয়। ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার পর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো উপলব্ধি করে, অনেক ডিগ্রিধারী প্রার্থী আসলে বাজারে অপ্রাসঙ্গিক। তারা তত্ত্ব জানে, কিন্তু প্রযুক্তি জানে না। তাই ২০১০ সালের পর থেকে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ‘Skills over Degrees’ নীতি গ্রহণ করে।
এর ফল এখন স্পষ্ট— ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আইটি খাতের প্রায় ৪৫ শতাংশ চাকরির বিজ্ঞাপনে ডিগ্রি আবশ্যিক ছিল না। ২০২৪ সালে এই হার অর্ধেক ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্রে আজ একজন প্রোগ্রামার বা ডেটা অ্যানালিস্টের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নয়, বরং বাস্তব দক্ষতাই মূল যোগ্যতা।
বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে একজন তরুণ তার দক্ষতা যাচাই করাতে পারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে, যেমন— কোর্সিয়া, এডএক্স বা ইউডেমি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসের সার্টিফিকেটধারীরা যুক্তরাষ্ট্রে বছরে গড়ে ৯০ থেকে ১২০ হাজার ডলার বেতন পাচ্ছেন।
একইভাবে গুগল ক্যারিয়ার সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীরা চাকরি পেতে গড়ে ছয় মাসেরও কম সময় নিচ্ছেন। এ ছাড়া গিটহাব বা কেগল প্রোফাইলের মাধ্যমে কেউ নিজের কোডিং দক্ষতা প্রমাণ করতে পারলেই মিলছে চাকরি। অর্থাৎ এখন আর প্রশ্ন নেই যে ‘তুমি কোথায় পড়েছ’, বরং প্রশ্নটা হলো ‘তুমি কী করতে পারো।’
কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো এমন পাঠ্যক্রম অনুসরণ করছে যা ১০ বছর আগের শিল্প-প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক প্রতিষ্ঠানে ল্যাব সুবিধা সীমিত, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা ইন্টার্নশিপ নেই। ফলাফল— শিক্ষার্থীরা কেবল বইয়ের জ্ঞান নিয়ে বেরিয়ে আসছে, কিন্তু বাস্তবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না।
বাংলাদেশের সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের (বেসিস) তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার নতুন আইটি পদ তৈরি হয়, কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় সর্বোচ্চ ১০ হাজার। অর্থাৎ প্রায় ৬০ শতাংশ পদ ফাঁকা থেকে যায়।
সমস্যার গভীরে গেলে দেখা যায় তিনটি বড় কারণ কাজ করছে। প্রথমত, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রম পুরোনো, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি, প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক বা ডেটা সায়েন্সের ব্যবহার সীমিত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা প্রক্রিয়ায় হাতে-কলমে কাজ শেখার সংস্কৃতি নেই। পরীক্ষার ফলাফলে মুখস্তবিদ্যা এখনো বড় প্রভাব রাখে। তৃতীয়ত, আমাদের সমাজে এখনো ডিগ্রিকে মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, দক্ষতাকে নয়। ফলে একজন তরুণ যদি বলে যে সে ফ্রিল্যান্সার বা ডেভেলপার, তখন অনেকেই ভাবে তার ঠিক ‘চাকরি নেই’।
এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে শেখার মতো অনেক কিছুই আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পসংযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র (স্কিল ল্যাব) তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করবে।
দ্বিতীয়ত, ডিগ্রি অর্জনের আগে অন্তত ছয় মাসের ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা দরকার।
তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে যৌথ সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম চালু করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা একদিকে জাতীয় ডিগ্রি পাবে, অন্যদিকে গুগল, মাইক্রোসফট বা আইবিএমের স্বীকৃত দক্ষতা অর্জন করবে।
চতুর্থত, নিয়োগদাতাদের মনোভাবও বদলাতে হবে। চাকরির বিজ্ঞাপনে ‘ন্যূনতম স্নাতক’ যোগ্যতা চাওয়ার বদলে ‘সমমানের দক্ষতা...’র উল্লেখ করা উচিত। এটি কেবল শব্দ পরিবর্তন নয়, এটি একটি নীতিগত সংস্কৃতি পরিবর্তনের সূচনা।
বিশ্ব এখন ‘স্কিল ইকোনমি’র দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইইফ) ২০২৩ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে বিশ্বের অর্ধেক কর্মীকে নতুন করে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকবে ডেটা অ্যানালিটিকস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), সাইবার সিকিউরিটি ও ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে।
অর্থাৎ, যেসব দেশে তরুণ জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু তারা নতুন দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ, সেসব দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঝুঁকিটি এখানেই। যদি আমরা এখনই দক্ষতাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে না তুলি, তবে আজকের ‘জনমিতিক সুবিধা’ (পপুলেশন ডিভিডেন্ট) একসময় ‘জনমিতিক বোঝা’ (পপুলেশন বার্ডেন) পরিণত হবে।
শিক্ষা একটি বিনিয়োগ। কিন্তু সেই বিনিয়োগের ফল তখনই পাওয়া যায়, যখন তা উৎপাদনশীল দক্ষতায় রূপ নেয়। আজকের বিশ্বে ডিগ্রি নয়, দক্ষতাই নতুন মুদ্রা। বাংলাদেশের তরুণ সমাজ যদি নিজেদের বৈশ্বিক চাকরি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে নিতে চায়, তবে এখনই সময় সনদনির্ভর শিক্ষা থেকে দক্ষতানির্ভর বাস্তব শিক্ষায় রূপান্তর ঘটানোর। যে তরুণ নিজে শেখার মানসিকতা ধরে রাখে, অনলাইনে নতুন দক্ষতা অর্জন করে এবং বাস্তব প্রকল্পে অংশ নেয়, সেই তরুণই আগামী বাংলাদেশের শক্তি।
যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাত আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে— দক্ষতা থাকলে ডিগ্রি নয়, কাজই কথা বলে। তাই এখনই সময় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, চাকরি সংস্কৃতি ও সামাজিক মানসিকতাকে পুনর্গঠন করার। কারণ, এ শতাব্দীর অর্থনীতি আর ডিগ্রির ওপর দাঁড়িয়ে নেই, এটি দাঁড়িয়ে আছে শেখার সক্ষমতার ওপর।
বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার যদি এখন থেকেই ‘দক্ষতায় অগ্রাধিকার’ নীতি গ্রহণ করে, তবে আমাদের তরুণরাই হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি। আর যদি আমরা পুরোনো কাঠামোতে আটকে থাকি, তবে সোনার তরুণ প্রজন্ম শুধু সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে— দক্ষতা থাকবে না, সুযোগ থাকবে না।
অতএব, এখনই সময় শিক্ষা ও কর্মনীতিতে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর— চাকরি পেতে সার্টিফিকেট নয়, দরকার বাস্তব দক্ষতা।
লেখক: বিজ্ঞানী ও গবেষক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
E-mail: [email protected]
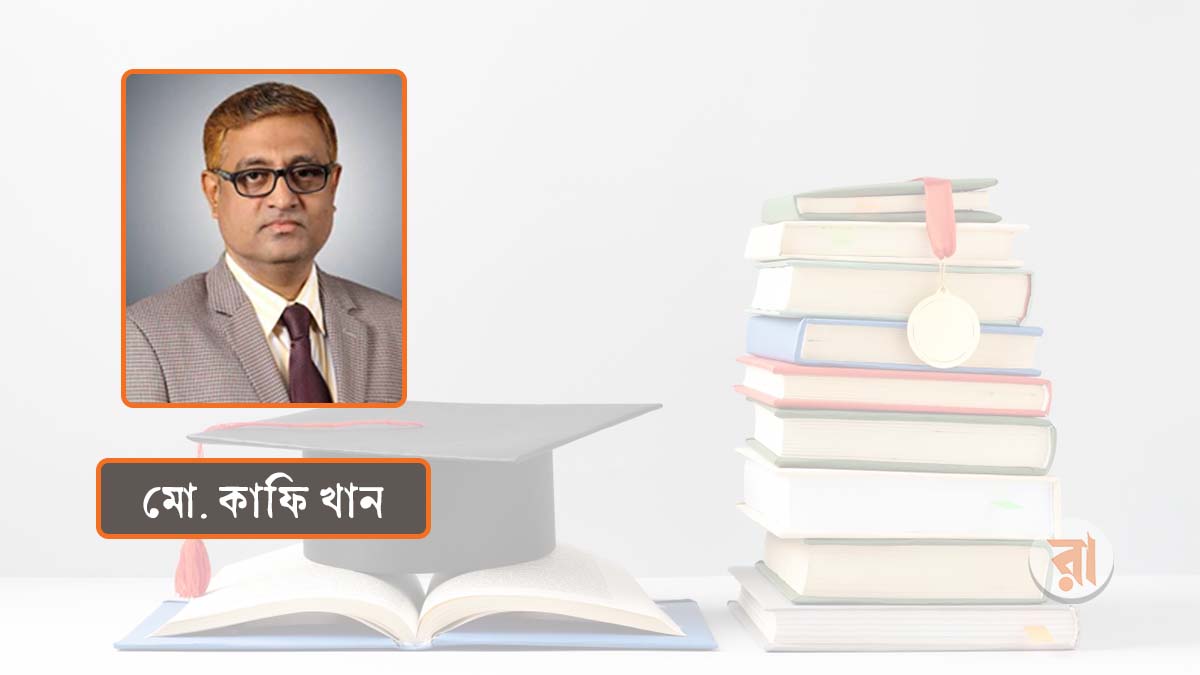
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই একাডেমিক মেরিটোক্রেসিকে (বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, মূল্যায়ন ও নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে শুধু যোগ্যতা ও কাজের মানের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত পরিচয়, রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবিরের ভিত্তিতে নয়) যথাযথভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
৪ দিন আগে
একজন উপদেষ্টার কাছ থেকে আমরা আশা করি নীতিগত সততা, সংস্কারের সাহস এবং মেধাবীদের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা। কিন্তু এখানে দেখা গেল উল্টো চিত্র— সংস্কারের প্রস্তাবকে শাস্তি দিয়ে দমন করা হলো। নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়; নীরবতা এখানে পক্ষ নেওয়া। আর সেই পক্ষটি দুর্নীতির সুবিধাভোগীদের।
৫ দিন আগে
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বা সংস্কার অনিবার্য। সেই সংস্কারের স্পিরিট বা চেতনা আমি এখন বিএনপির রাজনীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই দেশের এ বাস্তবতায় জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিএনপির সঙ্গেই পথ চলাকে আমি শ্রেয় মনে করেছি এবং যোগদানের সিদ্ধান
৫ দিন আগে
বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজার আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে এখনো পিছিয়ে। বছরে ৩০-৪০ লাখ দেশীয় পর্যটক এলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নগণ্য। তুলনায় থাইল্যান্ড বছরে প্রায় চার কোটি বিদেশি পর্যটক থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে। আর মালদ্বীপ মাত্র ২০ লাখ পর্যটক থেকেই তার জিডিপ
৭ দিন আগে