
জাকির আহমদ খান কামাল
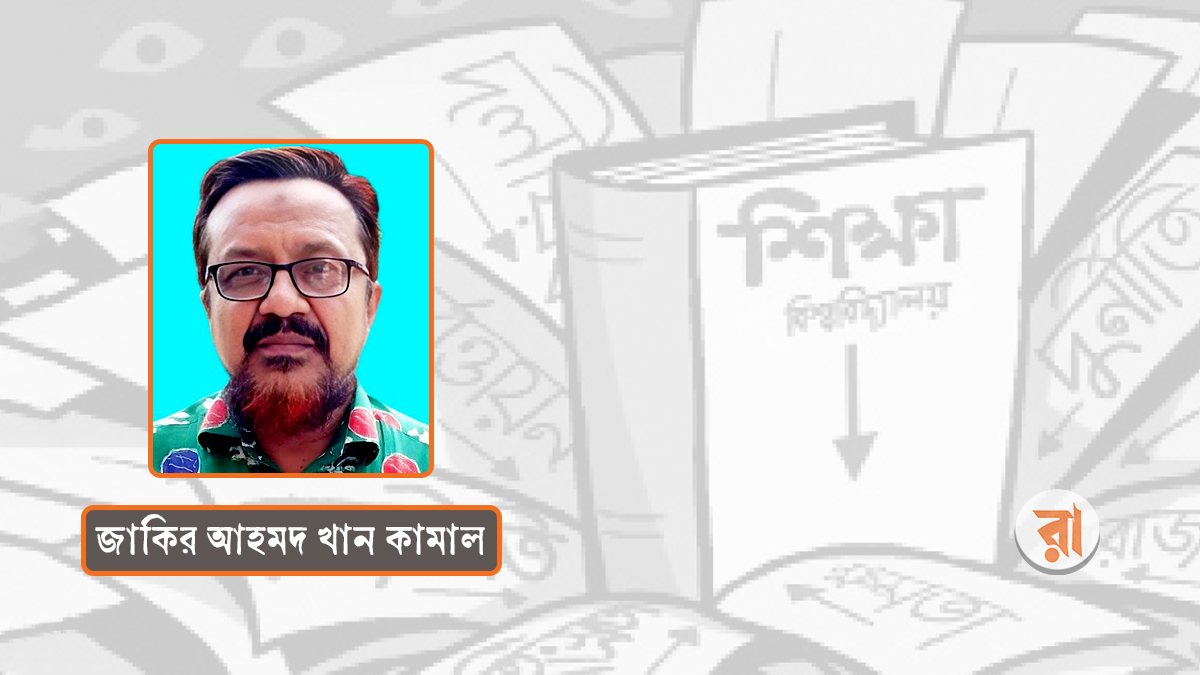
একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে বিদ্যমান শিক্ষাসংকট নিয়ে প্রচুর আলোচনা, কথাবার্তা ও লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু এর কোনো সঠিক গতিপথ আজ পর্যন্ত নির্ণীত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদরা নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষাধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেন, যা নিয়ে মাঠপর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও কর্মকর্তারা প্রায়শই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
এসব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। অধিকাংশ সময় তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে। তাই সমন্বয়হীনভাবে গৃহীত পরিবর্তন অধিকাংশ সময় শিক্ষাবান্ধব হয় না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার গুণগত মান শিক্ষার্থীর বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় না।
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই একটি ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠন করা হয়। এ কমিশন প্রণীত প্রস্তাবনা ও সুপারিশ ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হলেও বাস্তবে আলোর মুখ দেখেনি। ফলে আগেকার ধারায়ই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।
১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এ কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঠামো পুনর্গঠন এবং জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিকীকরণের জন্য একাধিক প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করে। কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালের ‘মজিদ খান শিক্ষানীতি’ নামে একটি নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়, যা পরে ব্যাপক বিতর্ক ও আন্দোলনের জন্ম দেয়।
১৯৮৭ সালে মফিজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিশন ও ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব-সুপারিশ পর্যালোচনা ও সংশোধনের মাধ্যমে ২০০২ সালে একটি কমিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নানা পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে কিছু সংশোধনের সুপারিশ করে। তবে এ কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ জন্য ২০০৩ সালে মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজন পড়ে।
২০০৯ সালে তৎকালীন সরকার জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন ও ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।
এ খসড়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়, যা পরে ‘জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০’ নামে পরিচিতি পায়। এ শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকেই দেশে বেসরকারি, বাণিজ্যনির্ভর ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা সমধিক অগ্রাধিকার পায়, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এ+, জিপিএ ফাইভ নামক ফলাফলের প্রতিযোগিতা। আগে যেখানে ভালো শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো, এখন তা অনেকাংশে ফলকেন্দ্রিক। ১৯৯১-এর পর থেকে মূলত ভালো ফলাফলের প্রতিযোগিতা শুরু।
১৯৯২ সাল থেকে প্রথমবারের মতো এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নব্যাংক প্রচলন শুরু হয়, যা বোদ্ধামহলে সমালোচনা জন্ম দেয়। কারণ এই প্রশ্নব্যাংক আদতে শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের চেয়ে মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করে। শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি নম্বর দিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কথাও জানা যায়, যা অতীতে কখনো ঘটেনি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে পাঠদানের মাধ্যমে নয়, নম্বর প্রদানের মাধ্যমে।
ফলে দেখা যায়, যতজন পরীক্ষার্থী তার অর্ধেকের বেশি ‘এ প্লাস’ বা ‘জিপিএ-৫’ পেয়ে থাকে। স্কুল অপেক্ষা মাদরাসা ও গ্রাম অপেক্ষা শহরের দিকে ফলাফল ভালো করে। এর মধ্যে একটি অংশ এইচএসসি পাস করার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের ফল খুবই হতাশাজনক। ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর পর্যন্ত পায় না। এতে ভর্তি কোটা পূরণ করতেও সংকটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এই যদি হয় শিক্ষার্থীদের অবস্থা তাহলে, দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টিতে শিক্ষকদের ভূমিকা কতটুকু সহায়ক হতে পারে?
বর্তমানে মব সংস্কৃতির ফলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শিক্ষকদের কান ধরানো, পানিতে ডোবানো, লাঞ্ছনা করাসহ নানা ঘটনায় মিডিয়া সরগরম থাকে, যা সত্যিই লজ্জাজনক ও অপমানজনক। এই অপমানজনক অবস্থা থেকে শিক্ষকদের যেন মুক্তি নেই। অবশ্য কিছু শিক্ষকও রয়েছেন যারা অপরাজনীতিসহ নানা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তারাও শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের সম্মান বিনষ্টের জন্য অনেকাংশে দায়ী।
শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকের সংখ্যা ইত্যাদি রীতিমতো চরম বৈষম্যের রূপ ধারণ করেছে। দেখা যায়, শিক্ষকরা মফস্বলে শিক্ষকতা করলেও অবস্থান করেন শহরে, প্রাইভেট কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বহুধাবিভক্ত জগাখিচুড়ি মার্কা শিক্ষার ধারায় এর থেকে বেশি কিছু আশা করাও কঠিন।
শহর ও গ্রামের অব্যাহত বৈষম্যের কারণে দেখা যায় শহরের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্তরে এসে তারা সেই ধারা আর ধরে রাখতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বরং গ্রামের শিক্ষার্থীরাই তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল করে।
প্রশ্নপত্র ফাঁস আরেকটি বড় সমস্যা। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিসিএস, মেডিকেলসহ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়া এখন রীতিমতো স্বাভাবিক খবর। হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকায় প্রশ্ন বিক্রির কথা শোনা যায়, যা আদৌ কাম্য নয়। আগে কেবল চাকরির জন্য আর্থিক লেনদেনের কথা শোনা গেলেও এখন প্রশ্নপত্র, চাকরি এবং বদলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে শিক্ষা নিয়ে। পরিকল্পনার অভাব নেই, অথচ বাজেট কমেছে। গুরুত্ব হারাচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা ও অনুকূল-নিরাপদ ক্যাম্পাস। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সংকটে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি যেখানে চরম আকার ধারণ করেছে, সেখানে অপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্ব হারাতে বসেছে।
কারণ, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শিক্ষার আরেকটি সংকট হলো শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তা। ছাত্র রাজনীতি ও যৌন সহিংসতা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে নিরাপদ বোধ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।
শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের এক প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও দলবেঁধে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছেন আরেক শিক্ষার্থী। তাকে অবশ্য ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিষয়ক কমিটিতেও পাঠানো হয়েছে।
কমিটির সম্মতি হলে হয়তো দূর ভবিষ্যতে অভিযোগটি আলোর মুখ দেখতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে যদি আরও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সে ক্ষেত্রে এ ঘটনা চাপা পড়ে যাবে। ‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কাঁদবে’।
বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ক্যাম্পাসে এত সংঘাত ও সহিংসতা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছন্দের বদলে খুব অসহায়বোধ করছে। সেশন জট আজও যেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্মরণ করিয়ে দেয় এরশাদ আমলের সেশন জটের কথা, যেটি দূর করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দৃশ্যমান উদ্যোগ নিলেও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা দুর্বল হওয়ায় ফল আসেনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় বর্তমানে অভিভাবকদের, বিশেষ করে যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী প্রবণতাও লক্ষণীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পড়াশোনা শেষ করেই পাড়ি জমায় বিদেশে।
বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মূলধারা-মাদরাসা শিক্ষার মাঝে অব্যাহত ব্যবধান বা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে হলে এ সব সংকট নিরসনে নিত্য পরিবর্তনশীল শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।
পাশাপাশি মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় যৌন সহিংসতার ভয়ের সংস্কৃতির মানসিকতা পরিহার করতে হবে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও কলাম লেখক
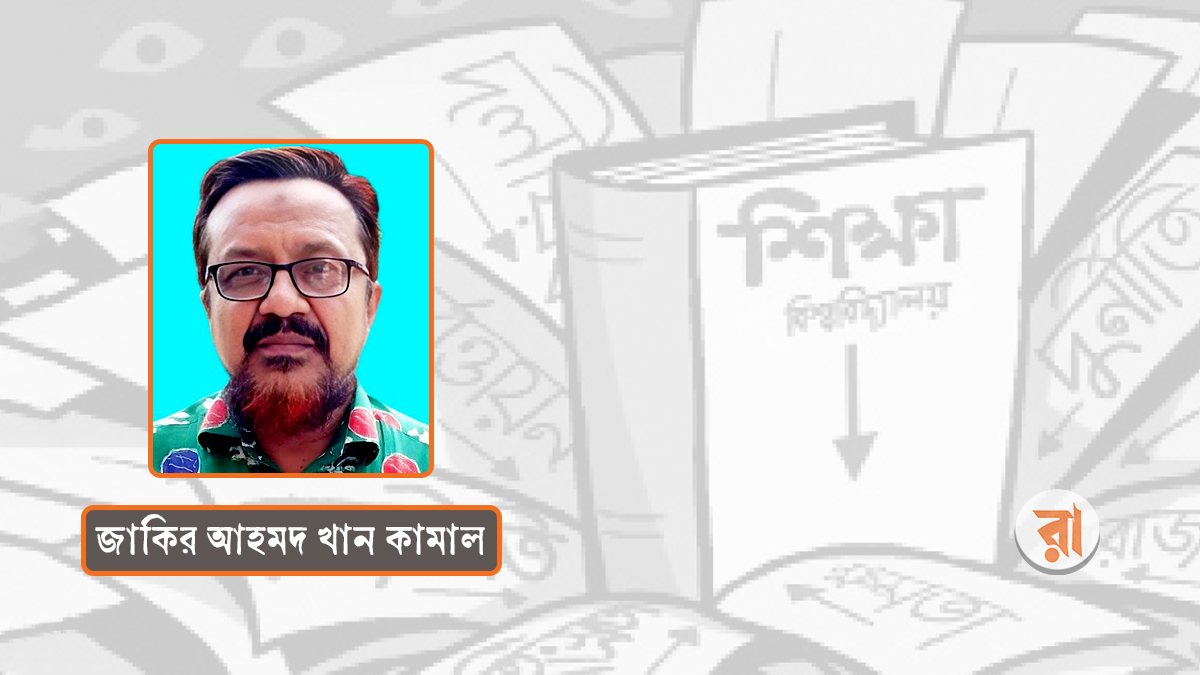
একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশে বিদ্যমান শিক্ষাসংকট নিয়ে প্রচুর আলোচনা, কথাবার্তা ও লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু এর কোনো সঠিক গতিপথ আজ পর্যন্ত নির্ণীত হচ্ছে না। মাঝে মাঝে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনাবিদরা নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে শিক্ষাধারায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেন, যা নিয়ে মাঠপর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও কর্মকর্তারা প্রায়শই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
এসব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে, বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত হয় না। অধিকাংশ সময় তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করে। তাই সমন্বয়হীনভাবে গৃহীত পরিবর্তন অধিকাংশ সময় শিক্ষাবান্ধব হয় না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার গুণগত মান শিক্ষার্থীর বিকাশের পক্ষে সহায়ক হয় না।
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বিজ্ঞানমনস্ক ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পরপর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই একটি ‘জাতীয় শিক্ষা কমিশন’ গঠন করা হয়। এ কমিশন প্রণীত প্রস্তাবনা ও সুপারিশ ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত হলেও বাস্তবে আলোর মুখ দেখেনি। ফলে আগেকার ধারায়ই শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।
১৯৮৩ সালে সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আবদুল মজিদ খানের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এ কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার লক্ষ্য ও কাঠামো পুনর্গঠন এবং জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আধুনিকীকরণের জন্য একাধিক প্রস্তাব ও সুপারিশ পেশ করে। কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৮৩ সালের ‘মজিদ খান শিক্ষানীতি’ নামে একটি নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়, যা পরে ব্যাপক বিতর্ক ও আন্দোলনের জন্ম দেয়।
১৯৮৭ সালে মফিজউদ্দীন আহমদ শিক্ষা কমিশন ও ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাব-সুপারিশ পর্যালোচনা ও সংশোধনের মাধ্যমে ২০০২ সালে একটি কমিটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর নানা পরীক্ষা, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে কিছু সংশোধনের সুপারিশ করে। তবে এ কমিশনের অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়নি। এ জন্য ২০০৩ সালে মনিরুজ্জামান মিয়া শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রয়োজন পড়ে।
২০০৯ সালে তৎকালীন সরকার জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে। কমিটি ১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রতিবেদন ও ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।
এ খসড়াটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়, যা পরে ‘জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০’ নামে পরিচিতি পায়। এ শিক্ষানীতিতে উচ্চ শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের উপযোগী বিজ্ঞানমনস্ক, অসাম্প্রদায়িক, উদারনৈতিক, মানবমুখী, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকেই দেশে বেসরকারি, বাণিজ্যনির্ভর ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা সমধিক অগ্রাধিকার পায়, যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এ+, জিপিএ ফাইভ নামক ফলাফলের প্রতিযোগিতা। আগে যেখানে ভালো শিক্ষার ওপর প্রাধান্য দেওয়া হতো, এখন তা অনেকাংশে ফলকেন্দ্রিক। ১৯৯১-এর পর থেকে মূলত ভালো ফলাফলের প্রতিযোগিতা শুরু।
১৯৯২ সাল থেকে প্রথমবারের মতো এসএসসি পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের ১০০ নম্বরের স্থলে ৫০ নম্বরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নব্যাংক প্রচলন শুরু হয়, যা বোদ্ধামহলে সমালোচনা জন্ম দেয়। কারণ এই প্রশ্নব্যাংক আদতে শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের চেয়ে মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করে। শিক্ষার্থীদের বেশি বেশি নম্বর দিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার কথাও জানা যায়, যা অতীতে কখনো ঘটেনি। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য শিক্ষকদেরও বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে পাঠদানের মাধ্যমে নয়, নম্বর প্রদানের মাধ্যমে।
ফলে দেখা যায়, যতজন পরীক্ষার্থী তার অর্ধেকের বেশি ‘এ প্লাস’ বা ‘জিপিএ-৫’ পেয়ে থাকে। স্কুল অপেক্ষা মাদরাসা ও গ্রাম অপেক্ষা শহরের দিকে ফলাফল ভালো করে। এর মধ্যে একটি অংশ এইচএসসি পাস করার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের ফল খুবই হতাশাজনক। ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম নম্বর পর্যন্ত পায় না। এতে ভর্তি কোটা পূরণ করতেও সংকটে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এই যদি হয় শিক্ষার্থীদের অবস্থা তাহলে, দূরদর্শী নাগরিক সৃষ্টিতে শিক্ষকদের ভূমিকা কতটুকু সহায়ক হতে পারে?
বর্তমানে মব সংস্কৃতির ফলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শিক্ষকদের কান ধরানো, পানিতে ডোবানো, লাঞ্ছনা করাসহ নানা ঘটনায় মিডিয়া সরগরম থাকে, যা সত্যিই লজ্জাজনক ও অপমানজনক। এই অপমানজনক অবস্থা থেকে শিক্ষকদের যেন মুক্তি নেই। অবশ্য কিছু শিক্ষকও রয়েছেন যারা অপরাজনীতিসহ নানা অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। তারাও শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের সম্মান বিনষ্টের জন্য অনেকাংশে দায়ী।
শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষকের সংখ্যা ইত্যাদি রীতিমতো চরম বৈষম্যের রূপ ধারণ করেছে। দেখা যায়, শিক্ষকরা মফস্বলে শিক্ষকতা করলেও অবস্থান করেন শহরে, প্রাইভেট কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বহুধাবিভক্ত জগাখিচুড়ি মার্কা শিক্ষার ধারায় এর থেকে বেশি কিছু আশা করাও কঠিন।
শহর ও গ্রামের অব্যাহত বৈষম্যের কারণে দেখা যায় শহরের শিক্ষার্থীরা এসএসসি ও এইচএসসিতে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করে। কিন্তু উচ্চশিক্ষার স্তরে এসে তারা সেই ধারা আর ধরে রাখতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বরং গ্রামের শিক্ষার্থীরাই তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল করে।
প্রশ্নপত্র ফাঁস আরেকটি বড় সমস্যা। প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিসিএস, মেডিকেলসহ প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়া এখন রীতিমতো স্বাভাবিক খবর। হাজার থেকে শুরু করে কয়েক লাখ টাকায় প্রশ্ন বিক্রির কথা শোনা যায়, যা আদৌ কাম্য নয়। আগে কেবল চাকরির জন্য আর্থিক লেনদেনের কথা শোনা গেলেও এখন প্রশ্নপত্র, চাকরি এবং বদলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
নিত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে শিক্ষা নিয়ে। পরিকল্পনার অভাব নেই, অথচ বাজেট কমেছে। গুরুত্ব হারাচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষাব্যবস্থা ও অনুকূল-নিরাপদ ক্যাম্পাস। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক সংকটে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি যেখানে চরম আকার ধারণ করেছে, সেখানে অপরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুরুত্ব হারাতে বসেছে।
কারণ, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শিক্ষার আরেকটি সংকট হলো শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তা। ছাত্র রাজনীতি ও যৌন সহিংসতা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ শিক্ষার্থী, বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে নিরাপদ বোধ করা কঠিন হয়ে উঠেছে।
শুধু তাই নয়, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের এক প্রার্থীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় আক্রমণ ও দলবেঁধে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছেন আরেক শিক্ষার্থী। তাকে অবশ্য ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে অভিযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়নবিষয়ক কমিটিতেও পাঠানো হয়েছে।
কমিটির সম্মতি হলে হয়তো দূর ভবিষ্যতে অভিযোগটি আলোর মুখ দেখতে পারে। কিন্তু এরই মধ্যে যদি আরও কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, সে ক্ষেত্রে এ ঘটনা চাপা পড়ে যাবে। ‘বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতেই কাঁদবে’।
বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে ক্যাম্পাসে এত সংঘাত ও সহিংসতা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বচ্ছন্দের বদলে খুব অসহায়বোধ করছে। সেশন জট আজও যেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্মরণ করিয়ে দেয় এরশাদ আমলের সেশন জটের কথা, যেটি দূর করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দৃশ্যমান উদ্যোগ নিলেও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা দুর্বল হওয়ায় ফল আসেনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় বর্তমানে অভিভাবকদের, বিশেষ করে যাদের আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়মুখী প্রবণতাও লক্ষণীয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পড়াশোনা শেষ করেই পাড়ি জমায় বিদেশে।
বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রাম-শহর, নারী-পুরুষ, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মূলধারা-মাদরাসা শিক্ষার মাঝে অব্যাহত ব্যবধান বা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে যেতে হলে এ সব সংকট নিরসনে নিত্য পরিবর্তনশীল শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য।
পাশাপাশি মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় যৌন সহিংসতার ভয়ের সংস্কৃতির মানসিকতা পরিহার করতে হবে।
লেখক: অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও কলাম লেখক

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে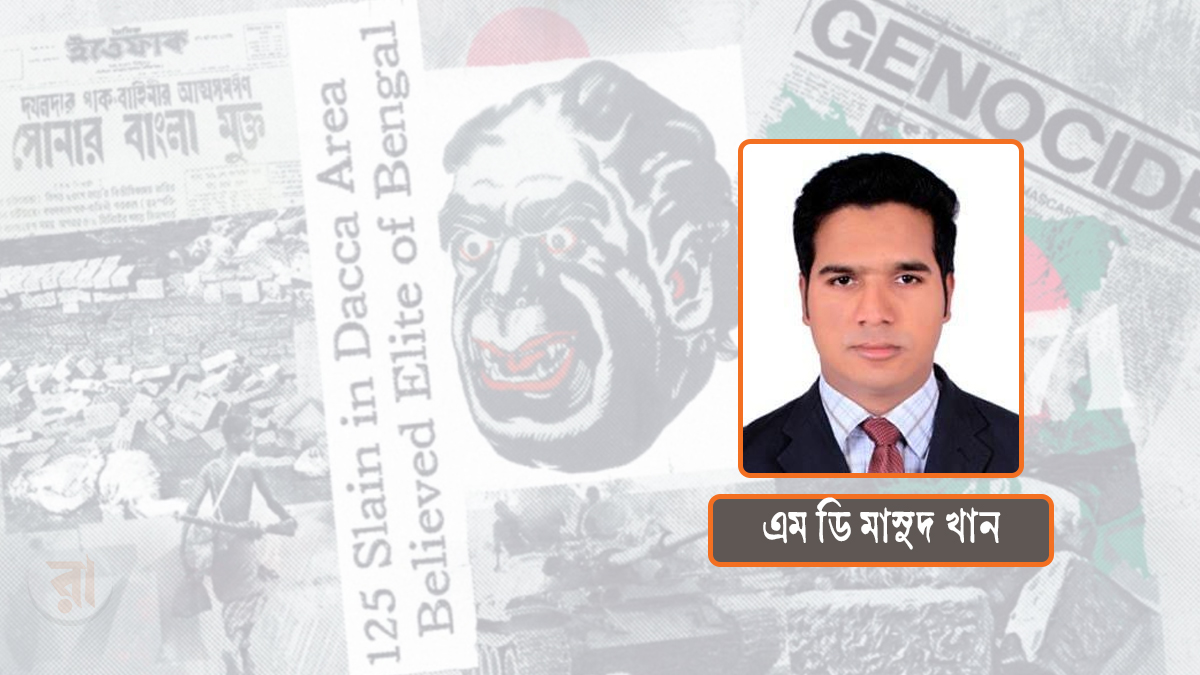
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে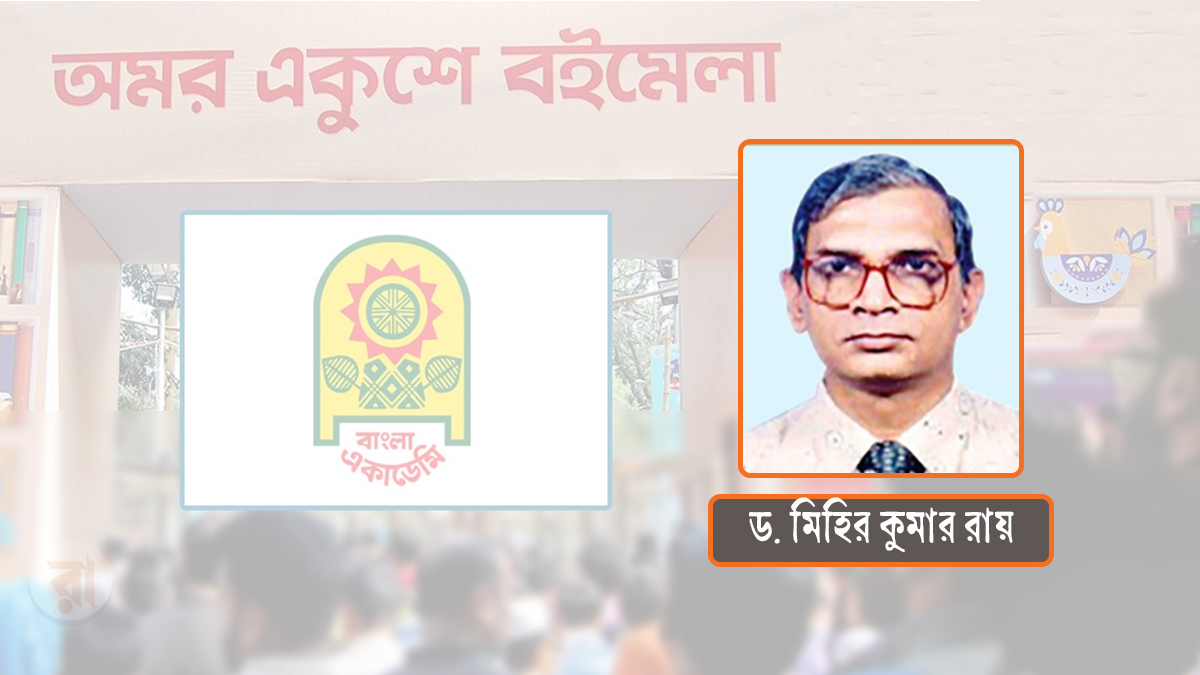
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে