
ড. মিহির কুমার রায়

দেবী দুর্গা সনাতন ধর্মে শক্তির প্রতীক। মঙ্গল ও ন্যায়ের অবতার হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন হাজার বছর ধরে। প্রাচীন আর্য ঋষিরা তাকে মহাশক্তি, অখণ্ড আশীর্বাদ ও অভয়ার প্রতীক হিসেবে আরাধনা করেছেন। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত—তিন ধারাতেই দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য সমানভাবে স্বীকৃত।
মহাভারতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নামার আগে অর্জুন দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। দেবীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে সফল হন। এভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে দেবী দুর্গা শক্তি, বীরত্ব ও মাতৃত্বের সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং আজও সেই চেতনা বাংলার সমাজে গভীরভাবে বিদ্যমান।
বাংলায় দুর্গাপূজার সূচনা বহু প্রাচীন কালে। প্রথম দিকে এ পূজা ছিল রাজকেন্দ্রিক ও অভিজাত শ্রেণির আয়োজিত অনুষ্ঠান। রাজা, জমিদার বা ধনী পরিবারগুলো যুদ্ধে জয়লাভ, বিপদ থেকে মুক্তি কিংবা প্রজাদের কল্যাণ কামনায় দেবীর পূজা করতেন।
ষোড়শ শতকে কৃত্তিবাস রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কাব্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার কাহিনি মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। অসুরবধিনী এই দেবীর আরাধনা তখন কেবল রাজপরিবার বা ধনীদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে পূজা হয়ে ওঠে পরিবারকেন্দ্রিক, আর পরে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।
চণ্ডীপাঠে বর্ণিত হয়েছে দেবী দুর্গার আবির্ভাবের মহিমা। যখন অসুররা দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তখন বিপর্যস্ত দেবতারা একত্র হয়ে নিজেদের শক্তি সঞ্চারিত করেন এক নারীমূর্তিতে। সেই নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। দেবী তখন ১০ হাতে ১০টি অস্ত্র ধারণ করেন— শক্তির প্রতীক সেই অস্ত্রগুলো তাকে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম করে তোলে।
শেষ পর্যন্ত মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দেবতাদের রক্ষা করেন এবং ন্যায় ও সত্যের বিজয় নিশ্চিত করেন। তাই দুর্গা কেবল এক দেবী নন, তিনি ন্যায়বিচার, কল্যাণ, মাতৃত্ব ও শৌর্যের প্রতীক। তার কাহিনী মানুষের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়।
দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য শুধু পৌরাণিক কাহিনি বা চণ্ডীপাঠেই সীমাবদ্ধ নয়। আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। শঙ্করাচার্য তাকে মহামায়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন— যিনি জগৎ সৃষ্টি, পালন ও লয়ের নিয়ন্ত্রক। পরে উনবিংশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গাকে দেখেছেন মানবকল্যাণের শক্তিরূপে। তার মতে, দুর্গা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর দেবী নন, বরং সার্বজনীন মা, যিনি মানবজাতিকে শক্তি ও সাহস দেন। বাংলার বাউল, বৈষ্ণব, শাক্তসহ নানা ধারার আধ্যাত্মিক সাধকরা দুর্গাকে মায়ের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা করেছেন।
বাংলায় দুর্গাপূজা শরৎকালে পালিত হয় বলে একে শারদীয় দুর্গোৎসব বলা হয়। তবে বসন্তকালেও বাসন্তী পূজার প্রচলন আছে। প্রাচীনকালে রাজা ও জমিদারেরা এ পূজার আয়োজন করলেও সময়ের পরিক্রমায় এটি পরিণত হয়েছে সর্বজনীন উৎসবে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পূজামণ্ডপ গড়ে ওঠে। প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা— সবকিছুতেই যুক্ত হয় স্থানীয় মানুষ।
মহালয়ার অমাবস্যা দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র সম্প্রচারিত হয়, যা বাংলার মানুষের কাছে গভীর আবেগের বিষয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী হলো দুর্গাপূজার মূল দিনগুলো। এর মধ্যে অষ্টমীর সন্ধিপূজা ও সায়ংকালীন আরতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পাশাপাশি কুমারী পূজা বাংলার দুর্গোৎসবকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেখানে এক অল্পবয়সী কন্যাশিশুর মধ্যে দেবীসত্তা উপলব্ধি করা হয়।
ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক আয়োজন। রাজধানীতে রমনা কালীমন্দির, শাঁখারীবাজার, টিকাটুলি, ধানমন্ডি লেকপাড়সহ বহু স্থানে প্রতিমা স্থাপন করা হয়। প্রতিমাশিল্পীরা কাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে রঙ, সাজসজ্জা পর্যন্ত নিখুঁত শিল্পকর্ম উপহার দেন। মণ্ডপগুলো সাজানো হয় নানা প্রতীকী থিমে। আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সঙ্গীতানুষ্ঠান পূজাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিমা ও সাজসজ্জা দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমায়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দর্শনার্থীরা একত্র হন।
দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূজা উপলক্ষে গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে, আত্মীয়-স্বজনের মিলন ঘটে। নাটক, যাত্রা, গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি— সব মিলিয়ে পূজা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উৎসব মানুষকে আনন্দ দেয়, একে অপরের কাছাকাছি আনে, সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ায়।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও দুর্গাপূজার প্রভাব বিশাল। প্রতিমাশিল্পী, ঢাকশিল্পী, আলোকসজ্জাকারী, ফুল ব্যবসায়ী, পোশাক ব্যবসায়ী, গয়না ও প্রসাধনী বিক্রেতা—সবাই এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মৌসুমি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, নগর ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, দোকানপাটে বাড়তি বিক্রি হয়।
আধুনিক যুগে দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এটি শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, বরং মিলন, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। পূজার মণ্ডপে শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান— সব ধর্মের মানুষ ভিড় করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পূজাকে ঘিরে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বার্তা দেওয়া হয়।
দুর্গাপূজা তাই কেবল দেবীর আরাধনা নয়, এটি বাংলার মানুষের আশা, আনন্দ, ভরসা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উৎস। মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনী মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়। প্রতি বছর দেবীর আগমন তাই মানুষকে মনে করিয়ে দেয় ন্যায়-অন্যায়ের চিরন্তন লড়াইয়ের কথা। এভাবেই দুর্গাপূজা ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে জাতীয় ও সামাজিক উৎসব হিসেবে বাঙালির জীবনে অমলিন হয়ে আছে।
লেখক: গবেষক, অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও অধ্যাপক, সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

দেবী দুর্গা সনাতন ধর্মে শক্তির প্রতীক। মঙ্গল ও ন্যায়ের অবতার হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন হাজার বছর ধরে। প্রাচীন আর্য ঋষিরা তাকে মহাশক্তি, অখণ্ড আশীর্বাদ ও অভয়ার প্রতীক হিসেবে আরাধনা করেছেন। শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত—তিন ধারাতেই দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য সমানভাবে স্বীকৃত।
মহাভারতে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নামার আগে অর্জুন দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন। দেবীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে সফল হন। এভাবেই প্রাচীন ভারতবর্ষে দেবী দুর্গা শক্তি, বীরত্ব ও মাতৃত্বের সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন এবং আজও সেই চেতনা বাংলার সমাজে গভীরভাবে বিদ্যমান।
বাংলায় দুর্গাপূজার সূচনা বহু প্রাচীন কালে। প্রথম দিকে এ পূজা ছিল রাজকেন্দ্রিক ও অভিজাত শ্রেণির আয়োজিত অনুষ্ঠান। রাজা, জমিদার বা ধনী পরিবারগুলো যুদ্ধে জয়লাভ, বিপদ থেকে মুক্তি কিংবা প্রজাদের কল্যাণ কামনায় দেবীর পূজা করতেন।
ষোড়শ শতকে কৃত্তিবাস রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্যে দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য কাব্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের মধ্য দিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার কাহিনি মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে। অসুরবধিনী এই দেবীর আরাধনা তখন কেবল রাজপরিবার বা ধনীদের গণ্ডি পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়। ধীরে ধীরে পূজা হয়ে ওঠে পরিবারকেন্দ্রিক, আর পরে সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।
চণ্ডীপাঠে বর্ণিত হয়েছে দেবী দুর্গার আবির্ভাবের মহিমা। যখন অসুররা দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছিল, তখন বিপর্যস্ত দেবতারা একত্র হয়ে নিজেদের শক্তি সঞ্চারিত করেন এক নারীমূর্তিতে। সেই নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটে। দেবী তখন ১০ হাতে ১০টি অস্ত্র ধারণ করেন— শক্তির প্রতীক সেই অস্ত্রগুলো তাকে মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম করে তোলে।
শেষ পর্যন্ত মহিষাসুরকে বধ করে দেবী দেবতাদের রক্ষা করেন এবং ন্যায় ও সত্যের বিজয় নিশ্চিত করেন। তাই দুর্গা কেবল এক দেবী নন, তিনি ন্যায়বিচার, কল্যাণ, মাতৃত্ব ও শৌর্যের প্রতীক। তার কাহিনী মানুষের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়।
দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য শুধু পৌরাণিক কাহিনি বা চণ্ডীপাঠেই সীমাবদ্ধ নয়। আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত দর্শনের বিকাশ ঘটেছে। শঙ্করাচার্য তাকে মহামায়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন— যিনি জগৎ সৃষ্টি, পালন ও লয়ের নিয়ন্ত্রক। পরে উনবিংশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দ দুর্গাকে দেখেছেন মানবকল্যাণের শক্তিরূপে। তার মতে, দুর্গা কেবল কোনো নির্দিষ্ট ধর্মগোষ্ঠীর দেবী নন, বরং সার্বজনীন মা, যিনি মানবজাতিকে শক্তি ও সাহস দেন। বাংলার বাউল, বৈষ্ণব, শাক্তসহ নানা ধারার আধ্যাত্মিক সাধকরা দুর্গাকে মায়ের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা করেছেন।
বাংলায় দুর্গাপূজা শরৎকালে পালিত হয় বলে একে শারদীয় দুর্গোৎসব বলা হয়। তবে বসন্তকালেও বাসন্তী পূজার প্রচলন আছে। প্রাচীনকালে রাজা ও জমিদারেরা এ পূজার আয়োজন করলেও সময়ের পরিক্রমায় এটি পরিণত হয়েছে সর্বজনীন উৎসবে। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে পূজামণ্ডপ গড়ে ওঠে। প্রতিমা নির্মাণ থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা— সবকিছুতেই যুক্ত হয় স্থানীয় মানুষ।
মহালয়ার অমাবস্যা দিয়ে দেবীপক্ষের সূচনা হয়। ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র সম্প্রচারিত হয়, যা বাংলার মানুষের কাছে গভীর আবেগের বিষয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও বিজয়া দশমী হলো দুর্গাপূজার মূল দিনগুলো। এর মধ্যে অষ্টমীর সন্ধিপূজা ও সায়ংকালীন আরতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পাশাপাশি কুমারী পূজা বাংলার দুর্গোৎসবকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, যেখানে এক অল্পবয়সী কন্যাশিশুর মধ্যে দেবীসত্তা উপলব্ধি করা হয়।
ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছে জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক আয়োজন। রাজধানীতে রমনা কালীমন্দির, শাঁখারীবাজার, টিকাটুলি, ধানমন্ডি লেকপাড়সহ বহু স্থানে প্রতিমা স্থাপন করা হয়। প্রতিমাশিল্পীরা কাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে রঙ, সাজসজ্জা পর্যন্ত নিখুঁত শিল্পকর্ম উপহার দেন। মণ্ডপগুলো সাজানো হয় নানা প্রতীকী থিমে। আলোকসজ্জা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সঙ্গীতানুষ্ঠান পূজাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রতিমা ও সাজসজ্জা দেখার জন্য মানুষ ভিড় জমায়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দর্শনার্থীরা একত্র হন।
দুর্গাপূজা কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পূজা উপলক্ষে গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে, আত্মীয়-স্বজনের মিলন ঘটে। নাটক, যাত্রা, গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি— সব মিলিয়ে পূজা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক উৎসব। এ উৎসব মানুষকে আনন্দ দেয়, একে অপরের কাছাকাছি আনে, সামাজিক সম্প্রীতি বাড়ায়।
অর্থনৈতিক দিক থেকেও দুর্গাপূজার প্রভাব বিশাল। প্রতিমাশিল্পী, ঢাকশিল্পী, আলোকসজ্জাকারী, ফুল ব্যবসায়ী, পোশাক ব্যবসায়ী, গয়না ও প্রসাধনী বিক্রেতা—সবাই এ উৎসবকে কেন্দ্র করে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। মৌসুমি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, নগর ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি আসে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, দোকানপাটে বাড়তি বিক্রি হয়।
আধুনিক যুগে দুর্গাপূজা বাংলাদেশসহ সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এটি শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, বরং মিলন, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সামাজিক সংহতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। পূজার মণ্ডপে শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান— সব ধর্মের মানুষ ভিড় করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও পূজাকে ঘিরে সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বার্তা দেওয়া হয়।
দুর্গাপূজা তাই কেবল দেবীর আরাধনা নয়, এটি বাংলার মানুষের আশা, আনন্দ, ভরসা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের উৎস। মহিষাসুরমর্দিনীর কাহিনী মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষা দেয়। প্রতি বছর দেবীর আগমন তাই মানুষকে মনে করিয়ে দেয় ন্যায়-অন্যায়ের চিরন্তন লড়াইয়ের কথা। এভাবেই দুর্গাপূজা ধর্মীয় সীমা অতিক্রম করে জাতীয় ও সামাজিক উৎসব হিসেবে বাঙালির জীবনে অমলিন হয়ে আছে।
লেখক: গবেষক, অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও অধ্যাপক, সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে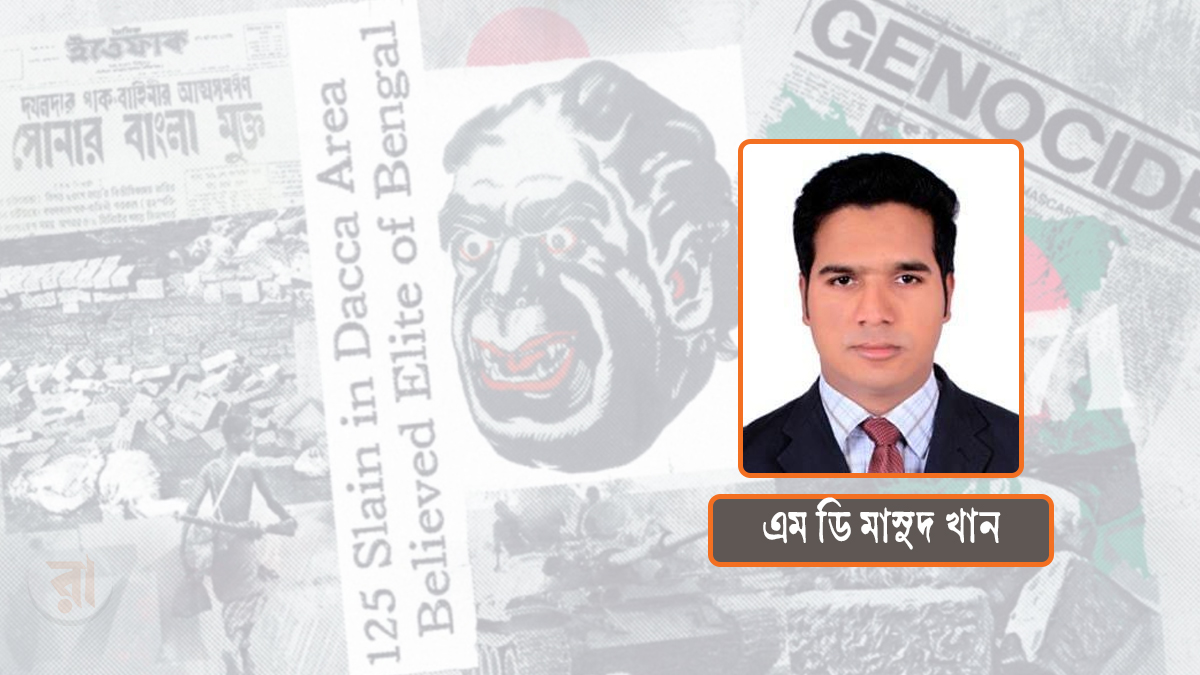
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে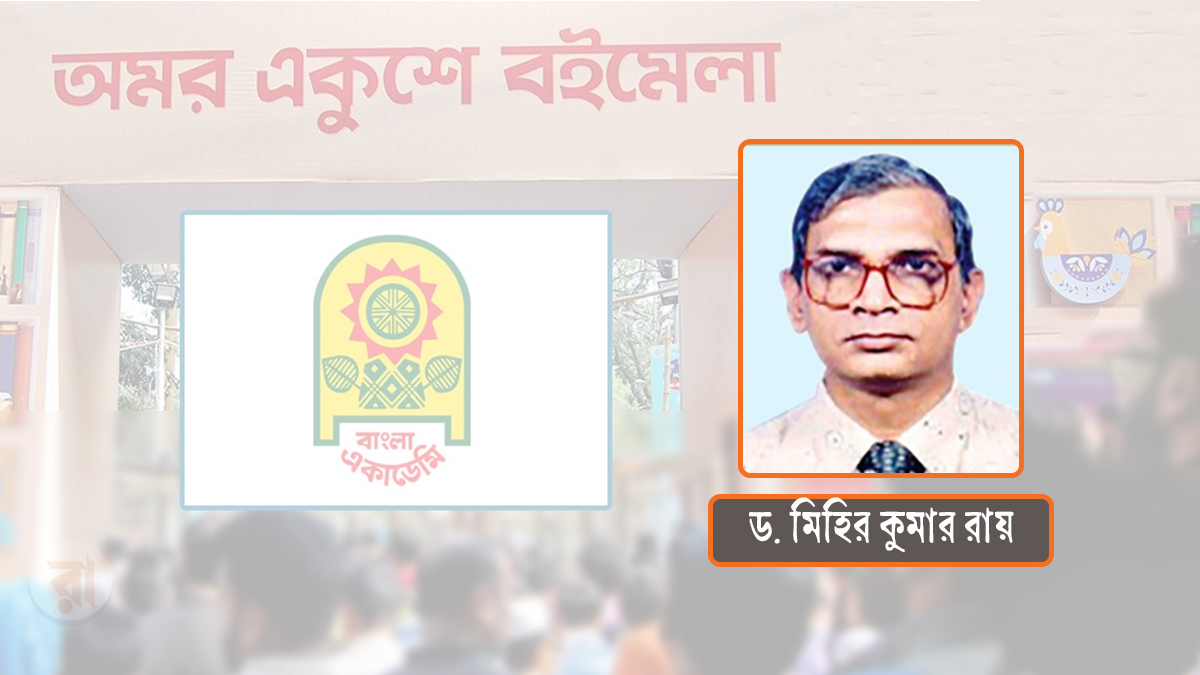
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে