
মো. ফেরদাউস মোবারক

৫ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা দেন—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, রমজানের আগেই। এই ঘোষণা ছিল এক ধরনের মাইলফলক, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানো এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে যে অস্থিরতা চলছিল, তা কিছুটা হলেও স্থিতিশীল করা। ওই গণ-অভ্যুত্থানেই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার পতনের মুখে পড়ে।
ঘোষণার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এটিকে স্বাগত জানায়। তারা মনে করে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা দেশের নির্বাচনী অনিশ্চয়তা দূর করবে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ও জামায়াতে ইসলামীর নীরবতা নতুন প্রশ্ন তুলেছে—এই নির্বাচন আসলেই কি সবার জন্য নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য?
ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার যে দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিল—প্রথমত, অভ্যুত্থানের সময় ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিচার করা, দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন করা এবং তৃতীয়ত, গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা। কিন্তু সরকার গঠনের পর থেকেই সময়সূচি নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব শুরু হয়।
বিএনপি, যাদের এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, তারা চাইছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হোক, যাতে তারা নিজেদের অবস্থান ফের শক্ত করতে পারে। তবে এনসিপি ও জামায়াত মনে করে, আগে সংবিধান সংস্কার ও নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দরকার—তারপরেই জাতীয় নির্বাচন দেওয়া যেতে পারে।
প্রথমদিকে ইউনূস বলেছিলেন, নির্বাচন ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ এর মধ্যে যে কোনো সময়ে হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারিকে বেছে নেওয়া হয়েছে—যা বিএনপির চাপ এবং লন্ডন বৈঠকের ফল বলেই মনে করছেন অনেকে।
রাজনৈতিক চিত্রকে আরও জটিল করে তোলে ‘জুলাই প্রোক্লেমেশন’ নামে ২৬ দফার সংস্কার-প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবটি মূলত অভ্যুত্থানের চেতনাকে সংবিধানে স্থায়ীভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি। এতে অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী অনেক ছাত্রনেতার প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে—এদের অনেকেই এখন এনসিপির নেতৃত্বে আছেন। তবে প্রস্তাবটি ঘিরে মতভেদ দেখা দেয়।
বিএনপি এই প্রস্তাবের প্রতীকী দিকটি মেনে নিলেও সংবিধানে তা যুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। তারা মনে করে, সময়মতো নির্বাচনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এনসিপি ও জামায়াত উভয়েই এই প্রস্তাবকে তড়িঘড়ি করে তৈরি ও সুনির্দিষ্টতা-বিহীন বলে নাকচ করে দেয়।
এসব মতবিরোধের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির গভীর বিভাজন প্রকাশ পেয়েছে। এনসিপি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। তারা বলছে, সবার আগে প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, এবং স্বচ্ছ নির্বাচনী কাঠামো। এসব ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না।
জামায়াতের অবস্থানও একইরকম অস্পষ্ট। শুরুতে তারা ফেব্রুয়ারির সময়সূচিকে সমর্থন করলেও পরে বলেছে, নির্বাচন অংশগ্রহণের আগে প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার, যার মধ্যে ‘প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন’ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত।
এদিকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো খুবই নাজুক। অভ্যুত্থানের পর রাজপথে বিক্ষোভ, ছত্রভঙ্গ জনতা, হঠাৎ হঠাৎ সহিংসতা ইত্যাদি চলছে, যা সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়।
যদি শেষ পর্যন্ত এনসিপি ও জামায়াত নিজেদের দাবি পূরণ না হওয়ার কারণে নির্বাচন বর্জন করে, তাহলে তা বড় ধরনের বৈধতা-সংকটে ফেলতে পারে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকে। এনসিপি, যাদের মূলভিত্তি ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়া অভ্যুত্থানে, এখন গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাদের অনুপস্থিতি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে বড়ভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। একইসঙ্গে জামায়াত না থাকলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।
‘জুলাই প্রোক্লেমেশন’ ভবিষ্যতে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে। বিএনপি যেভাবে এই প্রস্তাবের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিকে বিরোধিতা করছে, ঠিক বিপরীতে এনসিপি বলছে, নির্বাচন হবে এই ঘোষণাকে সংবিধানে যুক্ত করার পরেই। ফলে প্রস্তাবটি যদি একপক্ষের ইতিহাসকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে তা জাতীয় ঐক্যের বদলে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।
আন্তর্জাতিক মহল ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথের দিকে নজর রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা সতর্ক করে বলেছে—গণতন্ত্রে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। একটি ত্রুটিপূর্ণ বা বর্জিত নির্বাচন আন্তর্জাতিক নিন্দা ডেকে আনতে পারে, বিদেশি বিনিয়োগ কমে যেতে পারে, এমনকি নিষেধাজ্ঞা বা কূটনৈতিক চাপও আসতে পারে।
সবশেষে বলা যায়—ড. ইউনূসের ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ঘোষণা শুধু একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান দেয়নি। বিএনপি এখন পর্যন্ত আগ্রহ দেখালেও এনসিপি ও জামায়াতের নীরবতা অনেক কিছু বলছে। তাদের অংশগ্রহণ এখনো শর্তসাপেক্ষ, দাবি অনেকটাই অপূর্ণ, আর রাজনৈতিক ময়দান ভীষণভাবে খণ্ডিত। সময় যত এগোচ্ছে ফেব্রুয়ারির দিকে, ততই বোঝা যাচ্ছে—অনিশ্চয়তা শেষ হয়নি, বরং তা এখন কিছু সময়ের জন্য থেমে আছে।
লেখক: সাংবাদিক

৫ আগস্ট ২০২৫ বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঘোষণা দেন—ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, রমজানের আগেই। এই ঘোষণা ছিল এক ধরনের মাইলফলক, যার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটানো এবং ২০২৪ সালের জুলাই মাসের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে যে অস্থিরতা চলছিল, তা কিছুটা হলেও স্থিতিশীল করা। ওই গণ-অভ্যুত্থানেই শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার পতনের মুখে পড়ে।
ঘোষণার পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি এটিকে স্বাগত জানায়। তারা মনে করে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা দেশের নির্বাচনী অনিশ্চয়তা দূর করবে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) ও জামায়াতে ইসলামীর নীরবতা নতুন প্রশ্ন তুলেছে—এই নির্বাচন আসলেই কি সবার জন্য নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য?
ড. ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার যে দায়িত্ব নিয়ে ক্ষমতায় আসে, তার তিনটি মূল লক্ষ্য ছিল—প্রথমত, অভ্যুত্থানের সময় ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিচার করা, দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়ন করা এবং তৃতীয়ত, গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা। কিন্তু সরকার গঠনের পর থেকেই সময়সূচি নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব শুরু হয়।
বিএনপি, যাদের এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতিতে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল, তারা চাইছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হোক, যাতে তারা নিজেদের অবস্থান ফের শক্ত করতে পারে। তবে এনসিপি ও জামায়াত মনে করে, আগে সংবিধান সংস্কার ও নির্বাচন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দরকার—তারপরেই জাতীয় নির্বাচন দেওয়া যেতে পারে।
প্রথমদিকে ইউনূস বলেছিলেন, নির্বাচন ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে জুন ২০২৬ এর মধ্যে যে কোনো সময়ে হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারিকে বেছে নেওয়া হয়েছে—যা বিএনপির চাপ এবং লন্ডন বৈঠকের ফল বলেই মনে করছেন অনেকে।
রাজনৈতিক চিত্রকে আরও জটিল করে তোলে ‘জুলাই প্রোক্লেমেশন’ নামে ২৬ দফার সংস্কার-প্রস্তাবনা। এই প্রস্তাবটি মূলত অভ্যুত্থানের চেতনাকে সংবিধানে স্থায়ীভাবে যুক্ত করার উদ্দেশ্যে তৈরি। এতে অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী অনেক ছাত্রনেতার প্রতি সম্মান জানানো হয়েছে—এদের অনেকেই এখন এনসিপির নেতৃত্বে আছেন। তবে প্রস্তাবটি ঘিরে মতভেদ দেখা দেয়।
বিএনপি এই প্রস্তাবের প্রতীকী দিকটি মেনে নিলেও সংবিধানে তা যুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। তারা মনে করে, সময়মতো নির্বাচনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এনসিপি ও জামায়াত উভয়েই এই প্রস্তাবকে তড়িঘড়ি করে তৈরি ও সুনির্দিষ্টতা-বিহীন বলে নাকচ করে দেয়।
এসব মতবিরোধের মধ্যে দিয়ে রাজনীতির গভীর বিভাজন প্রকাশ পেয়েছে। এনসিপি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেয়নি। তারা বলছে, সবার আগে প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, এবং স্বচ্ছ নির্বাচনী কাঠামো। এসব ছাড়া তারা নির্বাচনে যাবে না।
জামায়াতের অবস্থানও একইরকম অস্পষ্ট। শুরুতে তারা ফেব্রুয়ারির সময়সূচিকে সমর্থন করলেও পরে বলেছে, নির্বাচন অংশগ্রহণের আগে প্রয়োজন কাঠামোগত সংস্কার, যার মধ্যে ‘প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন’ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত।
এদিকে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো খুবই নাজুক। অভ্যুত্থানের পর রাজপথে বিক্ষোভ, ছত্রভঙ্গ জনতা, হঠাৎ হঠাৎ সহিংসতা ইত্যাদি চলছে, যা সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়।
যদি শেষ পর্যন্ত এনসিপি ও জামায়াত নিজেদের দাবি পূরণ না হওয়ার কারণে নির্বাচন বর্জন করে, তাহলে তা বড় ধরনের বৈধতা-সংকটে ফেলতে পারে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থাকে। এনসিপি, যাদের মূলভিত্তি ছাত্রদের নেতৃত্বে গড়া অভ্যুত্থানে, এখন গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাদের অনুপস্থিতি নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতাকে বড়ভাবে প্রশ্নের মুখে ফেলবে। একইসঙ্গে জামায়াত না থাকলে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।
‘জুলাই প্রোক্লেমেশন’ ভবিষ্যতে বড় ধরনের রাজনৈতিক সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে। বিএনপি যেভাবে এই প্রস্তাবের সংবিধানে অন্তর্ভুক্তিকে বিরোধিতা করছে, ঠিক বিপরীতে এনসিপি বলছে, নির্বাচন হবে এই ঘোষণাকে সংবিধানে যুক্ত করার পরেই। ফলে প্রস্তাবটি যদি একপক্ষের ইতিহাসকে অন্যদের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাহলে তা জাতীয় ঐক্যের বদলে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।
আন্তর্জাতিক মহল ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথের দিকে নজর রাখছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ও বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা সতর্ক করে বলেছে—গণতন্ত্রে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। একটি ত্রুটিপূর্ণ বা বর্জিত নির্বাচন আন্তর্জাতিক নিন্দা ডেকে আনতে পারে, বিদেশি বিনিয়োগ কমে যেতে পারে, এমনকি নিষেধাজ্ঞা বা কূটনৈতিক চাপও আসতে পারে।
সবশেষে বলা যায়—ড. ইউনূসের ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ঘোষণা শুধু একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান দেয়নি। বিএনপি এখন পর্যন্ত আগ্রহ দেখালেও এনসিপি ও জামায়াতের নীরবতা অনেক কিছু বলছে। তাদের অংশগ্রহণ এখনো শর্তসাপেক্ষ, দাবি অনেকটাই অপূর্ণ, আর রাজনৈতিক ময়দান ভীষণভাবে খণ্ডিত। সময় যত এগোচ্ছে ফেব্রুয়ারির দিকে, ততই বোঝা যাচ্ছে—অনিশ্চয়তা শেষ হয়নি, বরং তা এখন কিছু সময়ের জন্য থেমে আছে।
লেখক: সাংবাদিক

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে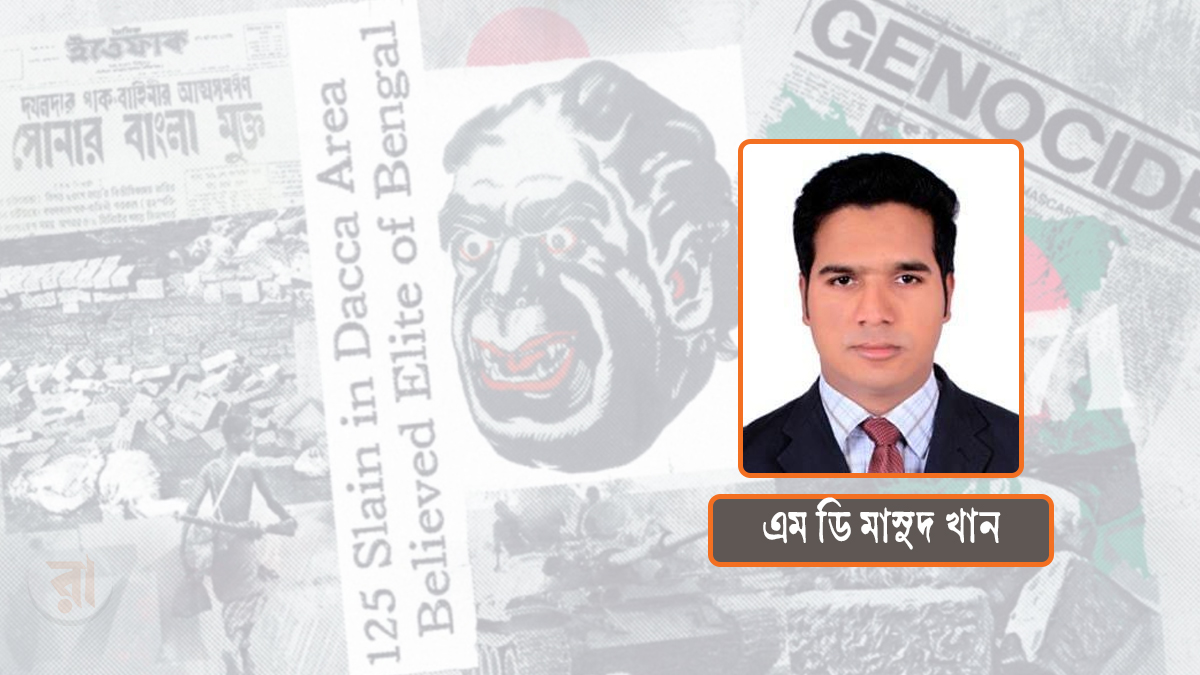
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে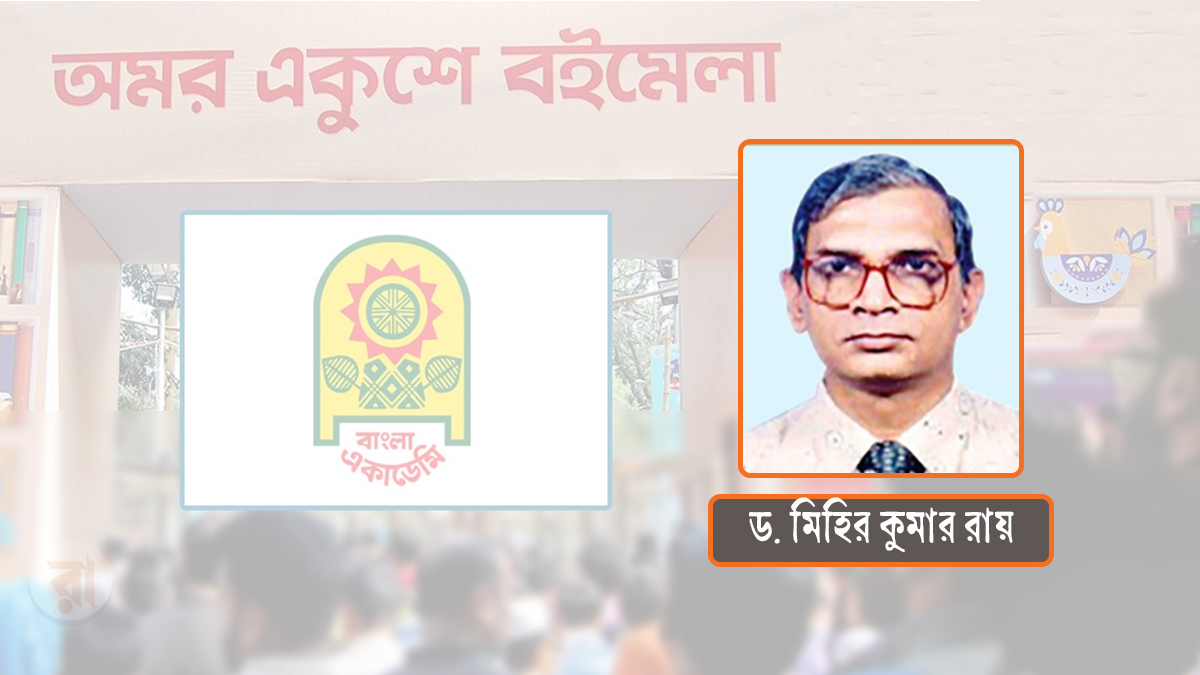
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১১ দিন আগে