
অরুণ কুমার

আধুনিক রান্নাঘরের সঙ্গে গ্রামবাংলার পরিচিত রান্নাঘরের আকাশ-পাতাল তফাত। সেকালের গ্রামীণ গ্রহস্থ পরিবারে রান্নাঘর ছিল বিশেষ কিছু। শহুরে রান্নাঘরের মতো শোবার ঘরের পাশাপাশেই রান্নাঘরি ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। শহরে আসলে ফ্ল্যাট বাসায় থাকে মানুষ। উঠোন নেই, তাই রান্নাঘর শোয়ার ঘর থেকে দূরে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
সেকালের গৃহস্থবাড়ির দুই প্রান্তে হতো শোবার ও রান্নাঘরের অবস্থান। এর অবশ্য কারণ আছে। প্রথম কারণ অবশ্যই আগুন লাগার ভয়।
রান্নাঘরে আগুন নিয়ে কারবার। তাই প্রায়ই আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা কম ছিল না। কিন্তু সেই আগুন যেন দ্রুত ছড়িয়ে না পড়তে পারে, এ জন্য রান্নাঘর থাকত শোবার ঘর থেকে দূরে। এতে শোবার ঘরের দামি জিনিসপত্র বেঁচে যেত সহজেই।
রান্নাঘর দূরে হওয়ার আরেকটা সুবিধা ছিল। কাঠ পুড়িয়ে রান্না করা হতো। ধোঁয়া হতো প্রচুর। সেই ধোঁয়াও শোবার ঘরে এসে সমস্যা করতে পারত না দূরে হওয়ার কারণে।
আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রান্নাঘর বা হেঁশেলের রকমফের হতো। দরিদ্রের হেঁশেল ঘর দাঁড়িয়ে থাকত বাঁশ-কঞ্চির বেড়ার ওপর। চাল হিসেবে তালাপাতা, পাটখড়ি বা ত্রিপল। গৃহস্থের হেঁশেল মাটির তৈরি, বাঁশের চটাও হতো। তবে চাল হিসেবে কেউ ব্যবহার করতেন টালি, কারও ঘরের খড় বা নাড়া দিয়ে ছাওয়া।
রান্নাঘরের এককোণে মাটির চুলা, পাশেই কিছু জ্বালানি। হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখার জন্য একাধিক শিকে। কারও কারও ঘরে আলমারিও থাকত। একটা মই ঝুলানো থাকত। মইয়ের ওপর যেসব হাঁড়ি-পাতিল কম ব্যবহার করা হয় সেগুলো রাখা হতো।
হেঁশেল ঘরের একটা অংশ ব্যবহার করা হতো ভাঁড়ার ঘর হিসেবে। রান্নাঘরগুলো হতো দোচালা। একটির সঙ্গে আরেকটা ঠেস, লম্বা পিরামিডের মতো করে। তাই দেয়ালের মাথা থেকে চালের শীর্ষরেখা পর্যন্ত ফাঁকা থাকে। সামনে দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত আড়াআড়ি করে রাখা হতো মোটা বাঁশ। এগুলোকে বলা হতো আড়া। আড়ার ওপর আবার বাঁশের মাচা। একে বলে আড়মাচা। আড়মাচায় সারা বছরের জন্য জমিয়ে রাখা হতো রসুন, পেঁয়াজ, কখনো কখনো ধানের বস্তাও রাখা হতো। হেঁশেলের চুলার ঠিক পেছনেই কলস, মাটির কিংবা কাঁসার, খাবার পানির জন্য। এককাণে থাকত মালসা বা শানকি, ভাতের মাড় গালবার জন্য।
হেঁশেলের অর্ধেক রান্নাবান্নার জন্য, বাকি অর্ধেক ভাঁড়ার ঘর। কারও কারও রান্নাঘরে বিশালাকৃতির মাটির হাঁড়া রাখা হতো। পেল্লায় আকারের কলসের মতো দেখতে। তুলনায় মুখ ও গলা অনেক ছোট। হাঁড়ার পেটের ভেতরে রাখা হতো প্রতিদিনকার রান্নার চাল।
রান্নাঘরের এককোণে রাখা হয় আলু। সারা বছর খাওয়ার জন্য। কেউ কেউ রান্নাঘরের এ দিকটায় ছাগল বাঁধার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতেন। যাদের আমা কাঁঠালেন বাগান আছে, তারা এই কোণে রাখতে নিজেদের খাওয়ার জন্য এসব ফল।
একটু বড় গৃহস্থ যারা, তাদের রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর আলাদা। ভাঁড়ার ঘরে আরও বহু জিনিস রাখত তারা- এক পাশে মাচা কিংবা ইট দিয়ে উঁচু করে তার ওপর রাখা হতো ধান-চাল বিভিন্ন ডালের বস্তা। কারও পাটের আঁটি। ড্রাম থাকত এক কোণে, ধান, মুগ মুসর, কিংবা গমের বীজ।
কেউ কেউ যেমন রান্নাঘরকে ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন, কারও কারও শোবার ঘরটাই ছিল ভাঁড়ার ঘর। যে যেটিই ব্যবহার করুন না কেন, ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আর জিনিসপত্র একই।

আধুনিক রান্নাঘরের সঙ্গে গ্রামবাংলার পরিচিত রান্নাঘরের আকাশ-পাতাল তফাত। সেকালের গ্রামীণ গ্রহস্থ পরিবারে রান্নাঘর ছিল বিশেষ কিছু। শহুরে রান্নাঘরের মতো শোবার ঘরের পাশাপাশেই রান্নাঘরি ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। শহরে আসলে ফ্ল্যাট বাসায় থাকে মানুষ। উঠোন নেই, তাই রান্নাঘর শোয়ার ঘর থেকে দূরে হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
সেকালের গৃহস্থবাড়ির দুই প্রান্তে হতো শোবার ও রান্নাঘরের অবস্থান। এর অবশ্য কারণ আছে। প্রথম কারণ অবশ্যই আগুন লাগার ভয়।
রান্নাঘরে আগুন নিয়ে কারবার। তাই প্রায়ই আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনা কম ছিল না। কিন্তু সেই আগুন যেন দ্রুত ছড়িয়ে না পড়তে পারে, এ জন্য রান্নাঘর থাকত শোবার ঘর থেকে দূরে। এতে শোবার ঘরের দামি জিনিসপত্র বেঁচে যেত সহজেই।
রান্নাঘর দূরে হওয়ার আরেকটা সুবিধা ছিল। কাঠ পুড়িয়ে রান্না করা হতো। ধোঁয়া হতো প্রচুর। সেই ধোঁয়াও শোবার ঘরে এসে সমস্যা করতে পারত না দূরে হওয়ার কারণে।
আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে রান্নাঘর বা হেঁশেলের রকমফের হতো। দরিদ্রের হেঁশেল ঘর দাঁড়িয়ে থাকত বাঁশ-কঞ্চির বেড়ার ওপর। চাল হিসেবে তালাপাতা, পাটখড়ি বা ত্রিপল। গৃহস্থের হেঁশেল মাটির তৈরি, বাঁশের চটাও হতো। তবে চাল হিসেবে কেউ ব্যবহার করতেন টালি, কারও ঘরের খড় বা নাড়া দিয়ে ছাওয়া।
রান্নাঘরের এককোণে মাটির চুলা, পাশেই কিছু জ্বালানি। হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখার জন্য একাধিক শিকে। কারও কারও ঘরে আলমারিও থাকত। একটা মই ঝুলানো থাকত। মইয়ের ওপর যেসব হাঁড়ি-পাতিল কম ব্যবহার করা হয় সেগুলো রাখা হতো।
হেঁশেল ঘরের একটা অংশ ব্যবহার করা হতো ভাঁড়ার ঘর হিসেবে। রান্নাঘরগুলো হতো দোচালা। একটির সঙ্গে আরেকটা ঠেস, লম্বা পিরামিডের মতো করে। তাই দেয়ালের মাথা থেকে চালের শীর্ষরেখা পর্যন্ত ফাঁকা থাকে। সামনে দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত আড়াআড়ি করে রাখা হতো মোটা বাঁশ। এগুলোকে বলা হতো আড়া। আড়ার ওপর আবার বাঁশের মাচা। একে বলে আড়মাচা। আড়মাচায় সারা বছরের জন্য জমিয়ে রাখা হতো রসুন, পেঁয়াজ, কখনো কখনো ধানের বস্তাও রাখা হতো। হেঁশেলের চুলার ঠিক পেছনেই কলস, মাটির কিংবা কাঁসার, খাবার পানির জন্য। এককাণে থাকত মালসা বা শানকি, ভাতের মাড় গালবার জন্য।
হেঁশেলের অর্ধেক রান্নাবান্নার জন্য, বাকি অর্ধেক ভাঁড়ার ঘর। কারও কারও রান্নাঘরে বিশালাকৃতির মাটির হাঁড়া রাখা হতো। পেল্লায় আকারের কলসের মতো দেখতে। তুলনায় মুখ ও গলা অনেক ছোট। হাঁড়ার পেটের ভেতরে রাখা হতো প্রতিদিনকার রান্নার চাল।
রান্নাঘরের এককোণে রাখা হয় আলু। সারা বছর খাওয়ার জন্য। কেউ কেউ রান্নাঘরের এ দিকটায় ছাগল বাঁধার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতেন। যাদের আমা কাঁঠালেন বাগান আছে, তারা এই কোণে রাখতে নিজেদের খাওয়ার জন্য এসব ফল।
একটু বড় গৃহস্থ যারা, তাদের রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর আলাদা। ভাঁড়ার ঘরে আরও বহু জিনিস রাখত তারা- এক পাশে মাচা কিংবা ইট দিয়ে উঁচু করে তার ওপর রাখা হতো ধান-চাল বিভিন্ন ডালের বস্তা। কারও পাটের আঁটি। ড্রাম থাকত এক কোণে, ধান, মুগ মুসর, কিংবা গমের বীজ।
কেউ কেউ যেমন রান্নাঘরকে ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন, কারও কারও শোবার ঘরটাই ছিল ভাঁড়ার ঘর। যে যেটিই ব্যবহার করুন না কেন, ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আর জিনিসপত্র একই।

‘এমন যদি হতো/ ইচ্ছে হলে আমি হতাম/ প্রজাপতির মতো...’ পঙ্ক্তির এমন যদি হতো কিংবা ‘ধন্য সবাই ধন্য/ অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করে/ মাতৃভূমির জন্য...’ পঙ্ক্তির মুক্তিসেনার মতো কালজয়ী সব ছড়া রচনা করে সুকুমার বড়ুয়া পেয়েছিলেন ‘ছড়াসম্রাট’ খ্যাতি।
১০ দিন আগে
বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, কিছু সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্ন ফেসবুক পেইজে উক্ত বিষয়টি ‘অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সকল কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা’ করা হয়েছে মর্মে সংবাদ প্রকাশ করে, বিষয়টি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক বলে উল্লেখ করা হয়।
২৩ দিন আগে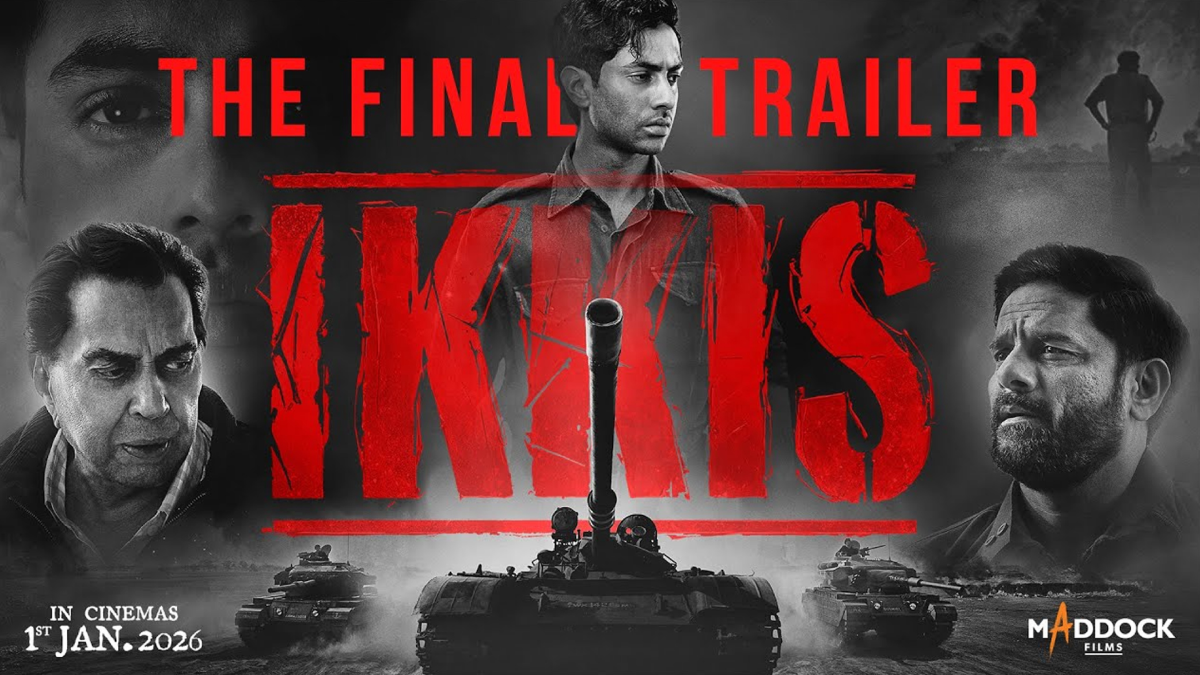
একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ চলচ্চিত্রটির মুক্তির তারিখ এর আগে তিন দফা পরিবর্তন করা হয়। সবশেষ নির্ধারিত তারিখ ছিল আগামী ২৫ ডিসেম্বর।
২৩ দিন আগে
১৬ ডিসেম্বর ছিল সেই দিন, যেদিন প্রমাণিত হয়েছিল— একটি নিরস্ত্র জাতি যখন স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তখন পৃথিবীর কোনো পরাশক্তি বা আধুনিক সমরাস্ত্র তাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। মার্কিন সপ্তম নৌ বহর বঙ্গোপসাগরের নীল জলেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। আর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সব কূটচাল ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল বাঙা
১৬ ডিসেম্বর ২০২৫