
এ কে এম মাহফুজুর রহমান

১৬ অক্টোবর ২০২৫। এইচএসসি ও সমমানের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই শিক্ষাঙ্গন ও অভিভাবকদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— জিপিএ-৫ কি সত্যিই গুণগত শিক্ষার প্রতিফলন? নাকি কেবল সংখ্যার খেলা?
এবার সারা দেশে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। জিপিএ-৫ অর্জন করেছে ৬৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী, যা ২০২৪ সালের এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জনের তুলনায় ৭৬ হাজার ৮১৪ কম, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।
বোর্ডভিত্তিক পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ, বরিশালে ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ, ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ, দিনাজপুরে ৫৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ, সিলেটে ৫১ দশমিক ৮৬ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ, যশোর শিক্ষা বোর্ডে ৫০ দশমিক ২০ শতাংশ ও কুমিল্লায় ৪৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
লিঙ্গভিত্তিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে— মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছে। মেয়েদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৯৭ শতাংশ, ছেলেদের ৫৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। আবার মেয়েদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৪৪ জন, যেখানে ছেলেদের মধ্যে এ সংখ্যা ৩২ হাজার ৫৩ জন।
এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেমে এসেছে এক হাজার ৩৮৮টি থেকে ৩৪৫টিতে। অন্যদিকে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জনে।
এ পরিসংখ্যানগুলোই বলে দিচ্ছে, শুধু জিপিএ-৫ গোনার মাধ্যমে শিক্ষার মান বিচার করা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। প্রশ্নের মান, মূল্যায়নের সমতা, শিক্ষকের দক্ষতা, স্কুলভিত্তিক প্রস্তুতি ও অঞ্চলভেদে সুযোগের বৈষম্য— সবকিছুরই প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়েছে এবারের ফলে।
গত তিন বছরের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিপিএ-৫ একটি ‘নীতি-সংবেদনশীল সূচক’। এটি শিক্ষার মানের ধারাবাহিক প্রতিফলন নয়। ২০২৩ সালে পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৯২ হাজার ৩৬৫ জন।
২০২৪ সালে পাসের হার কিছুটা কমে ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশে নামলেও জিপিএ-৫ বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জনে। আর এ বছর পাসের হার কমে ৫৮ শতাংশের ঘরে নেমে আসার পাশাপাশি জিপিএ-৫ নেমেছে ৬৯ হাজারের ঘরে। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে ৫০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা।
নটর ডেম কলেজের ইংরেজি সংস্করণের জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী মুস্তাকিম মাহফুজ আদৃত এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়, ‘গ্রেস মার্কস সঠিকভাবে দেওয়া হলে, একই নির্দেশনা অনুসারে সব খাতা মূল্যায়ন করা হলে এবং ইংরেজি সংস্করণের খাতা ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করলে ফলাফল আরও ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারত।”
তার মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অভিন্ন মানদণ্ড ও দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, যা আজকের শিক্ষাব্যবস্থার বড় ঘাটতি।
জিপিএ-৫ নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় সাফল্যের একটি প্রতীক, কিন্তু ‘গুণগত শিক্ষা’ নয়। কারণ গুণগত শিক্ষার আসল মানে হলো চিন্তা, বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা, গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান, দলগত কাজ ও নৈতিকতা। আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি এখনো মুখস্থনির্ভর ও প্রশ্নকেন্দ্রিক। ফলে প্রশ্নের মান বা মূল্যায়নের নীতিতে সামান্য পরিবর্তন এলেই জিপিএ-৫-এর সংখ্যা দুলে ওঠে।
এবারের ফলাফল তাই একদিকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবতায় ফেরার ইঙ্গিত দিলেও অন্যদিকে এটি বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে। অনেক পরিবারে মানসিক চাপ বেড়েছে এবং নিম্ন-সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলে শেখার ফাঁক আরও গভীর হয়েছে।
অভিভাবকদের প্রশ্ন তাই যুক্তিযুক্ত— এই বিপুল সংখ্যক অকৃতকার্য শিক্ষার্থী কি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে? নাকি এ ফলাফল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে গঠন করার একটি সুযোগ এনে দিচ্ছে?
এ পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই আছে। নেতিবাচক দিকে দুর্বল স্কুল ও নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষক সংকট, কোচিং নির্ভরতা, ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা, আর্থসামাজিক বৈষম্য— সব মিলিয়ে এই গোষ্ঠীতে অকৃতকার্যতার হার বেশি। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যদি জিপিএ কাট-অফ অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে অনেক যোগ্য শিক্ষার্থীও বাদ পড়বে।
ইতিবাচক দিকে জিপিএ-৫ কমে যাওয়ার অর্থ ‘গ্রেড ইনফ্লেশনে’র লাগাম টানা। এতে মেধা বাছাই তুলনামূলক নিরপেক্ষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন জিপিএর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা, রচনা, প্রজেক্ট, পোর্টফোলিও ও সাক্ষাৎকারের ওপর জোর দিতে পারবে।
একই সঙ্গে বোর্ডভিত্তিক পার্থক্য কমাতে প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা, দুর্বল স্কুলের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্স, ডায়াগনস্টিক টেস্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রিমেডিয়েশন প্রোগ্রাম। প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে কোন অংশে শিক্ষার্থীরা বেশি হোঁচট খাচ্ছে তা নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ পরীক্ষার মান ও বোর্ডভিত্তিক সমতা বজায় না থাকলে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম অনেক সময় বিফল হয়ে যায়।
আজকের বিশ্বে প্রশ্নটা আর শুধু পরীক্ষার নয়, বরং প্রশ্নটা হলো— ‘উজ্জ্বল স্কোরকার্ড’ নাকি ‘দৃঢ় বুনিয়াদ’? বর্তমান যুগে কর্মক্ষেত্র ও উচ্চ শিক্ষায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, দলগত নেতৃত্ব ও নৈতিকতা। জিপিএ-৫ এগুলোর নিশ্চয়তা দেয় না, তবে নিয়মিত পরিশ্রমের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, ইংরেজি যোগাযোগ ও ব্যবহারিক দক্ষতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।
তাই জিপিএ-৫ এখন ‘একটি সূচক’, ‘একমাত্র সূচক’ নয়। ২০২৫ সালের ফলাফল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক মাননিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী না হলে জাতীয় শিক্ষার মান কখনোই স্থিতিশীল হবে না। অভিভাবকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন প্রয়োজন তিনটি জরুরি পদক্ষেপ—
টেকসই ও দৃঢ় ভিত্তির শিক্ষাই ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি। গত তিন বছরের ফলাফল প্রমাণ করেছে, নীতির সামান্য পরিবর্তনেই ‘শীর্ষ গ্রেড’ দুলে ওঠে। তাই গুণগত শিক্ষা মাপতে একক সংখ্যা নয়, প্রয়োজন ধারাবাহিক, স্বচ্ছ ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন কাঠামো। নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান— প্রশ্নের মান ও সমতা বজায় রেখে এমন মূল্যায়ন তৈরি করুন, যা সত্যিকারের শেখার ফলাফল তুলে ধরে, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণ, প্রয়োগ, সৃজনশীলতা, যোগাযোগ, নৈতিকতা ও প্রযুক্তিদক্ষতা।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জিপিএকে ‘ফ্লোর’ হিসেবে ব্যবহার করুক, ‘সিলিং’ নয়। অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ— ফলাফলের সংখ্যার চেয়ে সন্তানের ধারণাগত বোঝাপড়া, নিয়মিত অধ্যবসায়, প্রকল্পকাজ, ভাষা-সংখ্যাজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব দিন। কারণ, উজ্জ্বল স্কোরকার্ড নয়, দৃঢ় বুনিয়াদই শেষ কথা। সেই বুনিয়াদই তৈরি করবে ভবিষ্যত-প্রস্তুত এক শিক্ষার্থী, এক সচেতন পরিবার ও এক সক্ষম বাংলাদেশ।
লেখক: ডেপুটি ডিরেক্টর-ফ্যাকাল্টি এইচআর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি; সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন

১৬ অক্টোবর ২০২৫। এইচএসসি ও সমমানের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই শিক্ষাঙ্গন ও অভিভাবকদের মনে একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে— জিপিএ-৫ কি সত্যিই গুণগত শিক্ষার প্রতিফলন? নাকি কেবল সংখ্যার খেলা?
এবার সারা দেশে পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত দুই দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন। জিপিএ-৫ অর্জন করেছে ৬৯ হাজার ৯৭ জন শিক্ষার্থী, যা ২০২৪ সালের এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জনের তুলনায় ৭৬ হাজার ৮১৪ কম, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম।
বোর্ডভিত্তিক পার্থক্যও বেশ স্পষ্ট। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ, বরিশালে ৬২ দশমিক ৫৭ শতাংশ, ৫৯ দশমিক ৪০ শতাংশ, দিনাজপুরে ৫৭ দশমিক ৪৯ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ, সিলেটে ৫১ দশমিক ৮৬ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ, যশোর শিক্ষা বোর্ডে ৫০ দশমিক ২০ শতাংশ ও কুমিল্লায় ৪৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ।
লিঙ্গভিত্তিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে— মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে এগিয়ে আছে। মেয়েদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৯৭ শতাংশ, ছেলেদের ৫৪ দশমিক ৬০ শতাংশ। আবার মেয়েদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ হাজার ৪৪ জন, যেখানে ছেলেদের মধ্যে এ সংখ্যা ৩২ হাজার ৫৩ জন।
এ বছর শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেমে এসেছে এক হাজার ৩৮৮টি থেকে ৩৪৫টিতে। অন্যদিকে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পাঁচ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জনে।
এ পরিসংখ্যানগুলোই বলে দিচ্ছে, শুধু জিপিএ-৫ গোনার মাধ্যমে শিক্ষার মান বিচার করা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। প্রশ্নের মান, মূল্যায়নের সমতা, শিক্ষকের দক্ষতা, স্কুলভিত্তিক প্রস্তুতি ও অঞ্চলভেদে সুযোগের বৈষম্য— সবকিছুরই প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়েছে এবারের ফলে।
গত তিন বছরের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, জিপিএ-৫ একটি ‘নীতি-সংবেদনশীল সূচক’। এটি শিক্ষার মানের ধারাবাহিক প্রতিফলন নয়। ২০২৩ সালে পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ, জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৯২ হাজার ৩৬৫ জন।
২০২৪ সালে পাসের হার কিছুটা কমে ৭৭ দশমিক ৭৮ শতাংশে নামলেও জিপিএ-৫ বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ জনে। আর এ বছর পাসের হার কমে ৫৮ শতাংশের ঘরে নেমে আসার পাশাপাশি জিপিএ-৫ নেমেছে ৬৯ হাজারের ঘরে। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে ৫০ শতাংশেরও বেশি কমে গেছে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা।
নটর ডেম কলেজের ইংরেজি সংস্করণের জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী মুস্তাকিম মাহফুজ আদৃত এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তার ভাষায়, ‘গ্রেস মার্কস সঠিকভাবে দেওয়া হলে, একই নির্দেশনা অনুসারে সব খাতা মূল্যায়ন করা হলে এবং ইংরেজি সংস্করণের খাতা ইংরেজিতে দক্ষ শিক্ষকেরা মূল্যায়ন করলে ফলাফল আরও ভারসাম্যপূর্ণ হতে পারত।”
তার মন্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে অভিন্ন মানদণ্ড ও দক্ষ পরীক্ষক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা, যা আজকের শিক্ষাব্যবস্থার বড় ঘাটতি।
জিপিএ-৫ নিঃসন্দেহে পরীক্ষায় সাফল্যের একটি প্রতীক, কিন্তু ‘গুণগত শিক্ষা’ নয়। কারণ গুণগত শিক্ষার আসল মানে হলো চিন্তা, বিশ্লেষণ, সমস্যা সমাধান, সৃজনশীলতা, গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও সংখ্যাজ্ঞান, দলগত কাজ ও নৈতিকতা। আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতি এখনো মুখস্থনির্ভর ও প্রশ্নকেন্দ্রিক। ফলে প্রশ্নের মান বা মূল্যায়নের নীতিতে সামান্য পরিবর্তন এলেই জিপিএ-৫-এর সংখ্যা দুলে ওঠে।
এবারের ফলাফল তাই একদিকে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় বাস্তবতায় ফেরার ইঙ্গিত দিলেও অন্যদিকে এটি বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে। অনেক পরিবারে মানসিক চাপ বেড়েছে এবং নিম্ন-সুবিধাপ্রাপ্ত অঞ্চলে শেখার ফাঁক আরও গভীর হয়েছে।
অভিভাবকদের প্রশ্ন তাই যুক্তিযুক্ত— এই বিপুল সংখ্যক অকৃতকার্য শিক্ষার্থী কি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে? নাকি এ ফলাফল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুনভাবে গঠন করার একটি সুযোগ এনে দিচ্ছে?
এ পরিবর্তনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই আছে। নেতিবাচক দিকে দুর্বল স্কুল ও নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষক সংকট, কোচিং নির্ভরতা, ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা, আর্থসামাজিক বৈষম্য— সব মিলিয়ে এই গোষ্ঠীতে অকৃতকার্যতার হার বেশি। আবার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় যদি জিপিএ কাট-অফ অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে অনেক যোগ্য শিক্ষার্থীও বাদ পড়বে।
ইতিবাচক দিকে জিপিএ-৫ কমে যাওয়ার অর্থ ‘গ্রেড ইনফ্লেশনে’র লাগাম টানা। এতে মেধা বাছাই তুলনামূলক নিরপেক্ষ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন জিপিএর পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা, রচনা, প্রজেক্ট, পোর্টফোলিও ও সাক্ষাৎকারের ওপর জোর দিতে পারবে।
একই সঙ্গে বোর্ডভিত্তিক পার্থক্য কমাতে প্রয়োজন লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা, দুর্বল স্কুলের জন্য ফাউন্ডেশন কোর্স, ডায়াগনস্টিক টেস্ট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রিমেডিয়েশন প্রোগ্রাম। প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে কোন অংশে শিক্ষার্থীরা বেশি হোঁচট খাচ্ছে তা নির্ধারণ করা জরুরি। কারণ পরীক্ষার মান ও বোর্ডভিত্তিক সমতা বজায় না থাকলে শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম অনেক সময় বিফল হয়ে যায়।
আজকের বিশ্বে প্রশ্নটা আর শুধু পরীক্ষার নয়, বরং প্রশ্নটা হলো— ‘উজ্জ্বল স্কোরকার্ড’ নাকি ‘দৃঢ় বুনিয়াদ’? বর্তমান যুগে কর্মক্ষেত্র ও উচ্চ শিক্ষায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন বিশ্লেষণী ক্ষমতা, যোগাযোগ দক্ষতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, দলগত নেতৃত্ব ও নৈতিকতা। জিপিএ-৫ এগুলোর নিশ্চয়তা দেয় না, তবে নিয়মিত পরিশ্রমের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ, ইংরেজি যোগাযোগ ও ব্যবহারিক দক্ষতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে।
তাই জিপিএ-৫ এখন ‘একটি সূচক’, ‘একমাত্র সূচক’ নয়। ২০২৫ সালের ফলাফল আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে, প্রাতিষ্ঠানিক মাননিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী না হলে জাতীয় শিক্ষার মান কখনোই স্থিতিশীল হবে না। অভিভাবকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন প্রয়োজন তিনটি জরুরি পদক্ষেপ—
টেকসই ও দৃঢ় ভিত্তির শিক্ষাই ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি। গত তিন বছরের ফলাফল প্রমাণ করেছে, নীতির সামান্য পরিবর্তনেই ‘শীর্ষ গ্রেড’ দুলে ওঠে। তাই গুণগত শিক্ষা মাপতে একক সংখ্যা নয়, প্রয়োজন ধারাবাহিক, স্বচ্ছ ও বহুমাত্রিক মূল্যায়ন কাঠামো। নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান— প্রশ্নের মান ও সমতা বজায় রেখে এমন মূল্যায়ন তৈরি করুন, যা সত্যিকারের শেখার ফলাফল তুলে ধরে, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্লেষণ, প্রয়োগ, সৃজনশীলতা, যোগাযোগ, নৈতিকতা ও প্রযুক্তিদক্ষতা।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জিপিএকে ‘ফ্লোর’ হিসেবে ব্যবহার করুক, ‘সিলিং’ নয়। অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ— ফলাফলের সংখ্যার চেয়ে সন্তানের ধারণাগত বোঝাপড়া, নিয়মিত অধ্যবসায়, প্রকল্পকাজ, ভাষা-সংখ্যাজ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব দিন। কারণ, উজ্জ্বল স্কোরকার্ড নয়, দৃঢ় বুনিয়াদই শেষ কথা। সেই বুনিয়াদই তৈরি করবে ভবিষ্যত-প্রস্তুত এক শিক্ষার্থী, এক সচেতন পরিবার ও এক সক্ষম বাংলাদেশ।
লেখক: ডেপুটি ডিরেক্টর-ফ্যাকাল্টি এইচআর, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি; সাবেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
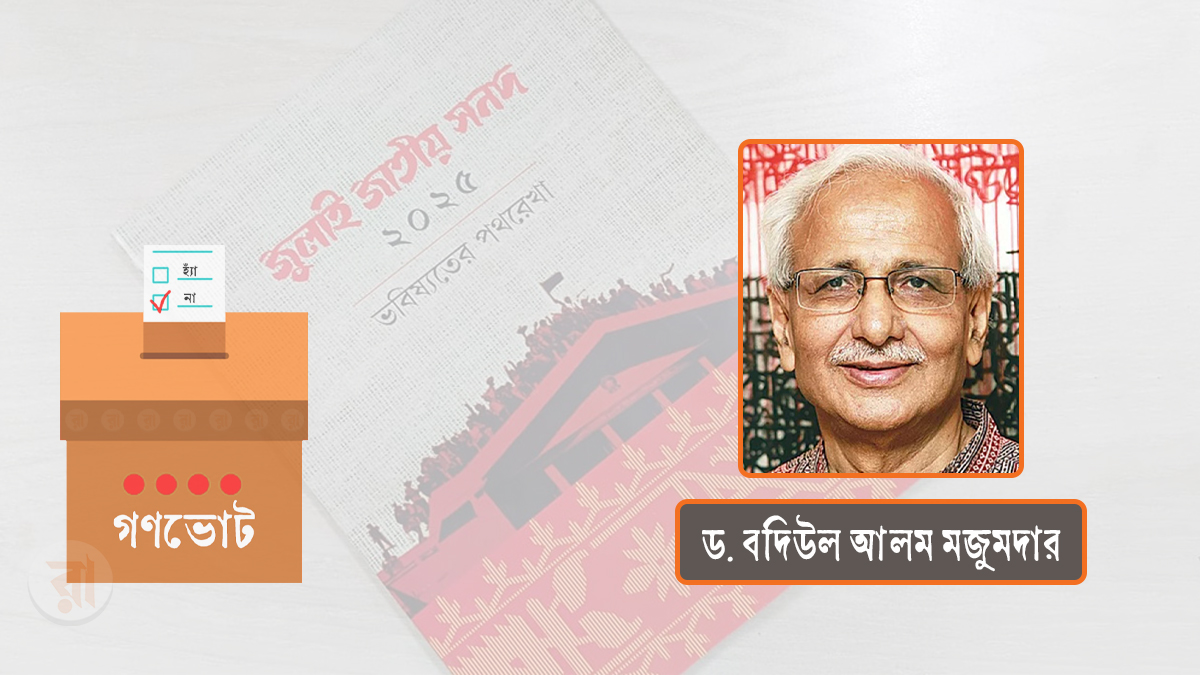
‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল, যাতে দেশে বিদ্যমান সক্রিয় প্রায় সব দল সই করেছে। যেহেতু সংবিধান হলো ‘উইল অব দ্য পিপল’ বা জনগণের চরম অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি, তাই জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে জনগণের সম্মতি বা গণভোট আয়ো
৫ দিন আগে
ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে যুক্ত থেকেও নিজেদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন অবস্থান নিয়েছে (European Council on Foreign Relations, ২০২৩)। এ অভিজ্ঞতা দেখায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কতটা জরুরি।
৫ দিন আগে
এই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকেই আসে ‘নতুন বাংলাদেশে’র ধারণা। এটি কোনো সাময়িক রাজনৈতিক স্লোগান নয়; এটি একটি নৈতিক অঙ্গীকার, একটি সামাজিক চুক্তি— যেখানে রাষ্ট্র হবে মানুষের সেবক, প্রভু নয়।
৬ দিন আগে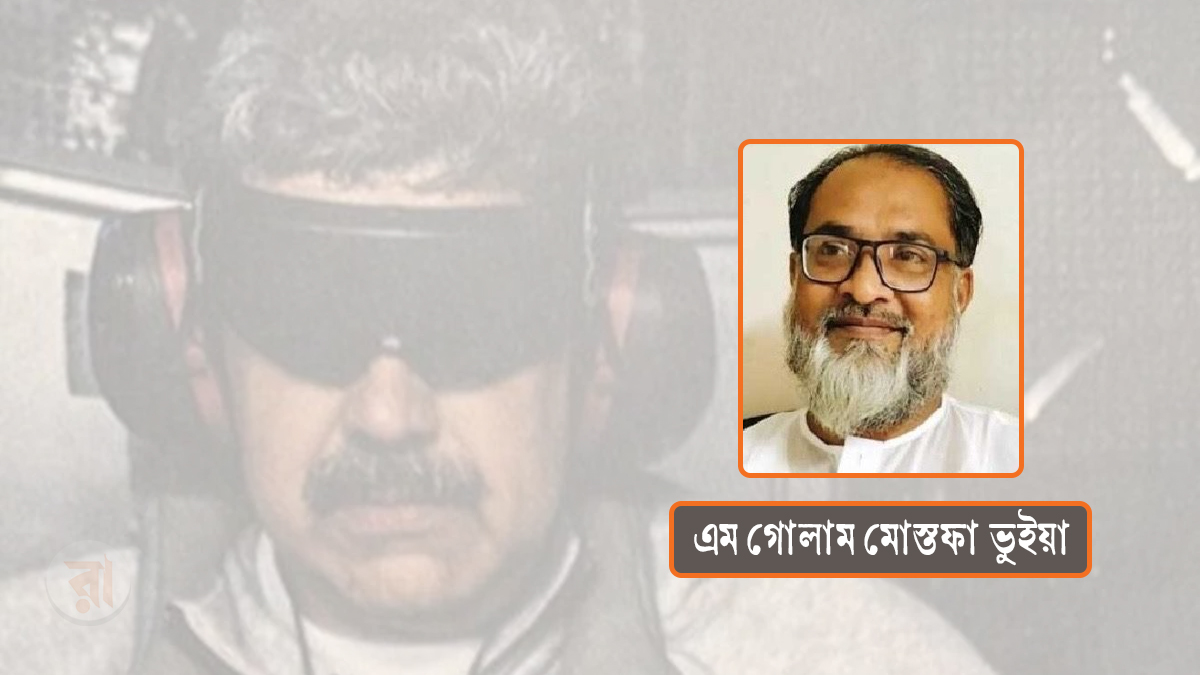
আন্তর্জাতিক আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে, আইনকে পদদলিত করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে গেছে, সেই দৃশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতিরই নগ্ন বহির্প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।
৭ দিন আগে