
টিম রাজনীতি ডটকম

৩১ ঘণ্টার ব্যবধানে চার চারটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ। এক সপ্তাহ পর ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও দুটি ভূমিকম্প হয়েছে কক্সবাজার ও ঢাকায়। এর মধ্যে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার প্রথম ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে দেশ জুড়ে, তাতে ঢাকা-নরসিংদী-নারায়ণগঞ্জে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০ জন। একের পর এক ভূমিকম্প আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা দেশের মানুষের মধ্যে। ছড়িয়ে পড়ছে ভূমিকম্প নিয়ে নানা তথ্য-অপতথ্য-অর্ধসত্য তথ্য। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েই চলেছে।
ভূমিকম্প নিয়ে নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রাজনীতি ডটকম কথা বলেছে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ড. মো. জিল্লুর রহমানের সঙ্গে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন, ডিজ্যাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া (ইউবিসি) থেকে জিওটেকনিক্যাল আর্থকোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি, এর আগে নেদারল্যান্ডস থেকে জিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে করেছেন এমএসসি।
গত ৩০ বছর ধরে ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত অধ্যাপক জিল্লুর রহমান রাজনীতি ডটকমের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপচারিতায় তুলে ধরেছেন ভূমিকম্পের কারণ ও ঝুঁকির বিভিন্ন দিক। বলেছেন ভূমিকম্প প্রসঙ্গে কীভাবে সচেতনত থাকা যায়, ভূমিকম্প হলে করণীয়ই বা কী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাজনীতি ডটকমের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল ইসলাম হৃদয়, ভিডিও ধারণ করেছেন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রবিউল ইসলাম, ভিডিও সম্পাদনা করেছেন আরেক মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রায়হান হক।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্প কেন হয়, খুব সহজ করে যদি বুঝিয়ে বলতেন...
জিল্লুর রহমান: সহজ কথায় ভূমিকম্প হলো একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই হয়ে আসছে। এর মূল কারণ হলো ভূ-অভ্যন্তরে থাকা বিশাল সব ফাটল, যেগুলোকে ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা হয় ‘ফল্ট’। ধরুন, ভূ-অভ্যন্তরে একটি লম্বা ফাটল রেখা বা লাইন আছে। কোনো কারণে যদি সেই লাইন বরাবর মাটি ভেঙে যায় বা ‘ডিসপ্লেসমেন্ট’ হয়, তখন সেখানে প্রচুর শক্তি বা এনার্জি রিলিজ হয়। সেই এনার্জি ঢেউ বা ‘ওয়েভ’ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ যখন আপনার পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দেয় এবং আপনি সেটা অনুভব করেন, তখন আমরা বলি ভূমিকম্প হয়েছে।
রাজনীতি ডটকম: গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে বাংলাদেশে। এর পেছনে কি নির্দিষ্ট কোনো ভূতাত্ত্বিক কারণ আছে?
জিল্লুর রহমান: অবশ্যই। ভূমিকম্পের মূল কারণই ভূতাত্ত্বিক। পৃথিবীর ওপরের শক্ত স্তর বা ভূ-ত্বকে যখন দুটি বিশাল মাটির ব্লক একটি আরেকটির সাপেক্ষে নড়ে যায় বা সরে যায়, তখনই কম্পন সৃষ্টি হয়। তবে শুধু প্রাকৃতিক কারণে নয়, বর্তমানে মানুষের তৈরি কারণেও ছোটখাটো ভূমিকম্প হতে পারে। যেমন— মাটির নিচে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা করলে ভূমিকম্প হয়। এমনকি আপনার পাশ দিয়ে যদি একটি ভারী ট্রাক চলে যায়, তখন যে কম্পন হয়, সেটাও এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র ভূমিকম্প, যাকে আমরা বলি ‘মাইক্রো ট্রেমর’। তবে বড় আকারের ফাটল বা মুভমেন্ট হলে সেটাকে আমরা মূল ভূমিকম্প হিসেবে গণ্য করি।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের অগ্রিম পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব কি?
জিল্লুর রহমান: ঠিক ‘পূর্বাভাস’ না হলেও বর্তমানে প্রযুক্তির সাহায্যে ভূমিকম্পের ‘আর্লি ওয়ার্নিং’ বা ‘তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা’ দেওয়া সম্ভব। ভূমিকম্পের সময় সাধারণত একাধিক ‘ওয়েভ’ বা ঢেউ তৈরি হয়। অনেকেই অভিজ্ঞতায় বলেন, প্রথমে হালকা একটু কাঁপুনি অনুভূত হলো (ছোট ওয়েভ), তার কিছুক্ষণ পরেই শক্তিশালী ঝাঁকুনি (বড় ওয়েভ) আঘাত হানল। মূলত এই পরবর্তী ওয়েভগুলোই প্রলয়ংকরী বা ধ্বংসাত্মক হয়, প্রথম ওয়েভে সাধারণত তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না।
ফলে যখনই ভূমিকম্পের এই প্রথম বা প্রাথমিক ওয়েভটি তৈরি হয়, তখনই যদি সেন্সরের মাধ্যমে সেই তথ্য মোবাইলে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা আলোর গতিতে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে মাটির ভেতর দিয়ে ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক ওয়েভটি আসতে তুলনামূলক বেশি সময় নেয়। গতির এই পার্থক্যের কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল দূরে হলে আমরা প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট, আর কাছে হলে অন্তত ৩০ সেকেন্ড সময় হাতে পেতে পারি। জাপান ও আমেরিকার মতো দেশগুলো এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষকে আগেভাগেই সতর্ক করছে।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বা ঝুঁকি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই যে আতঙ্ক ও বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছড়ানো হয়, সেগুলো নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
জিল্লুর রহমান: বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা হচ্ছে তা মূলত প্যানিক বা আতঙ্ক ছড়ানো। দিন-তারিখ দিয়ে (যেমন— আগামীকাল বা ২ দিন পর বা এক সপ্তাহের মধ্যে) ভূমিকম্পের যে পূর্বাভাসের কথা বলা হয়, এগুলোর সবই সম্পূর্ণ ভুয়া। কারণ এ ধরনের পূর্বাভাস দেওয়ার মতো যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। ফলে সোজা কথায় বললে, সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়াচ্ছে। আমার পরামর্শ— এসব গুজবে কান দেওয়া যাবে না। যখনই এ ধরনের কথা শুনবেন, মনে রাখতে হবে এগুলো গুজব। এ বিষয়ে একমাত্র ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতামতই গ্রহণ করতে হবে।
আমাদের বিশেষজ্ঞদেরও কথা বলার ধরনে সতর্ক হওয়া উচিত। আতঙ্ক না ছড়িয়ে বিষয়গুলো আরেকটু গুছিয়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কিছুটা দায় গণমাধ্যমকেও নিতে হবে। আপনারা অনেক সময় একটু বাড়িয়ে বলেন। অনেক ‘বড়’ পত্রিকাতেও দেখেছি হেডিং দেওয়া হয় ‘বড় ধরনের ভূমিকম্পে দেশ প্রকম্পিত হবে’। সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ানোর জন্য এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করা একদমই ঠিক না।
আমার বার্তা— সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হলো ‘আতঙ্ক’। ভূমিকম্প হোক বা অন্য দুর্যোগ, আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া যাবে না। ভূমিকম্প সাধারণত সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এ সময়ে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করলে বাঁচার চেয়ে হতাহত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই ভূমিকম্প শুরু হলে শান্ত থেকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে।

রাজনীতি ডটকম: আমরা শুনছি মাটির নিচে প্রচুর শক্তি জমা হয়ে আছে। এই জমা হওয়া শক্তি রিলিজ হলে আমরা কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি?
জিল্লুর রহমান: প্রথমেই আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান বুঝতে হবে। বাংলাদেশের ‘প্লেট বাউন্ডারি’ বা সীমানা মূলত দেশের বাইরে। পূর্বে মিয়ানমার, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ বা আসাম। সাধারণত এই প্লেট বাউন্ডারিগুলোতেই ৮ থেকে ৯ মাত্রার বড় ভূমিকম্পগুলো হয়। আর দেশের ভেতরে যে ‘ফল্ট’গুলো, সেগুলোতে সাধারণত ৭ থেকে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বস্তির বিষয়, প্লেট বাউন্ডারি ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় (ফল্ট লাইনে) একবার বড় ভূমিকম্প হলে সেই একই জায়গায় পুনরায় শক্তি সঞ্চয় হতে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বছর সময় লাগে।
প্রশ্ন হলো— ৮ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটানোর মতো যে শক্তি জমা আছে, সেটা কি একবারে বের হবে? ৮ বা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে হলে মাটির নিচের ফল্ট লাইনে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একসঙ্গে ফাটল বা ‘ডিসপ্লেসমেন্ট’ হতে হবে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি কি আছে যা একসাথে ৫০০ কিলোমিটার ভেঙে ফেলবে? এটা নিশ্চিত বলা যায় না। এমনও হতে পারে, ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বা ১০০ কিলোমিটার এলাকা ভেঙে ৭ ম্যাগনিচিউডের ভূমিকম্প হয়ে শক্তিটা ধাপে ধাপে বের হলো।
রাজনীতি ডটকম: বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প কোনগুলো?
জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশের ভেতরে বা একদম কাছাকাছি ৭ মাত্রার ওপরে অনেক ভূমিকম্প হয়েছে। তবে গত ১০০ বছরের মধ্যে দেশের ভেতরে বড় কিছু হয়নি। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কয়েকটি বড় ভূমিকম্পের তথ্য পাই। এর মধ্যে ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গলে যে ভূমিকম্প হয়েছিল সেটি ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ছিল বলা হয়। ১৮৮৫ সালে মানিকগঞ্জে প্রায় ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে আসামের শিলং এলাকায় হয়েছিল ৮ মাত্রার চেয়েও বড় ভূমিকম্প, যেটি গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমাদের দেশে ও আশপাশে অনেক বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও হতে পারে।
রাজনীতি ডটকম: গত শুক্রবারের (২১ নভেম্বর) ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর আমরা বেশ কয়েকটি ‘আফটারশক’ দেখেছি। এটি কি বড় কোনো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস?
জিল্লুর রহমান: ভূমিকম্প একটি চলমান প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। টেকটোনিক প্লেটগুলো প্রতিনিয়ত নড়াচড়া করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—একটি লাঠিকে দুই পাশ থেকে বাঁকাতে থাকলে সেটি প্রথমে একটু বাঁকবে। এটাকে আমরা বলি ‘স্ট্রেইন এনার্জি’। এরপর আরও বাঁকানো হলে চাপ লাঠিটির সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এবং একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে ‘মট’ করে ভেঙে যাবে। একইভাবে মাটির নিচে যখন ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কোনো ফাটল রেখা ভেঙে যায়, তখন সেখানে বিপুল পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয়। ফাটলটি অনেক দীর্ঘ হলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে (২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় যেমন হয়েছিল), আর ফাটলটি ছোট হলে ছোট বা মাঝারি ভূমিকম্প হবে।
রাজনীতি ডটকম: ছোট ছোট ভূমিকম্প হলে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমে যায়— এমন ধারণার কথাও বলে থাকেন অনেকে। এটি কি সত্য?
জিল্লুর রহমান: বিজ্ঞান ও প্রকৃতিতে এ নিয়ে দুটি মতই সত্য। যদি দেখা যায় একটি লম্বা লাইন বা ফল্ট বরাবর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘন ঘন ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে, তবে আমরা আশঙ্কা করতে পারি যে সামনে একটি বড় ভূমিকম্প হতে পারে। আবার এটাও সত্য, ছোট ছোট ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটির নিচের জমে থাকা শক্তিটা অবমুক্ত হতে থাকলে বড় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা কমে যাচ্ছে। কাজেই কোনো একটি মতকে এককভাবে সঠিক বা ভুল বলা যাবে না।
রাজনীতি ডটকম: নরসিংদীতে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত করল গত শুক্রবার। সেখানে কি আবার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে?
জিল্লুর রহমান: ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের অর্থ সেখানে হয়তো ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফাটল ভেঙে গেছে। এর ফলে সেখানে জমে থাকা শক্তিটা অবমুক্ত হয়েছে। এখন এ রকম পরিস্থিতি আবার কবে হবে, তা জানতে হলে আমাদের সেই জায়গার ইতিহাস বা ‘পেলিওসাইসমিক স্টাডি’ করতে হবে। যদি দেখা যায় প্রতি ২০০ বছর পরপর ওখানে ভূমিকম্প হয়, তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে আগামী ২০০ বছরের আগে এখানে বড় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আগামীকাল বা ১০ ঘণ্টা পর ভূমিকম্প হবে— এমন প্রেডিকশন করার মতো প্রযুক্তি এখনো পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।
রাজনীতি ডটকম: পুরান ঢাকার প্রায় ২২০০ ভবনকে ‘হেরিটেজ’ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ মানুষ এখনো সেখানে বসবাস করছে। এই ভবনগুলো নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?
জিল্লুর রহমান: সারা পৃথিবীতেই হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী ভবন সংরক্ষণ করা হয়। যেমন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল। এটি আমরা ভেঙে ফেলতে পারি না। সমাধান হলো ‘রেট্রোফিটিং’ বা ভবনকে শক্তিশালী করা। আমাদের বিল্ডিং কোডে নির্দিষ্ট কিছু ‘প্রভিশন’ আছে, যা ব্যবহার করে ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ভবনটি ধসে পড়বে না— এমনভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব। হেরিটেজ ভবনের ক্ষেত্রে নতুন কনস্ট্রাকশনের চেয়ে বেশি টাকা লাগলেও ইতিহাস রক্ষার স্বার্থে রেট্রোফিটিং করতে হবে। আর সাধারণ পুরোনো ভবনের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে নতুন করে বানানোর খরচের ২০ শতাংশ বা ৩০ শতাংশ খরচ করলেই বর্তমান ভবনটিকে ‘ভূমিকম্প সহনশীল’ করা সম্ভব, তবে সেটাই করা উচিত।
রাজনীতি ডটকম: আমাদের ঢাকার অবকাঠামো ও মাটির অবস্থা বিবেচনায় রিখটার স্কেলে ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটা কেমন হতে পারে?
জিল্লুর রহমান: ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মূলত নির্ভর করে এর উৎস বা ‘সোর্সে’র দূরত্বের ওপর। উৎসের কাছাকাছি এলাকায় ক্ষতি সবসময় বেশি হয়। তবে ভয়ের জায়গা হলো আমাদের ভবনগুলোর অবস্থা। আমাদের অনেক ভবনই প্রকৌশলের নিয়ম-কানুন না মেনে সাধারণ রাজমিস্ত্রি দিয়ে ইচ্ছামতো তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় ভবনগুলোতে ‘সিসমিক লোড’ তৈরি হয়, যা যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি না করা ভবনগুলো সহ্য করতে পারবে না।
আমরা উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের স্থাপনাগুলোর মানও খুব একটা উন্নত নয়। আমাদের জন্য হাইতির উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। হাইতিতে একবার ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল এবং ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমাদের এখানে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে হাইতির মতোই বা তার কাছাকাছি বিপর্যয় ঘটতে পারে। গত ১০০ বছরে এখানে বড় ভূমিকম্প হয়নি। তাই এটা আমাদের জন্য একটা প্রস্তুতির সময়।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য সরকারের কী কী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়া উচিত?
জিল্লুর রহমান: আমাদের পরিকল্পনাগুলোকে সময়ের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করে এগোতে হবে—
রাজনীতি ডটকম: দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি বা করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কী পরামর্শ দেবেন?
জিল্লুর রহমান: দুর্যোগের আগে আমাদের দুটি কৌশলে কাজ করতে হবে— প্রস্তুতি ও প্রশমন। প্রস্তুতি মানে হলো ইমার্জেন্সি রেসপন্স বা জরুরি উদ্ধারকাজে প্রস্তুত থাকা। আমাদের সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে, উদ্ধারের যন্ত্রপাতি মজুত রাখতে হবে। আর মানুষকে সচেতন করতে হবে। যেহেতু আমরা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে আছি, তাই এই জ্ঞান থাকাটা জরুরি। ভূমিকম্প কাল হবে নাকি পরশু, তা আমরা জানি না। তাই বলে সব ভবন একসঙ্গে ভেঙে ফেলাও সমাধান নয়। আমাদের ধাপে ধাপে ভবনগুলো নিরাপদ করতে হবে।
রাজনীতি ডটকম: অনেকে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কায় রাতে ঘুমাচ্ছেন না। এই ‘বিগ ওয়ান’ বা বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি আসলে কতটা আসন্ন?
জিল্লুর রহমান: আতঙ্কিত হয়ে জীবন থামিয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। আমরা কেউ জানি না বড় ভূমিকম্প আজ হবে, ১০ বছর পর হবে, নাকি ৫০ বছর পর হবে। অনিশ্চিত একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে খাওয়া-ঘুম বাদ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। একটি ভুল ধারণা হলো— অনেকে বলেন ৮ বা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি জমা আছে। শক্তি জমা আছে সত্য, কিন্তু সেটি একবারে বের না হয়ে ছোট ছোট ভূমিকম্পের মাধ্যমেও বের হয়ে যেতে পারে।
রাজনীতি ডটকম: সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বা ট্রমা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনার পরামর্শ কী?
জিল্লুর রহমান: প্রথমেই বুঝতে হবে, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ একা নেই। জাপান, চিলি বা ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের চেয়ে ঝুঁকি অনেক বেশি। তারা কি ভূমিকম্পের ভয়ে জীবন থামিয়ে দিয়েছে? দেয়নি। আমাদের সমস্যা হলো, এমন বড় ঝাঁকুনি আমাদের জন্য অনেকটা ‘প্রথম অভিজ্ঞতা’র মতো, তাই আমরা বেশি ভয় পাচ্ছি।
আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের আধুনিক বিল্ডিংগুলো যদি সঠিক নকশা মেনে তৈরি করা হয়, তবে সেগুলো ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনায়াসেই সহ্য করতে পারবে। যেহেতু আমরা শহর ছেড়ে চলে যেতে পারব না, তাই আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় বিল্ডিং কোড ও সেফটি নিয়মগুলো মেনে চলাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

৩১ ঘণ্টার ব্যবধানে চার চারটি ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ। এক সপ্তাহ পর ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও দুটি ভূমিকম্প হয়েছে কক্সবাজার ও ঢাকায়। এর মধ্যে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার প্রথম ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে দেশ জুড়ে, তাতে ঢাকা-নরসিংদী-নারায়ণগঞ্জে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০ জন। একের পর এক ভূমিকম্প আতঙ্ক ছড়িয়েছে সারা দেশের মানুষের মধ্যে। ছড়িয়ে পড়ছে ভূমিকম্প নিয়ে নানা তথ্য-অপতথ্য-অর্ধসত্য তথ্য। তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েই চলেছে।
ভূমিকম্প নিয়ে নানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে রাজনীতি ডটকম কথা বলেছে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ড. মো. জিল্লুর রহমানের সঙ্গে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন, ডিজ্যাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া (ইউবিসি) থেকে জিওটেকনিক্যাল আর্থকোয়েক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছেন তিনি, এর আগে নেদারল্যান্ডস থেকে জিওলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে করেছেন এমএসসি।
গত ৩০ বছর ধরে ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণায় নিয়োজিত অধ্যাপক জিল্লুর রহমান রাজনীতি ডটকমের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপচারিতায় তুলে ধরেছেন ভূমিকম্পের কারণ ও ঝুঁকির বিভিন্ন দিক। বলেছেন ভূমিকম্প প্রসঙ্গে কীভাবে সচেতনত থাকা যায়, ভূমিকম্প হলে করণীয়ই বা কী। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রাজনীতি ডটকমের স্টাফ রিপোর্টার নাজমুল ইসলাম হৃদয়, ভিডিও ধারণ করেছেন মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রবিউল ইসলাম, ভিডিও সম্পাদনা করেছেন আরেক মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার রায়হান হক।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্প কেন হয়, খুব সহজ করে যদি বুঝিয়ে বলতেন...
জিল্লুর রহমান: সহজ কথায় ভূমিকম্প হলো একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, যা পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকেই হয়ে আসছে। এর মূল কারণ হলো ভূ-অভ্যন্তরে থাকা বিশাল সব ফাটল, যেগুলোকে ভূতাত্ত্বিক পরিভাষায় বলা হয় ‘ফল্ট’। ধরুন, ভূ-অভ্যন্তরে একটি লম্বা ফাটল রেখা বা লাইন আছে। কোনো কারণে যদি সেই লাইন বরাবর মাটি ভেঙে যায় বা ‘ডিসপ্লেসমেন্ট’ হয়, তখন সেখানে প্রচুর শক্তি বা এনার্জি রিলিজ হয়। সেই এনার্জি ঢেউ বা ‘ওয়েভ’ আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ যখন আপনার পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দেয় এবং আপনি সেটা অনুভব করেন, তখন আমরা বলি ভূমিকম্প হয়েছে।
রাজনীতি ডটকম: গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ভূমিকম্প হয়েছে বাংলাদেশে। এর পেছনে কি নির্দিষ্ট কোনো ভূতাত্ত্বিক কারণ আছে?
জিল্লুর রহমান: অবশ্যই। ভূমিকম্পের মূল কারণই ভূতাত্ত্বিক। পৃথিবীর ওপরের শক্ত স্তর বা ভূ-ত্বকে যখন দুটি বিশাল মাটির ব্লক একটি আরেকটির সাপেক্ষে নড়ে যায় বা সরে যায়, তখনই কম্পন সৃষ্টি হয়। তবে শুধু প্রাকৃতিক কারণে নয়, বর্তমানে মানুষের তৈরি কারণেও ছোটখাটো ভূমিকম্প হতে পারে। যেমন— মাটির নিচে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা করলে ভূমিকম্প হয়। এমনকি আপনার পাশ দিয়ে যদি একটি ভারী ট্রাক চলে যায়, তখন যে কম্পন হয়, সেটাও এক ধরনের অতি ক্ষুদ্র ভূমিকম্প, যাকে আমরা বলি ‘মাইক্রো ট্রেমর’। তবে বড় আকারের ফাটল বা মুভমেন্ট হলে সেটাকে আমরা মূল ভূমিকম্প হিসেবে গণ্য করি।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের অগ্রিম পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব কি?
জিল্লুর রহমান: ঠিক ‘পূর্বাভাস’ না হলেও বর্তমানে প্রযুক্তির সাহায্যে ভূমিকম্পের ‘আর্লি ওয়ার্নিং’ বা ‘তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা’ দেওয়া সম্ভব। ভূমিকম্পের সময় সাধারণত একাধিক ‘ওয়েভ’ বা ঢেউ তৈরি হয়। অনেকেই অভিজ্ঞতায় বলেন, প্রথমে হালকা একটু কাঁপুনি অনুভূত হলো (ছোট ওয়েভ), তার কিছুক্ষণ পরেই শক্তিশালী ঝাঁকুনি (বড় ওয়েভ) আঘাত হানল। মূলত এই পরবর্তী ওয়েভগুলোই প্রলয়ংকরী বা ধ্বংসাত্মক হয়, প্রথম ওয়েভে সাধারণত তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না।
ফলে যখনই ভূমিকম্পের এই প্রথম বা প্রাথমিক ওয়েভটি তৈরি হয়, তখনই যদি সেন্সরের মাধ্যমে সেই তথ্য মোবাইলে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে তা আলোর গতিতে মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে মাটির ভেতর দিয়ে ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক ওয়েভটি আসতে তুলনামূলক বেশি সময় নেয়। গতির এই পার্থক্যের কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল দূরে হলে আমরা প্রায় এক থেকে দেড় মিনিট, আর কাছে হলে অন্তত ৩০ সেকেন্ড সময় হাতে পেতে পারি। জাপান ও আমেরিকার মতো দেশগুলো এখন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষকে আগেভাগেই সতর্ক করছে।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বা ঝুঁকি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই যে আতঙ্ক ও বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছড়ানো হয়, সেগুলো নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?
জিল্লুর রহমান: বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় যা হচ্ছে তা মূলত প্যানিক বা আতঙ্ক ছড়ানো। দিন-তারিখ দিয়ে (যেমন— আগামীকাল বা ২ দিন পর বা এক সপ্তাহের মধ্যে) ভূমিকম্পের যে পূর্বাভাসের কথা বলা হয়, এগুলোর সবই সম্পূর্ণ ভুয়া। কারণ এ ধরনের পূর্বাভাস দেওয়ার মতো যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। ফলে সোজা কথায় বললে, সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়াচ্ছে। আমার পরামর্শ— এসব গুজবে কান দেওয়া যাবে না। যখনই এ ধরনের কথা শুনবেন, মনে রাখতে হবে এগুলো গুজব। এ বিষয়ে একমাত্র ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের মতামতই গ্রহণ করতে হবে।
আমাদের বিশেষজ্ঞদেরও কথা বলার ধরনে সতর্ক হওয়া উচিত। আতঙ্ক না ছড়িয়ে বিষয়গুলো আরেকটু গুছিয়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। কিছুটা দায় গণমাধ্যমকেও নিতে হবে। আপনারা অনেক সময় একটু বাড়িয়ে বলেন। অনেক ‘বড়’ পত্রিকাতেও দেখেছি হেডিং দেওয়া হয় ‘বড় ধরনের ভূমিকম্পে দেশ প্রকম্পিত হবে’। সংবাদপত্রের কাটতি বাড়ানোর জন্য এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করা একদমই ঠিক না।
আমার বার্তা— সবচেয়ে বড় দুর্যোগ হলো ‘আতঙ্ক’। ভূমিকম্প হোক বা অন্য দুর্যোগ, আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া যাবে না। ভূমিকম্প সাধারণত সর্বোচ্চ ৩০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এ সময়ে আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করলে বাঁচার চেয়ে হতাহত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তাই ভূমিকম্প শুরু হলে শান্ত থেকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে হবে।

রাজনীতি ডটকম: আমরা শুনছি মাটির নিচে প্রচুর শক্তি জমা হয়ে আছে। এই জমা হওয়া শক্তি রিলিজ হলে আমরা কী ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি?
জিল্লুর রহমান: প্রথমেই আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান বুঝতে হবে। বাংলাদেশের ‘প্লেট বাউন্ডারি’ বা সীমানা মূলত দেশের বাইরে। পূর্বে মিয়ানমার, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ বা আসাম। সাধারণত এই প্লেট বাউন্ডারিগুলোতেই ৮ থেকে ৯ মাত্রার বড় ভূমিকম্পগুলো হয়। আর দেশের ভেতরে যে ‘ফল্ট’গুলো, সেগুলোতে সাধারণত ৭ থেকে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বস্তির বিষয়, প্লেট বাউন্ডারি ছাড়া অন্য কোনো জায়গায় (ফল্ট লাইনে) একবার বড় ভূমিকম্প হলে সেই একই জায়গায় পুনরায় শক্তি সঞ্চয় হতে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বছর সময় লাগে।
প্রশ্ন হলো— ৮ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প ঘটানোর মতো যে শক্তি জমা আছে, সেটা কি একবারে বের হবে? ৮ বা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে হলে মাটির নিচের ফল্ট লাইনে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একসঙ্গে ফাটল বা ‘ডিসপ্লেসমেন্ট’ হতে হবে। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি কি আছে যা একসাথে ৫০০ কিলোমিটার ভেঙে ফেলবে? এটা নিশ্চিত বলা যায় না। এমনও হতে পারে, ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বা ১০০ কিলোমিটার এলাকা ভেঙে ৭ ম্যাগনিচিউডের ভূমিকম্প হয়ে শক্তিটা ধাপে ধাপে বের হলো।
রাজনীতি ডটকম: বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্প কোনগুলো?
জিল্লুর রহমান: বাংলাদেশের ভেতরে বা একদম কাছাকাছি ৭ মাত্রার ওপরে অনেক ভূমিকম্প হয়েছে। তবে গত ১০০ বছরের মধ্যে দেশের ভেতরে বড় কিছু হয়নি। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা কয়েকটি বড় ভূমিকম্পের তথ্য পাই। এর মধ্যে ১৯১৮ সালে শ্রীমঙ্গলে যে ভূমিকম্প হয়েছিল সেটি ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ছিল বলা হয়। ১৮৮৫ সালে মানিকগঞ্জে প্রায় ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে আসামের শিলং এলাকায় হয়েছিল ৮ মাত্রার চেয়েও বড় ভূমিকম্প, যেটি গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক নামে পরিচিত। অর্থাৎ আমাদের দেশে ও আশপাশে অনেক বড় বড় ভূমিকম্প হয়েছে, যা ভবিষ্যতেও হতে পারে।
রাজনীতি ডটকম: গত শুক্রবারের (২১ নভেম্বর) ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের পর আমরা বেশ কয়েকটি ‘আফটারশক’ দেখেছি। এটি কি বড় কোনো ভূমিকম্পের পূর্বাভাস?
জিল্লুর রহমান: ভূমিকম্প একটি চলমান প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। টেকটোনিক প্লেটগুলো প্রতিনিয়ত নড়াচড়া করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—একটি লাঠিকে দুই পাশ থেকে বাঁকাতে থাকলে সেটি প্রথমে একটু বাঁকবে। এটাকে আমরা বলি ‘স্ট্রেইন এনার্জি’। এরপর আরও বাঁকানো হলে চাপ লাঠিটির সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যাবে এবং একটা পর্যায়ে হঠাৎ করে ‘মট’ করে ভেঙে যাবে। একইভাবে মাটির নিচে যখন ৪০০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কোনো ফাটল রেখা ভেঙে যায়, তখন সেখানে বিপুল পরিমাণ শক্তি অবমুক্ত হয়। ফাটলটি অনেক দীর্ঘ হলে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে (২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় যেমন হয়েছিল), আর ফাটলটি ছোট হলে ছোট বা মাঝারি ভূমিকম্প হবে।
রাজনীতি ডটকম: ছোট ছোট ভূমিকম্প হলে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমে যায়— এমন ধারণার কথাও বলে থাকেন অনেকে। এটি কি সত্য?
জিল্লুর রহমান: বিজ্ঞান ও প্রকৃতিতে এ নিয়ে দুটি মতই সত্য। যদি দেখা যায় একটি লম্বা লাইন বা ফল্ট বরাবর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘন ঘন ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে, তবে আমরা আশঙ্কা করতে পারি যে সামনে একটি বড় ভূমিকম্প হতে পারে। আবার এটাও সত্য, ছোট ছোট ভূমিকম্পের মাধ্যমে মাটির নিচের জমে থাকা শক্তিটা অবমুক্ত হতে থাকলে বড় ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা কমে যাচ্ছে। কাজেই কোনো একটি মতকে এককভাবে সঠিক বা ভুল বলা যাবে না।
রাজনীতি ডটকম: নরসিংদীতে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত করল গত শুক্রবার। সেখানে কি আবার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে?
জিল্লুর রহমান: ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের অর্থ সেখানে হয়তো ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফাটল ভেঙে গেছে। এর ফলে সেখানে জমে থাকা শক্তিটা অবমুক্ত হয়েছে। এখন এ রকম পরিস্থিতি আবার কবে হবে, তা জানতে হলে আমাদের সেই জায়গার ইতিহাস বা ‘পেলিওসাইসমিক স্টাডি’ করতে হবে। যদি দেখা যায় প্রতি ২০০ বছর পরপর ওখানে ভূমিকম্প হয়, তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে আগামী ২০০ বছরের আগে এখানে বড় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আগামীকাল বা ১০ ঘণ্টা পর ভূমিকম্প হবে— এমন প্রেডিকশন করার মতো প্রযুক্তি এখনো পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।
রাজনীতি ডটকম: পুরান ঢাকার প্রায় ২২০০ ভবনকে ‘হেরিটেজ’ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ মানুষ এখনো সেখানে বসবাস করছে। এই ভবনগুলো নিয়ে আমাদের কী করা উচিত?
জিল্লুর রহমান: সারা পৃথিবীতেই হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী ভবন সংরক্ষণ করা হয়। যেমন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল। এটি আমরা ভেঙে ফেলতে পারি না। সমাধান হলো ‘রেট্রোফিটিং’ বা ভবনকে শক্তিশালী করা। আমাদের বিল্ডিং কোডে নির্দিষ্ট কিছু ‘প্রভিশন’ আছে, যা ব্যবহার করে ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলেও ভবনটি ধসে পড়বে না— এমনভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব। হেরিটেজ ভবনের ক্ষেত্রে নতুন কনস্ট্রাকশনের চেয়ে বেশি টাকা লাগলেও ইতিহাস রক্ষার স্বার্থে রেট্রোফিটিং করতে হবে। আর সাধারণ পুরোনো ভবনের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে নতুন করে বানানোর খরচের ২০ শতাংশ বা ৩০ শতাংশ খরচ করলেই বর্তমান ভবনটিকে ‘ভূমিকম্প সহনশীল’ করা সম্ভব, তবে সেটাই করা উচিত।
রাজনীতি ডটকম: আমাদের ঢাকার অবকাঠামো ও মাটির অবস্থা বিবেচনায় রিখটার স্কেলে ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প হলে ক্ষয়ক্ষতির চিত্রটা কেমন হতে পারে?
জিল্লুর রহমান: ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মূলত নির্ভর করে এর উৎস বা ‘সোর্সে’র দূরত্বের ওপর। উৎসের কাছাকাছি এলাকায় ক্ষতি সবসময় বেশি হয়। তবে ভয়ের জায়গা হলো আমাদের ভবনগুলোর অবস্থা। আমাদের অনেক ভবনই প্রকৌশলের নিয়ম-কানুন না মেনে সাধারণ রাজমিস্ত্রি দিয়ে ইচ্ছামতো তৈরি করা হয়েছে। ভূমিকম্পের সময় ভবনগুলোতে ‘সিসমিক লোড’ তৈরি হয়, যা যথাযথ নিয়ম মেনে তৈরি না করা ভবনগুলো সহ্য করতে পারবে না।
আমরা উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের স্থাপনাগুলোর মানও খুব একটা উন্নত নয়। আমাদের জন্য হাইতির উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। হাইতিতে একবার ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল এবং ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমাদের এখানে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলে হাইতির মতোই বা তার কাছাকাছি বিপর্যয় ঘটতে পারে। গত ১০০ বছরে এখানে বড় ভূমিকম্প হয়নি। তাই এটা আমাদের জন্য একটা প্রস্তুতির সময়।
রাজনীতি ডটকম: ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য সরকারের কী কী পরিকল্পনা ও উদ্যোগ নেওয়া উচিত?
জিল্লুর রহমান: আমাদের পরিকল্পনাগুলোকে সময়ের ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করে এগোতে হবে—
রাজনীতি ডটকম: দুর্যোগ মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি বা করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কী পরামর্শ দেবেন?
জিল্লুর রহমান: দুর্যোগের আগে আমাদের দুটি কৌশলে কাজ করতে হবে— প্রস্তুতি ও প্রশমন। প্রস্তুতি মানে হলো ইমার্জেন্সি রেসপন্স বা জরুরি উদ্ধারকাজে প্রস্তুত থাকা। আমাদের সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে, উদ্ধারের যন্ত্রপাতি মজুত রাখতে হবে। আর মানুষকে সচেতন করতে হবে। যেহেতু আমরা ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে আছি, তাই এই জ্ঞান থাকাটা জরুরি। ভূমিকম্প কাল হবে নাকি পরশু, তা আমরা জানি না। তাই বলে সব ভবন একসঙ্গে ভেঙে ফেলাও সমাধান নয়। আমাদের ধাপে ধাপে ভবনগুলো নিরাপদ করতে হবে।
রাজনীতি ডটকম: অনেকে বড় ভূমিকম্পের আশঙ্কায় রাতে ঘুমাচ্ছেন না। এই ‘বিগ ওয়ান’ বা বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকি আসলে কতটা আসন্ন?
জিল্লুর রহমান: আতঙ্কিত হয়ে জীবন থামিয়ে দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। আমরা কেউ জানি না বড় ভূমিকম্প আজ হবে, ১০ বছর পর হবে, নাকি ৫০ বছর পর হবে। অনিশ্চিত একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে খাওয়া-ঘুম বাদ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। একটি ভুল ধারণা হলো— অনেকে বলেন ৮ বা ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি জমা আছে। শক্তি জমা আছে সত্য, কিন্তু সেটি একবারে বের না হয়ে ছোট ছোট ভূমিকম্পের মাধ্যমেও বের হয়ে যেতে পারে।
রাজনীতি ডটকম: সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক বা ট্রমা বিরাজ করছে। এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আপনার পরামর্শ কী?
জিল্লুর রহমান: প্রথমেই বুঝতে হবে, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ একা নেই। জাপান, চিলি বা ইন্দোনেশিয়ায় আমাদের চেয়ে ঝুঁকি অনেক বেশি। তারা কি ভূমিকম্পের ভয়ে জীবন থামিয়ে দিয়েছে? দেয়নি। আমাদের সমস্যা হলো, এমন বড় ঝাঁকুনি আমাদের জন্য অনেকটা ‘প্রথম অভিজ্ঞতা’র মতো, তাই আমরা বেশি ভয় পাচ্ছি।
আতঙ্কিত না হয়ে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের আধুনিক বিল্ডিংগুলো যদি সঠিক নকশা মেনে তৈরি করা হয়, তবে সেগুলো ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনায়াসেই সহ্য করতে পারবে। যেহেতু আমরা শহর ছেড়ে চলে যেতে পারব না, তাই আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে ঠান্ডা মাথায় বিল্ডিং কোড ও সেফটি নিয়মগুলো মেনে চলাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

এভাবেই লাখ লাখ ভোটারকে একত্রিত করতে সক্ষম একটি নির্বাচন দলীয় কর্মী বাহিনীর একত্রিতকরণের একটি অপারেশনে পরিণত হয়। ফলে শুধু ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনাতেই কয়েক লাখ সংগঠিত কর্মী মাঠে নামাতে হয়। এই মানুষগুলো স্বেচ্ছাসেবী নন, তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হয় অর্থ, প্রভাব ও সুবিধার আশ্বাস দিয়ে।
৬ দিন আগে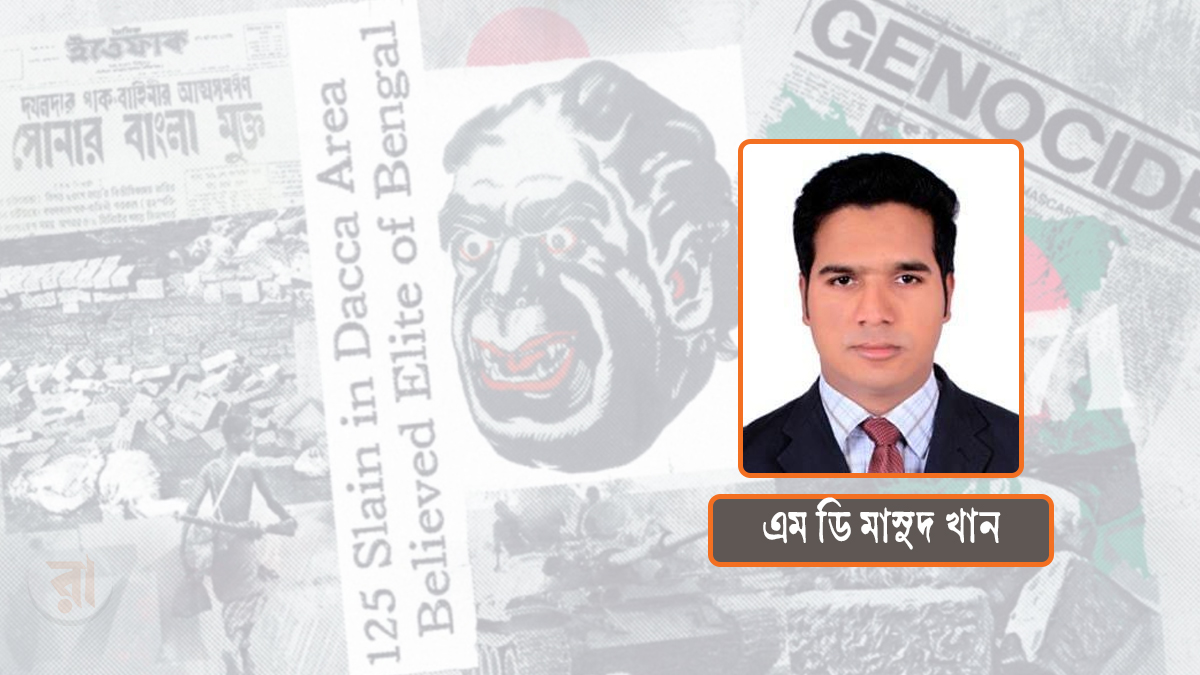
বিপরীতভাবে, ইতিহাস যখন বিকৃত হয়— ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অবহেলার কারণে— তখন একটি জাতি ধীরে ধীরে তার শেকড় হারাতে শুরু করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই একটি গভীর ও বহুমাত্রিক সংকট হিসেবে বিদ্যমান।
৭ দিন আগে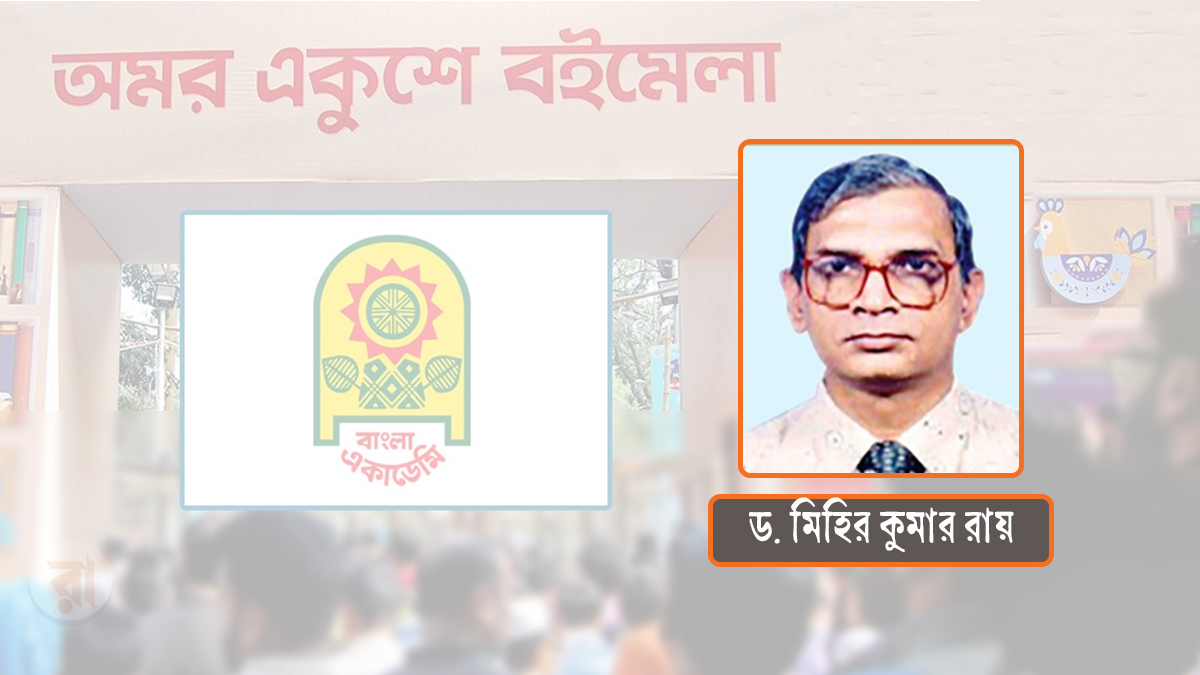
অর্থাৎ এ পর্যন্ত তিনবার ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে; এবারেরটি হবে চতুর্থ। তবে নির্বাচনের কারণে বইমেলা কখনো বন্ধ থাকেনি। ১৯৭৯ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলেছে। ১৯৯১ সালেও মেলা চলেছে পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে। ১৯৯৬ সালেও একই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৯৭৯ সালের মেলাটি কিছুটা ব্যতিক
৮ দিন আগে
যতদিন শাসনব্যবস্থা মানুষকে রাজকীয় যন্ত্রের বিনিময়যোগ্য যন্ত্রাংশ হিসেবে গণ্য করবে, ততদিন এ দেশ বহু রাজার, শোষিত প্রজার দেশ হয়েই থাকবে— আর নাগরিকরা চিরকালই গলা মিলিয়ে গান গাইতে বাধ্য হবে— আমরা সবাই গাধা…
১০ দিন আগে