
স ম গোলাম কিবরিয়া

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গভীর রাতে ঢাকার মতো পাবনাতেও শুরু হয় অপরেশন সার্চলাইট। রাজশাহী থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য (১৩০ জন) রাত আড়াইটায় পাবনা পৌঁছায়। তারা বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থান নেয়। কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার ছিল ক্যাপ্টেন আসগর, ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রশিদ।
২৭ মার্চ সকাল থেকেই পাবনাবাসী সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধে হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে প্রাণ হারাতে থাকে। খবর পেয়ে রাজশাহী থেকে ১৮ জন সৈন্যসহ ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার মেজর আসলাম পাবনা আসে। দুই দিনের যুদ্ধে মেজর আসলামসহ সবাইকে প্রাণ হারাতে হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেড় শ সৈন্যের হানাদার বাহিনী পাবনাবাসীর দেশীয় অস্ত্র ও সাহসের কাছে পরাজিত হয়। তাদের একজনও রাজশাহীতে ফিরে যেতে পারেনি।
২৯ মার্চ পাবনা হানাদারমুক্ত হয়। এ জেলায় কোনো সেনানিবাস বা ইপিআর ক্যাম্প ছিল না। তাই যুদ্ধে কোনো বাঙালি সেনা বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) অংশ নেয়নি। পাবনার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় যুবসমাজ এই যুদ্ধে অংশ নেয়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে ছাত্রলীগ প্রস্তুতি নিতে থাকে। যুবসমাজকে সংগঠিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ছাত্রলীগ। পাবনা শহরে এ ধরনের চার-পাঁচটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। কেন্দ্রগুলো ২৫ মার্চ পর্যন্ত চালু ছিল।
একই সময়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আমজাদ হোসেনকে (এমএনএ) আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— আব্দুর রব বগা মিয়া (এমপিএ), অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন (এমপিএ), আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান মাহবুবুল হক ফেরু ও গোলাম আলী কাদেরী, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা এবং ছাত্রলীগ পাবনা জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সাত্তার লালু। ২৫ মার্চের পর পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খান ও এসপি চৌধুরী আব্দুল গফফারকে কমিটির সদস্য করা হয়।
পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন এমএনএ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বগা মিয়া এমপিএ, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা, রনেশ মৈত্র, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম আলী কাদেরী, দেওয়ান মাহবুবুল হক ফেরু, ওয়াজি উদ্দিন খান, নবাব আলী মোল্লা, পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তার লালু, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বকুল, জহুরুল ইসলাম বিশুসহ অনেকেই যুদ্ধে অসীম সাহস দেখান। ছাত্র ইউনিয়নের রবিউল ইসলাম রবি ও শিরিন বানু মিতিলসহ তাদের নেতাকর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।
যুদ্ধে ছাত্রলীগের রফিকুল ইসলাম বকুল, ইকবাল হোসেন, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, বেবী ইসলাম, মো. ইসমত, ফজলুল হক মন্টু, মোখলেছুর রহমান মুকুল, সাঈদ আকতার ডিডু, জহুরুল ইসলাম বিশু প্রমুখ ছাত্রনেতার ভুমিকা ছিল অনন্য। এই প্রতিরোধযুদ্ধে পাবনায় ডিসি ও এসপি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। অনেক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীও যুদ্ধে অংশ নেন।
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বিজয় ও জনযুদ্ধের ক্ষেত্রে পাবনা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিজয়ের পর পাবনাকে হানাদার মুক্ত রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো মূল্যে পাবনাকে শত্রুমুক্ত রাখতে যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হানাদার বাহিনীর পুনর্প্রবেশ ঠেকাতে তাই নগরবাড়ি ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার ছিলো নগরবাড়ি। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গে যেতে শুধু এ ঘাটেই গাড়িসহ পারাপারের সুবিধা ছিল। ফুলছড়িঘাট বা ভূঞাপুরে গাড়ি পারাপারের সুযোগ ছিল না। তাই নগরবাড়ির গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকেই নাকি নগরবাড়ী-দিনাজপুর সড়ক নির্মম করা হয়েছিল। উত্তরাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধ করতে হলে নগরবাড়ী ঘাটের দখল নেওয়া পাকিস্তানিদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ভৌগোলিক দিক থেকে পাবনা ছিল হানাদার বাহিনীর জন্য নিরাপদ জেলা। পদ্মা ও যমুনা পরিবেষ্টিত এই জেলার ভারতের সঙ্গে কোনো সীমান্ত নেই। উত্তরে রংপুর সেনানিবাস, উত্তর-পশ্চিমে রাজশাহী সেনানিবাস। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নিয়ন্ত্রণে থাকলে কুষ্টিয়া থেকেও যেকোনো হামলা প্রতিহত করা সম্ভব। এ ছাড়া ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ ও রংপুর সেনানিবাসে রসদ পাঠাতেও নগরবাড়ি ঘাট গুরুত্বপুর্ণ। অন্যথায় পুরো উত্তরবঙ্গ মুক্তাঞ্চলে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।
২৯ মার্চ শত্রুমুক্ত করার পর পাবনার প্রতিরোধযোদ্ধারা প্রস্তুতি জোরদার করে। পুনরায় আক্রমণ প্রতিহত করতে পুলিশ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ‘সম্মিলিত বাহিনী’ গঠন করা হয়। সঙ্গত কারণেই সম্মিলিত বাহিনীতে বাঙালি সৈনিক বা ইপিআর জোয়ান ছিল না। ৩১ মার্চ এক সভায় নগরবাড়ি প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। পুলিশ ও পরাজিত হানাদার বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রগুলো তখন জনযোদ্ধাদের হাতে। সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশি। শহরে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করায় যোদ্ধাদের মনোবল পাহাড়সম।
পাবনা জেলা ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ যোদ্ধা ২ এপ্রিল নগরবাড়িতে অবস্থান নেয়। শহরের বিজয়ী যোদ্ধরাই প্রতিরোধের প্রধান শক্তি। শহরের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে রফিকুল ইসলাম বকুল তখন সবার আস্থাভাজন।
হানাদার বাহিনীর দখল করা আটটি জিপ ও বড় একটি বাস নিয়ে সবাই একযোগে পাবনা থেকে রওয়ানা হয়। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাংকার নির্মাণ করে সামনে বালির বস্তা দেওয়া হয়। যোদ্ধারা ঘাটে অপেক্ষমাণ তিনটি ফেরির চাবি দখলে নেযন। ফলে সেগুলো আর আরিচায় ফেরত যেতে পারে না। আরিচা থেকে নৌকাযোগে পার হয়ে আসা লোকজনের মাধ্যমে যোদ্ধারা ওপারের খবর সংগ্রহ করতে থাকে।
৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় হঠাৎ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যুদ্ধবিমান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। জবাবে যোদ্ধারা বিমান লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুড়ে। সৌভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হয়নি। এই আক্রমণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রতিরোধ অবস্থান সম্পর্কে পাকিস্তানিরা খবর পেয়ে গেছে। যোদ্ধারা মনে করেছে বড় একটি যুদ্ধ তাদের মোকাবিলা করতে হবে।
মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই পাবনায় মাওবাদীদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। মাওবাদীরা এলাকায় নকশাল নামের আতঙ্ক। নকশালদের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ করেই পাবনায় আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে হয়েছে। শুরু থেকেই নকশালরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। প্রসঙ্গত, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় নকশালরা পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল। তারাও রাজাকার-আলবদরদের মতোই মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষকে হত্যা, বাড়িঘর দখল ও লুটপাট করে।
শহরের যোদ্ধারা সবাই নগরবাড়িতে। ফলে শহর অরক্ষিত। এ সুযোগে ৩ এপ্রিল নকশালরা শহরে প্রবেশ করে। তবে বড় কোনো অঘটন না ঘটিয়েই শহর ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা জানে, পুলিশ ও পরাজিত পাকিস্তানিদের আধুনিক অস্ত্র এখন যোদ্ধাদের কাছে। খবর পেয়ে কয়েকজন যোদ্ধা শহরে ফিরে আসে। তারা গাড়ি নিয়ে টহল দিয়ে অস্তিত্ব জানান দেয়। বিষয়টি যোদ্ধাদের জন্য নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এদিকে পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খান শহরে অবস্থান করে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর গতিবিধি জানার চেষ্টা করছেন। কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রফিকুল ইসলাম বকুলকে তা জানিয়ে দেন। নগরবাড়ির কাছেই পাবনার পথে একটি ব্রিজ ছিল। ডিসি ৬ এপ্রিল রফিকুল ইসলাম বকুলকে ব্রিজটি ভেঙে ফেলতে বলেন, যেন পাকিস্তানিরা নদী পার হলেও শহরে প্রবেশের আগেই আবারও বাধার সম্মুখীন হয়।
যোদ্ধাদের কাছে তখন ব্রিজ ভাঙার জন্য কোনো অ্যামুনিশন নেই। তাই কোদাল, শাবল, হাতুড়ি জোগাড় করতে স্থানীয়দের সাহায্য চান তারা। কিন্তু স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একজোট হয়ে ব্রিজ ভাঙার বিরোধিতা করে। অনেক অনুরোধ করার পরও তারা রাজি হয় না। সন্ধ্যায় ডিসি অবস্থান দেখতে নগরবাড়ি যান। ব্রিজ না ভাঙায় তিনি খুব রেগে যান। ডিসিও চেয়ারম্যানকে ব্রিজ ভাঙার কারণ বোঝান ও সহযোগিতা চান। কিন্তু চেয়ারম্যান তার সিদ্ধান্তে অটল।
এ সময় ডিসি তার হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ ফাঁকা গুলি ছোড়েন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যোদ্ধাও গুলি ছোড়েন। ভয়ে লোকজন সরে যায়। চেয়ারম্যানের কলার ধরে টেনে এনে ডিসি দ্রুত ব্রিজ ভাঙার নির্দেশ দেন। এই কৌশল দারুণভাবে কাজ করে। স্থানীয়রাও যোগ দেয়, কিন্তু ব্রিজ ভাঙা সম্ভব হয় না। অগত্যা ব্রিজসংলগ্ন রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়া হয়।
৭ এপ্রিল দুপুরে ফের পাকিস্তানিরা বিমান আক্রমণ চালায়। এ দিনও কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু বারবার বিমান আক্রমণে অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। পুলিশ ও আনসারদের অনেকেই গোপনে অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে পাবনা যুদ্ধের বিজয়ীরা অবস্থানে অনড়। সব মিলিয়ে অটল থাকেন প্রায় ৮০ জন যোদ্ধা।
৮ এপ্রিল কোনো আক্রমণ না হলেও পরদিন ৯ এপ্রিল দুই দফায় বিমান হামলা হয়। এবারের আক্রমণ আগের চেয়ে বেশি জোরালো। দুটি বিমান থেকে মেশিনগানের ব্রাশফায়ার করে। আগের মতোই যোদ্ধারা পালটা গুলি ছোড়েন। প্রতিবার আক্রমণের পরই দেখতে হয়, কেউ হতাহত হলো কি না। সৌভাগ্যের বিষয়, এবারেও সবাই রক্ষা পায়।
এদিকে নৌকায় নদী পার হয়ে আসা লোকজন জানায়, আরিচায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্যাংক, কামান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্রাক, গানবোটসহ বিপুল সৈন্যের সমাবেশ করেছে। যেকোনো সময় তারা এ পারে আক্রমণ করতে পারে।
খবর পেয়ে যোদ্ধারাও প্রস্তুতি নেয়। নিজ নিজ বাংকারে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ খবরে নগরবাড়ি এলাকা জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। আগের কয়দিন স্থানীয়রা যোদ্ধাদের প্রচুর খবর দিত। কিন্তু তারাও তখন কেউ নেই। সারা দিন কাটে ক্ষুধার্ত অবস্থায়। গভীর রাতে কয়েকজন ছাত্র খিচুড়ি নিয়ে হাজির। পরিমাণে কম হলেও সেটুকুই সবাই ভাগাভাগি করে খায়। এভাবে রাত কেটে যায়, কোনো আক্রমণ হয় না।
ভৌগোলিক কারণেই হয়তো পাকিস্তানিরা পাবনায় অপরেশন সার্চলাইট কার্যকর করতে খুব গুরুত্ব দেয়নি। তারা শহরে অবস্থান নিয়ে নির্বিচারে গুলি করে সাধারণ মানুষ হত্যা, আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার, বিভিন্ন স্থাপনা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নির্বিঘ্নে ৩৬ ঘণ্টা পার করে। হানাদার বাহিনী ধারণা করেছিল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এ কারণে ওয়াপদার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন ও চেকপোস্টে অল্প কয়জন সৈন্য মোতায়েন করে। সিদ্দিক সালিক তার ‘উইটনেস টু সারেন্ডার’ বইয়ে পাবনায় এসব স্থাপনায় অল্প সৈন্য মোতায়েনকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন।
দুদিন পর যখন পাবনার সর্বস্তরের জনসাধারণ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন তাদের চরম মূল্য দিতে হয়। এ ঘটনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পুনর্দখলের বিষয়কে হানাদার বাহিনী বাড়তি গুরুত্ব দেয়। তখন যেন নগরবাড়ি দখলের ওপর গোটা উত্তরবঙ্গে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল। মেজর জেনারেল নজর হুসাইন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে পাবনাসহ উত্তরাঞ্চল দখল করতে পাঠানো হয়।
১০ এপ্রিল ভোর হয় অন্যদিনের মতোই। কিন্তু একটু বেলা বাড়তেই চিত্র পালটে যায়। দুটি যুদ্ধবিমান তীব্রবেগে উড়ে আগের মতোই গুলিবর্ষণ শুরু করে। একই সঙ্গে বিকট শব্দে মর্টার শেল পড়তে থাকে বাংকারের অদূরে। শেলের আঘাতে বিশাল গর্ত তৈরি হতে থাকে। মাটি গুঁড়ো হয়ে অনেক ওপরে উঠে যায়। পুরো এলাকা তখন ধুলোয় অন্ধকার। আর্টিলারি গানের গোলায় পুরো এলাকা প্রকম্পিত। সৌভাগ্য, একটি শেলও বাংকারে আঘাত করেনি। একটি শেল আঘাত করলেই একসঙ্গে কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যাবে, যোদ্ধাদের জীবনও যাবে।
নগরবাড়ি ঘটে অনেকগুলো ব্যবসায়িক গুদামঘর ছিলো। গোলার আঘাতে বেশ কয়েকটি গুদামে আগুন ধরে যায়। চতুর্মুখী আক্রমণে যোদ্ধারা দিশেহারা। পুরো এলাকা ধুলোয় আচ্ছন্ন, কিছুই দেখা যায় না। বারবার বিমান থেকে বৃষ্টির মতো গুলোবর্ষণ, নদী দিক থেকে ব্রাশ ফায়ার, মর্টারের আঘাত— এক ভয়ংকর পরিস্থিতি!
যোদ্ধাদের হাতে হালকা অস্ত্র। যুদ্ধের জন্য তেমন প্রশিক্ষণও নেই। অন্যদিকে হানাদার বাহিনী ভারী অস্ত্রের গোলা বর্ষণ করছে। তারা অন্যতম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবেই পরিচিত। এমন অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ তো দূরের কথা, জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়াই কঠিন। শত্রুর অবস্থানও বোঝার উপায় নেই। তবু যোদ্ধারা পালটা গুলি ছুঁড়তে থাকেন অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কোনো ফল মেলে না।
অবস্থান ত্যাগের নির্দেশ পেয়ে ঝুঁকি নিয়েই সবাই দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে যায়। দ্রুত গাড়ি পাবনার দিকে রওনা হয়। তখন বুঝতে পারে, সবাই অক্ষত আছে। কিন্তু পাবনা শত্রুমুক্ত রাখা সম্ভব হয় না— এ কষ্টে সবারই মন খারাপ। এখন তারা কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই বুঝতে পারেন না। সকাল ৯টার দিকে নগরবাড়ি পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায়।
পাবনার পথে আতাইকুলা গিয়ে যোদ্ধারা ইপিআর সৈন্য ভর্তি একটি ট্রাক দেখতে পায়। তাদের থামতে বলা হয়। কথা বলে জানা যায়, তারা নগরবাড়িতে জনযোদ্ধদের সহযোগিতা করতে যাচ্ছে। নগরবাড়ির অবস্থার কথা শুনে তাদের আর যাওয়া হলো না। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, আতাইকুলাতেই অ্যামবুশ করবে। তাহলে শহরে প্রবেশের আগেই হানাদার বাহিনীকে রুখে দেওয়া যাবে।
অ্যামবুশ পেতে পাকিস্তানিদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন যোদ্ধারা। অনেকক্ষণ অবস্থান করেও হানাদার বাহিনীর গতিবিধির খবর পাওয়া গেল না। রাস্তায় গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজনেরও চলাচল নেই। কিছু বুঝতে না পেরে সেখান থেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজশাহী-পাবনা সড়কে টেবুনিয়ায় অ্যামবুশ করতে বলে ইপিআর। তাহলে রাজশাহী থেকে আসা সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধ করা যাবে।
সে অনুযায়ী সবাই টেবুনিয়া রওয়ানা হয়। টেবুনিয়ায় অ্যামবুশ করে অপেক্ষা করতে থাকে। রাত ১২টার দিকে ইপিআর জানায়, এই হালকা অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। তাই তারা ব্যাটালিয়নে ফিরে যাবে। তারা যোদ্ধাদেরও আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। নাগরবাড়িতে অবস্থানের সময় হানাদার বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে যোদ্ধাদের ধারণা হয়েছে। তাই ইপিআর চলে গেলে যোদ্ধারাও অবস্থান ত্যাগ করেন।
সকাল ৯টার দিকে ১৬ ডিভিশন নগরবাড়ি দখল করে নেয়। পালাক্রমে ভারী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ আরিচা থেকে পার করে আনে। ফলে নাগরবাড়িতেই তাদের সারা দিন কেটে যায়। পরদিন সেখান থেকেই ২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড বগুড়া ও ২৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড দিনাজপুর রওনা হয়। বগুড়া ও দিনাজপুরগামী হানাদার বাহিনী শাহজাদপুরের কাছে বাঘাবাড়ি ঘটে গিয়ে বাঁধা পায়। বড়াল নদীর ওপর বাঘাবাড়ি ঘাটে ফেরি নেই। নগরবাড়ি পতনের পর এখানকার প্রতিরোধযোদ্ধারা ফেরি সরিয়ে ফেলেছে। ১৬ ব্রিগেডের অবশিষ্ট সৈন্য ১১ এপ্রিল পাবনা দখল করতে অগ্রসর হয়।
পূর্বে পাবনায় করুন পরিণতির প্রতিশোধে হানাদার বাহিনী হিংস্র পশু হয়ে গেছে। নগরবাড়ি থেকে পাবনা পর্যন্ত রাস্তার দুধারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও বাড়িঘর ভস্মীভূত করে। রাস্তার দুপাশে ধ্বংসলীলা চালাতে চালাতে অগ্রসর হয়। আগের পরিণতির কথা ভেবে সতর্কতার সঙ্গেও চলতে থাকে। ফলে পাবনা শহরে পৌঁছায় বিকেল ৪টায়। ১৩ দিন মুক্ত থাকার পর পাবনা পুনরায় পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায়। হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধযোদ্ধারা কুষ্টিয়া হয়ে ভারতের পথে রওনা হয়।
পাবনা শহরে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাস্তায় লোকজন দেখামাত্রই গুলি করে হত্যা করে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর গুলি চালায়। পুলিশ লাইনে কয়েকজন পুলিশ অস্ত্রাগার ও গোলাবারুদ পাহারায় ছিল। হানাদার বাহিনী তাদেরও হত্যা করে। গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নুরপুর ডাকবাংলোতে ক্যাম্প স্থাপন করে পাকিস্তানি বাহিনী। ওয়াপদার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল নেয়। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গোডাউনে হানাদার বাহিনী গোলাবারুদ মজুদ করে।
১১ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঈশ্বরদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজে অবস্থান নেয়, যেন কুষ্টিয়া থেকে আক্রমণ হলে প্রতিহত করা যায়। শহরের সার্কিট হাউজ, বিসিক, পুলিশ লাইন, পলিটেকনিক, ডিগ্রি কলেজে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসায়। এভাবে পুরো শহর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দখলে চলে যায়। শহর জুড়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। শুরু হয় তাদের বর্বরতা— হত্যা, লুটতরাজ, আগুন দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে পাবনার দ্বিতীয় পর্ব।
লেখক: সাবেক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি)

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। গভীর রাতে ঢাকার মতো পাবনাতেও শুরু হয় অপরেশন সার্চলাইট। রাজশাহী থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য (১৩০ জন) রাত আড়াইটায় পাবনা পৌঁছায়। তারা বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থান নেয়। কোম্পানির কমান্ডিং অফিসার ছিল ক্যাপ্টেন আসগর, ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট রশিদ।
২৭ মার্চ সকাল থেকেই পাবনাবাসী সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধে হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে প্রাণ হারাতে থাকে। খবর পেয়ে রাজশাহী থেকে ১৮ জন সৈন্যসহ ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ডেপুটি কমান্ডিং অফিসার মেজর আসলাম পাবনা আসে। দুই দিনের যুদ্ধে মেজর আসলামসহ সবাইকে প্রাণ হারাতে হয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দেড় শ সৈন্যের হানাদার বাহিনী পাবনাবাসীর দেশীয় অস্ত্র ও সাহসের কাছে পরাজিত হয়। তাদের একজনও রাজশাহীতে ফিরে যেতে পারেনি।
২৯ মার্চ পাবনা হানাদারমুক্ত হয়। এ জেলায় কোনো সেনানিবাস বা ইপিআর ক্যাম্প ছিল না। তাই যুদ্ধে কোনো বাঙালি সেনা বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) অংশ নেয়নি। পাবনার আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা এবং স্থানীয় যুবসমাজ এই যুদ্ধে অংশ নেয়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর থেকে ছাত্রলীগ প্রস্তুতি নিতে থাকে। যুবসমাজকে সংগঠিত করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ছাত্রলীগ। পাবনা শহরে এ ধরনের চার-পাঁচটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। কেন্দ্রগুলো ২৫ মার্চ পর্যন্ত চালু ছিল।
একই সময়ে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. আমজাদ হোসেনকে (এমএনএ) আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— আব্দুর রব বগা মিয়া (এমপিএ), অ্যাডভোকেট আমিন উদ্দিন (এমপিএ), আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান মাহবুবুল হক ফেরু ও গোলাম আলী কাদেরী, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা এবং ছাত্রলীগ পাবনা জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সাত্তার লালু। ২৫ মার্চের পর পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খান ও এসপি চৌধুরী আব্দুল গফফারকে কমিটির সদস্য করা হয়।
পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন এমএনএ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বগা মিয়া এমপিএ, ন্যাপ নেতা আমিনুল ইসলাম বাদশা, রনেশ মৈত্র, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম আলী কাদেরী, দেওয়ান মাহবুবুল হক ফেরু, ওয়াজি উদ্দিন খান, নবাব আলী মোল্লা, পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সাত্তার লালু, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম বকুল, জহুরুল ইসলাম বিশুসহ অনেকেই যুদ্ধে অসীম সাহস দেখান। ছাত্র ইউনিয়নের রবিউল ইসলাম রবি ও শিরিন বানু মিতিলসহ তাদের নেতাকর্মীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন।
যুদ্ধে ছাত্রলীগের রফিকুল ইসলাম বকুল, ইকবাল হোসেন, সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, বেবী ইসলাম, মো. ইসমত, ফজলুল হক মন্টু, মোখলেছুর রহমান মুকুল, সাঈদ আকতার ডিডু, জহুরুল ইসলাম বিশু প্রমুখ ছাত্রনেতার ভুমিকা ছিল অনন্য। এই প্রতিরোধযুদ্ধে পাবনায় ডিসি ও এসপি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। অনেক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীও যুদ্ধে অংশ নেন।
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বিজয় ও জনযুদ্ধের ক্ষেত্রে পাবনা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। বিজয়ের পর পাবনাকে হানাদার মুক্ত রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। যেকোনো মূল্যে পাবনাকে শত্রুমুক্ত রাখতে যোদ্ধারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। হানাদার বাহিনীর পুনর্প্রবেশ ঠেকাতে তাই নগরবাড়ি ঘাটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়ে।
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার ছিলো নগরবাড়ি। ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গে যেতে শুধু এ ঘাটেই গাড়িসহ পারাপারের সুবিধা ছিল। ফুলছড়িঘাট বা ভূঞাপুরে গাড়ি পারাপারের সুযোগ ছিল না। তাই নগরবাড়ির গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকেই নাকি নগরবাড়ী-দিনাজপুর সড়ক নির্মম করা হয়েছিল। উত্তরাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধ করতে হলে নগরবাড়ী ঘাটের দখল নেওয়া পাকিস্তানিদের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
ভৌগোলিক দিক থেকে পাবনা ছিল হানাদার বাহিনীর জন্য নিরাপদ জেলা। পদ্মা ও যমুনা পরিবেষ্টিত এই জেলার ভারতের সঙ্গে কোনো সীমান্ত নেই। উত্তরে রংপুর সেনানিবাস, উত্তর-পশ্চিমে রাজশাহী সেনানিবাস। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নিয়ন্ত্রণে থাকলে কুষ্টিয়া থেকেও যেকোনো হামলা প্রতিহত করা সম্ভব। এ ছাড়া ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গ ও রংপুর সেনানিবাসে রসদ পাঠাতেও নগরবাড়ি ঘাট গুরুত্বপুর্ণ। অন্যথায় পুরো উত্তরবঙ্গ মুক্তাঞ্চলে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।
২৯ মার্চ শত্রুমুক্ত করার পর পাবনার প্রতিরোধযোদ্ধারা প্রস্তুতি জোরদার করে। পুনরায় আক্রমণ প্রতিহত করতে পুলিশ, আনসার ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ‘সম্মিলিত বাহিনী’ গঠন করা হয়। সঙ্গত কারণেই সম্মিলিত বাহিনীতে বাঙালি সৈনিক বা ইপিআর জোয়ান ছিল না। ৩১ মার্চ এক সভায় নগরবাড়ি প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। পুলিশ ও পরাজিত হানাদার বাহিনীর আধুনিক অস্ত্রগুলো তখন জনযোদ্ধাদের হাতে। সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশি। শহরে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করায় যোদ্ধাদের মনোবল পাহাড়সম।
পাবনা জেলা ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত সংসদ সদস্য রফিকুল ইসলাম বকুলের নেতৃত্বে প্রায় ২০০ যোদ্ধা ২ এপ্রিল নগরবাড়িতে অবস্থান নেয়। শহরের বিজয়ী যোদ্ধরাই প্রতিরোধের প্রধান শক্তি। শহরের যুদ্ধে অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে রফিকুল ইসলাম বকুল তখন সবার আস্থাভাজন।
হানাদার বাহিনীর দখল করা আটটি জিপ ও বড় একটি বাস নিয়ে সবাই একযোগে পাবনা থেকে রওয়ানা হয়। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাংকার নির্মাণ করে সামনে বালির বস্তা দেওয়া হয়। যোদ্ধারা ঘাটে অপেক্ষমাণ তিনটি ফেরির চাবি দখলে নেযন। ফলে সেগুলো আর আরিচায় ফেরত যেতে পারে না। আরিচা থেকে নৌকাযোগে পার হয়ে আসা লোকজনের মাধ্যমে যোদ্ধারা ওপারের খবর সংগ্রহ করতে থাকে।
৪ এপ্রিল সকাল ১০টায় হঠাৎ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যুদ্ধবিমান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। জবাবে যোদ্ধারা বিমান লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ছুড়ে। সৌভাগ্যক্রমে কেউ হতাহত হয়নি। এই আক্রমণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রতিরোধ অবস্থান সম্পর্কে পাকিস্তানিরা খবর পেয়ে গেছে। যোদ্ধারা মনে করেছে বড় একটি যুদ্ধ তাদের মোকাবিলা করতে হবে।
মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই পাবনায় মাওবাদীদের শক্তিশালী অবস্থান ছিল। মাওবাদীরা এলাকায় নকশাল নামের আতঙ্ক। নকশালদের সঙ্গে সংঘাত-সংঘর্ষ করেই পাবনায় আওয়ামী লীগকে রাজনীতি করতে হয়েছে। শুরু থেকেই নকশালরা মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। প্রসঙ্গত, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় নকশালরা পাকিস্তানিদের পক্ষে ছিল। তারাও রাজাকার-আলবদরদের মতোই মুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষকে হত্যা, বাড়িঘর দখল ও লুটপাট করে।
শহরের যোদ্ধারা সবাই নগরবাড়িতে। ফলে শহর অরক্ষিত। এ সুযোগে ৩ এপ্রিল নকশালরা শহরে প্রবেশ করে। তবে বড় কোনো অঘটন না ঘটিয়েই শহর ছেড়ে চলে যায়। কারণ তারা জানে, পুলিশ ও পরাজিত পাকিস্তানিদের আধুনিক অস্ত্র এখন যোদ্ধাদের কাছে। খবর পেয়ে কয়েকজন যোদ্ধা শহরে ফিরে আসে। তারা গাড়ি নিয়ে টহল দিয়ে অস্তিত্ব জানান দেয়। বিষয়টি যোদ্ধাদের জন্য নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এদিকে পাবনার ডিসি নুরুল কাদের খান শহরে অবস্থান করে ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর গতিবিধি জানার চেষ্টা করছেন। কোনো খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রফিকুল ইসলাম বকুলকে তা জানিয়ে দেন। নগরবাড়ির কাছেই পাবনার পথে একটি ব্রিজ ছিল। ডিসি ৬ এপ্রিল রফিকুল ইসলাম বকুলকে ব্রিজটি ভেঙে ফেলতে বলেন, যেন পাকিস্তানিরা নদী পার হলেও শহরে প্রবেশের আগেই আবারও বাধার সম্মুখীন হয়।
যোদ্ধাদের কাছে তখন ব্রিজ ভাঙার জন্য কোনো অ্যামুনিশন নেই। তাই কোদাল, শাবল, হাতুড়ি জোগাড় করতে স্থানীয়দের সাহায্য চান তারা। কিন্তু স্থানীয়রা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে একজোট হয়ে ব্রিজ ভাঙার বিরোধিতা করে। অনেক অনুরোধ করার পরও তারা রাজি হয় না। সন্ধ্যায় ডিসি অবস্থান দেখতে নগরবাড়ি যান। ব্রিজ না ভাঙায় তিনি খুব রেগে যান। ডিসিও চেয়ারম্যানকে ব্রিজ ভাঙার কারণ বোঝান ও সহযোগিতা চান। কিন্তু চেয়ারম্যান তার সিদ্ধান্তে অটল।
এ সময় ডিসি তার হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে হঠাৎ ফাঁকা গুলি ছোড়েন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন যোদ্ধাও গুলি ছোড়েন। ভয়ে লোকজন সরে যায়। চেয়ারম্যানের কলার ধরে টেনে এনে ডিসি দ্রুত ব্রিজ ভাঙার নির্দেশ দেন। এই কৌশল দারুণভাবে কাজ করে। স্থানীয়রাও যোগ দেয়, কিন্তু ব্রিজ ভাঙা সম্ভব হয় না। অগত্যা ব্রিজসংলগ্ন রাস্তা কেটে প্রতিরোধ গড়া হয়।
৭ এপ্রিল দুপুরে ফের পাকিস্তানিরা বিমান আক্রমণ চালায়। এ দিনও কেউ হতাহত হয়নি। কিন্তু বারবার বিমান আক্রমণে অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। পুলিশ ও আনসারদের অনেকেই গোপনে অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবে পাবনা যুদ্ধের বিজয়ীরা অবস্থানে অনড়। সব মিলিয়ে অটল থাকেন প্রায় ৮০ জন যোদ্ধা।
৮ এপ্রিল কোনো আক্রমণ না হলেও পরদিন ৯ এপ্রিল দুই দফায় বিমান হামলা হয়। এবারের আক্রমণ আগের চেয়ে বেশি জোরালো। দুটি বিমান থেকে মেশিনগানের ব্রাশফায়ার করে। আগের মতোই যোদ্ধারা পালটা গুলি ছোড়েন। প্রতিবার আক্রমণের পরই দেখতে হয়, কেউ হতাহত হলো কি না। সৌভাগ্যের বিষয়, এবারেও সবাই রক্ষা পায়।
এদিকে নৌকায় নদী পার হয়ে আসা লোকজন জানায়, আরিচায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্যাংক, কামান, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ট্রাক, গানবোটসহ বিপুল সৈন্যের সমাবেশ করেছে। যেকোনো সময় তারা এ পারে আক্রমণ করতে পারে।
খবর পেয়ে যোদ্ধারাও প্রস্তুতি নেয়। নিজ নিজ বাংকারে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। এ খবরে নগরবাড়ি এলাকা জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। আগের কয়দিন স্থানীয়রা যোদ্ধাদের প্রচুর খবর দিত। কিন্তু তারাও তখন কেউ নেই। সারা দিন কাটে ক্ষুধার্ত অবস্থায়। গভীর রাতে কয়েকজন ছাত্র খিচুড়ি নিয়ে হাজির। পরিমাণে কম হলেও সেটুকুই সবাই ভাগাভাগি করে খায়। এভাবে রাত কেটে যায়, কোনো আক্রমণ হয় না।
ভৌগোলিক কারণেই হয়তো পাকিস্তানিরা পাবনায় অপরেশন সার্চলাইট কার্যকর করতে খুব গুরুত্ব দেয়নি। তারা শহরে অবস্থান নিয়ে নির্বিচারে গুলি করে সাধারণ মানুষ হত্যা, আওয়ামী লীগসহ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার, বিভিন্ন স্থাপনা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নির্বিঘ্নে ৩৬ ঘণ্টা পার করে। হানাদার বাহিনী ধারণা করেছিল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। এ কারণে ওয়াপদার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবন ও চেকপোস্টে অল্প কয়জন সৈন্য মোতায়েন করে। সিদ্দিক সালিক তার ‘উইটনেস টু সারেন্ডার’ বইয়ে পাবনায় এসব স্থাপনায় অল্প সৈন্য মোতায়েনকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেন।
দুদিন পর যখন পাবনার সর্বস্তরের জনসাধারণ হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তখন তাদের চরম মূল্য দিতে হয়। এ ঘটনা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই পুনর্দখলের বিষয়কে হানাদার বাহিনী বাড়তি গুরুত্ব দেয়। তখন যেন নগরবাড়ি দখলের ওপর গোটা উত্তরবঙ্গে যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করছিল। মেজর জেনারেল নজর হুসাইন শাহের নেতৃত্বে ১৬ ডিভিশনকে পাবনাসহ উত্তরাঞ্চল দখল করতে পাঠানো হয়।
১০ এপ্রিল ভোর হয় অন্যদিনের মতোই। কিন্তু একটু বেলা বাড়তেই চিত্র পালটে যায়। দুটি যুদ্ধবিমান তীব্রবেগে উড়ে আগের মতোই গুলিবর্ষণ শুরু করে। একই সঙ্গে বিকট শব্দে মর্টার শেল পড়তে থাকে বাংকারের অদূরে। শেলের আঘাতে বিশাল গর্ত তৈরি হতে থাকে। মাটি গুঁড়ো হয়ে অনেক ওপরে উঠে যায়। পুরো এলাকা তখন ধুলোয় অন্ধকার। আর্টিলারি গানের গোলায় পুরো এলাকা প্রকম্পিত। সৌভাগ্য, একটি শেলও বাংকারে আঘাত করেনি। একটি শেল আঘাত করলেই একসঙ্গে কয়েকটি বাংকার ধ্বংস হয়ে যাবে, যোদ্ধাদের জীবনও যাবে।
নগরবাড়ি ঘটে অনেকগুলো ব্যবসায়িক গুদামঘর ছিলো। গোলার আঘাতে বেশ কয়েকটি গুদামে আগুন ধরে যায়। চতুর্মুখী আক্রমণে যোদ্ধারা দিশেহারা। পুরো এলাকা ধুলোয় আচ্ছন্ন, কিছুই দেখা যায় না। বারবার বিমান থেকে বৃষ্টির মতো গুলোবর্ষণ, নদী দিক থেকে ব্রাশ ফায়ার, মর্টারের আঘাত— এক ভয়ংকর পরিস্থিতি!
যোদ্ধাদের হাতে হালকা অস্ত্র। যুদ্ধের জন্য তেমন প্রশিক্ষণও নেই। অন্যদিকে হানাদার বাহিনী ভারী অস্ত্রের গোলা বর্ষণ করছে। তারা অন্যতম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবেই পরিচিত। এমন অসম যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ তো দূরের কথা, জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়াই কঠিন। শত্রুর অবস্থানও বোঝার উপায় নেই। তবু যোদ্ধারা পালটা গুলি ছুঁড়তে থাকেন অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মতো। স্বাভাবিকভাবেই তাতে কোনো ফল মেলে না।
অবস্থান ত্যাগের নির্দেশ পেয়ে ঝুঁকি নিয়েই সবাই দৌড়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে যায়। দ্রুত গাড়ি পাবনার দিকে রওনা হয়। তখন বুঝতে পারে, সবাই অক্ষত আছে। কিন্তু পাবনা শত্রুমুক্ত রাখা সম্ভব হয় না— এ কষ্টে সবারই মন খারাপ। এখন তারা কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই বুঝতে পারেন না। সকাল ৯টার দিকে নগরবাড়ি পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায়।
পাবনার পথে আতাইকুলা গিয়ে যোদ্ধারা ইপিআর সৈন্য ভর্তি একটি ট্রাক দেখতে পায়। তাদের থামতে বলা হয়। কথা বলে জানা যায়, তারা নগরবাড়িতে জনযোদ্ধদের সহযোগিতা করতে যাচ্ছে। নগরবাড়ির অবস্থার কথা শুনে তাদের আর যাওয়া হলো না। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়, আতাইকুলাতেই অ্যামবুশ করবে। তাহলে শহরে প্রবেশের আগেই হানাদার বাহিনীকে রুখে দেওয়া যাবে।
অ্যামবুশ পেতে পাকিস্তানিদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন যোদ্ধারা। অনেকক্ষণ অবস্থান করেও হানাদার বাহিনীর গতিবিধির খবর পাওয়া গেল না। রাস্তায় গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজনেরও চলাচল নেই। কিছু বুঝতে না পেরে সেখান থেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজশাহী-পাবনা সড়কে টেবুনিয়ায় অ্যামবুশ করতে বলে ইপিআর। তাহলে রাজশাহী থেকে আসা সেনাবাহিনী শহরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধ করা যাবে।
সে অনুযায়ী সবাই টেবুনিয়া রওয়ানা হয়। টেবুনিয়ায় অ্যামবুশ করে অপেক্ষা করতে থাকে। রাত ১২টার দিকে ইপিআর জানায়, এই হালকা অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। তাই তারা ব্যাটালিয়নে ফিরে যাবে। তারা যোদ্ধাদেরও আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। নাগরবাড়িতে অবস্থানের সময় হানাদার বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে যোদ্ধাদের ধারণা হয়েছে। তাই ইপিআর চলে গেলে যোদ্ধারাও অবস্থান ত্যাগ করেন।
সকাল ৯টার দিকে ১৬ ডিভিশন নগরবাড়ি দখল করে নেয়। পালাক্রমে ভারী অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ আরিচা থেকে পার করে আনে। ফলে নাগরবাড়িতেই তাদের সারা দিন কেটে যায়। পরদিন সেখান থেকেই ২০৫ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড বগুড়া ও ২৩ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড দিনাজপুর রওনা হয়। বগুড়া ও দিনাজপুরগামী হানাদার বাহিনী শাহজাদপুরের কাছে বাঘাবাড়ি ঘটে গিয়ে বাঁধা পায়। বড়াল নদীর ওপর বাঘাবাড়ি ঘাটে ফেরি নেই। নগরবাড়ি পতনের পর এখানকার প্রতিরোধযোদ্ধারা ফেরি সরিয়ে ফেলেছে। ১৬ ব্রিগেডের অবশিষ্ট সৈন্য ১১ এপ্রিল পাবনা দখল করতে অগ্রসর হয়।
পূর্বে পাবনায় করুন পরিণতির প্রতিশোধে হানাদার বাহিনী হিংস্র পশু হয়ে গেছে। নগরবাড়ি থেকে পাবনা পর্যন্ত রাস্তার দুধারে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও বাড়িঘর ভস্মীভূত করে। রাস্তার দুপাশে ধ্বংসলীলা চালাতে চালাতে অগ্রসর হয়। আগের পরিণতির কথা ভেবে সতর্কতার সঙ্গেও চলতে থাকে। ফলে পাবনা শহরে পৌঁছায় বিকেল ৪টায়। ১৩ দিন মুক্ত থাকার পর পাবনা পুনরায় পাকিস্তানিদের দখলে চলে যায়। হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশের আগেই প্রতিরোধযোদ্ধারা কুষ্টিয়া হয়ে ভারতের পথে রওনা হয়।
পাবনা শহরে প্রবেশ করেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাস্তায় লোকজন দেখামাত্রই গুলি করে হত্যা করে। সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর গুলি চালায়। পুলিশ লাইনে কয়েকজন পুলিশ অস্ত্রাগার ও গোলাবারুদ পাহারায় ছিল। হানাদার বাহিনী তাদেরও হত্যা করে। গোটা শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নুরপুর ডাকবাংলোতে ক্যাম্প স্থাপন করে পাকিস্তানি বাহিনী। ওয়াপদার বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা দখল নেয়। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গোডাউনে হানাদার বাহিনী গোলাবারুদ মজুদ করে।
১১ এপ্রিল রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঈশ্বরদীর হার্ডিঞ্জ ব্রিজে অবস্থান নেয়, যেন কুষ্টিয়া থেকে আক্রমণ হলে প্রতিহত করা যায়। শহরের সার্কিট হাউজ, বিসিক, পুলিশ লাইন, পলিটেকনিক, ডিগ্রি কলেজে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে চেকপোস্ট বসায়। এভাবে পুরো শহর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দখলে চলে যায়। শহর জুড়ে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। শুরু হয় তাদের বর্বরতা— হত্যা, লুটতরাজ, আগুন দিয়ে বাড়িঘর জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে পাবনার দ্বিতীয় পর্ব।
লেখক: সাবেক মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি)
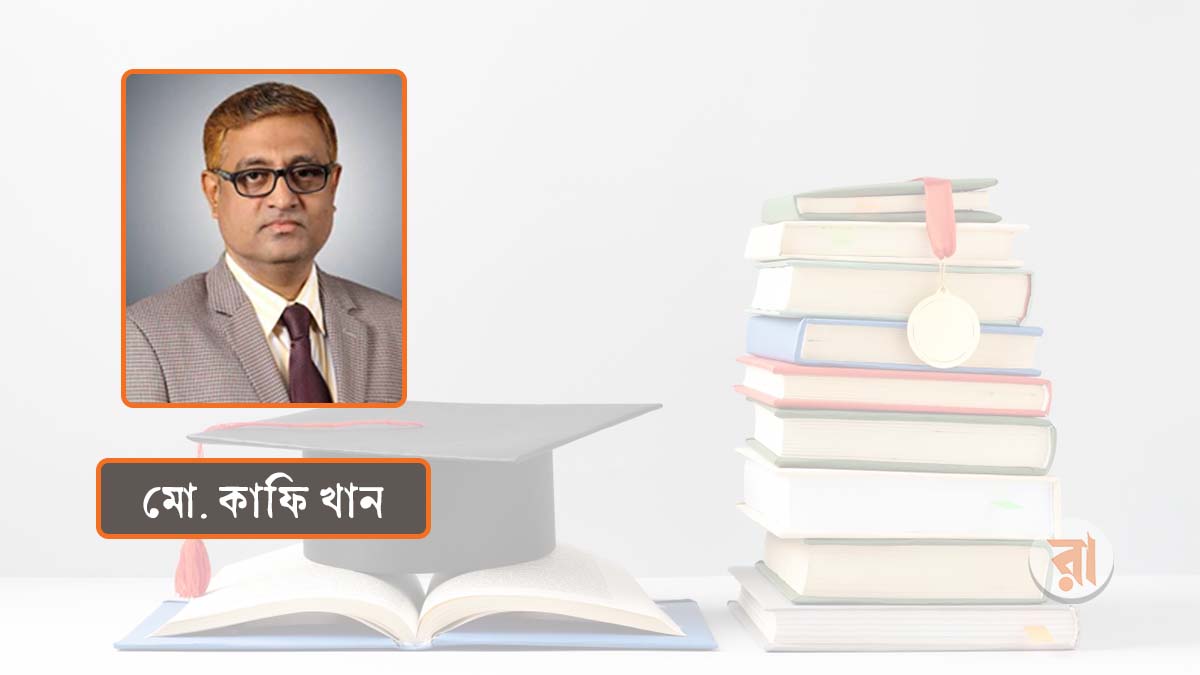
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই একাডেমিক মেরিটোক্রেসিকে (বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, মূল্যায়ন ও নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে শুধু যোগ্যতা ও কাজের মানের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত পরিচয়, রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবিরের ভিত্তিতে নয়) যথাযথভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
৪ দিন আগে
একজন উপদেষ্টার কাছ থেকে আমরা আশা করি নীতিগত সততা, সংস্কারের সাহস এবং মেধাবীদের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা। কিন্তু এখানে দেখা গেল উল্টো চিত্র— সংস্কারের প্রস্তাবকে শাস্তি দিয়ে দমন করা হলো। নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়; নীরবতা এখানে পক্ষ নেওয়া। আর সেই পক্ষটি দুর্নীতির সুবিধাভোগীদের।
৫ দিন আগে
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বা সংস্কার অনিবার্য। সেই সংস্কারের স্পিরিট বা চেতনা আমি এখন বিএনপির রাজনীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই দেশের এ বাস্তবতায় জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিএনপির সঙ্গেই পথ চলাকে আমি শ্রেয় মনে করেছি এবং যোগদানের সিদ্ধান
৬ দিন আগে
বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজার আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে এখনো পিছিয়ে। বছরে ৩০-৪০ লাখ দেশীয় পর্যটক এলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নগণ্য। তুলনায় থাইল্যান্ড বছরে প্রায় চার কোটি বিদেশি পর্যটক থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে। আর মালদ্বীপ মাত্র ২০ লাখ পর্যটক থেকেই তার জিডিপ
৭ দিন আগে