
ড. কামরুল হক

কখনো কি ভেবে দেখেছেন, গণমাধ্যমের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ? দেশের জনসাধারণের সঙ্গে গণমাধ্যম ও রাজনীতির সম্পর্ক কতটা নিবিড়? আমরা তো সবসময় রাজনীতির আবহের মধ্যেই বসবাস করি। আর গণমাধ্যম তো এখন প্রতি মুহূর্তেই হাতের নাগালের মধ্যে। যখন-তখন গণমাধ্যমের বিশাল তথ্যভাণ্ডারে ডুব দিতে পারি। তাই হয়তো বিষয়টি আমাদের ভাবায় না।
আমরা না ভাবলেও গণমাধ্যম কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বাহন হয়ে কাজ করে সবসময়। যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে প্রাণবন্তও রাখে। সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টাল প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক খবর ও খবরের বিশ্লেষণ প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের পাতায় পাঠক বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরে। নিউজ পোর্টালের পাঠক কমেন্ট বক্সে তাদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও ক্রমাগত রাজনীতির বিভিন্ন খবর এবং বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচার করে। টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতারা তাদের মতামত প্রকাশ করে। রাজনৈতিক ঘটনার খবর ও বিশ্লেষণ দিনের পর দিন গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হলে একসময় তা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। জনসাধারণকে তা প্রভাবিত করতে থাকে। জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।
পেছনে ফিরে তাকালেও গণমাধ্যম ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের নজির চোখে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় দেড় শ বছর আগে। এ অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে, রংপুর থেকে। বাংলা এই সাপ্তাহিকটি টিকে ছিল প্রায় এক দশক। এটি প্রকাশিত হয়েছিল এমন একসময় যখন সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ক্রমশ রাজনীতিমুখী হতে শুরু করেছে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়টিতে পত্রিকাটির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল রাজনীতি। তবে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যর্থতার পর গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের রোষানলে পড়ে ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’। আইনি মারপ্যাচে পড়ে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এই সংবাদপত্রের।
বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র ‘ঢাকা নিউজ’। ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল ইংরেজি এই সাপ্তাহিকটি ঢাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা রাখে। ‘ঢাকা নিউজ’ প্রায় বছর ধরে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছিল। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সিপাহিরা রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হয়। আসন্ন বিপ্লবের জন্যে নিজেদের সংগঠিত করে।
ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’। আত্মপ্রকাশ করে ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ। প্রায় এক শ বছর ধরে প্রকাশিত হয় এই সংবাদপত্র। সে সময় ঢাকার প্রভাবশালী এই সংবাদপত্রের পাতা উলটালে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আঁচ করা যায়।
আরেকটি প্রাচীন সংবাদপত্র ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’। প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। এ সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নিজেই লিখেছেন— ‘যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল তখন রাজনীতিময় প্রস্তাব গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রক্ষার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার হইয়া বাহুলারূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল।’
পুরোনো আরেকটি সংবাদপত্র ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’। ১৮৬৮ সালে যশোরের চরমাগুরা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রও জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ ছিল। শুরু থেকেই সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিল নির্ভীকভাবে। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ জনসাধারণকে ইংরেজ মুখাপেক্ষী না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে সবসময়।
উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সে সময়ের সংবাদপত্রের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে রাজনীতি আর ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর তীব্র ব্রিটিশবিরোধিতা শুরু হয়। এর প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে।
বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পর বাংলাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়— একটি প্রকাশ্য স্বাদেশি আন্দোলন, আরেকটি গোপন সশস্ত্র তৎপরতা। দুটি আন্দোলনই সমকালীন সংবাদপত্রের ব্যাপক সমর্থন পায়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতিকে উপজীব্য করে সাংবাদিকতায় একটি নতুন ধারার সংযোজন ঘটে।
পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময়ের প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল— দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেহাদ, জিন্দেগী, ইনসাফ, পাকিস্তান অবজারভার ও মর্নিং নিউজ। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন পূর্ণতা পায়।
ভাষা আন্দোলনে সব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি এক ছিল না। সব সংবাদপত্র এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কারওভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কেউ ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু পরবর্তী সময় সংবাদপত্র সরকারবিরোধী রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলায় সহযোগী হয়ে উঠে। একসময় সরকারবিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে সংবাদপত্র। এ সব আন্দোলন-সংগ্রামে সরকার সমর্থক কিছু সংবাদপত্র ছাড়া সব সংবাদপত্রই জোরালো ভূমিকা রেখেছে। সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রবহমান রেখেছে। শুধু সংবাদ পরিবেশনই না, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশেও সাহসী হয়ে উঠেছিল।
১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে রাজনীতি শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। স্থগিত করা হয় সংবিধান। রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে কালাকানুনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে বিধিনিষেধের মাঝেও সুযোগ পেলেই সরকারবিরোধী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তুলে ধরার চেষ্টা করত সংবাদপত্র।
বছর চারেক পরে সামরিক শাসন শিথিল হলে সীমিত রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয়। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্ব দিতে থাকে। মাঝে-মাঝে সরকারের বেঁধে দেওয়া গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলনকে বেশির ভাগ সংবাদপত্রই উৎসাহিত করেছিল। ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো খুবই গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়।
এ সময় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক কলাম ও অভিমত রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে জোরালো অবস্থান নেওয়ায় স্বৈরাচারী আইয়ূব সরকারের রোষানলে পড়ে অনেক সংবাদপত্র। দৈনিক ইত্তেফাককে ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন বন্ধ করে দেয় আইয়ূব সরকার। দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় সংবাদপত্রটির প্রকাশনা বন্ধ ছিল।
ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ওই বছরের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সরকারবিরোধী গণআন্দোলন তীব্র হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থানের খবর ফলাও করে তুলে ধরা হয় সে সময়ের প্রভাবশালী দৈনিক আজাদ, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার, এমনকি সরকারি ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন দৈনিক পাকিস্তানসহ সব সংবাদপত্রে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক।
১৯৭০ সালে সামরিক শাসনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। কিন্তু নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আসতেই শুরু হয় পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। এক পর্যায়ে বাংলাদেশব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। সংবাদপত্রগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে আন্দোলনের খবর। দিনের পর দিন এই আন্দোলনকে প্রাণবন্ত রাখে সংবাদপত্র।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের ভেতরে ও বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে সংবাদপত্র। তবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান সংবাদপত্রগুলো হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত জীবন। কিন্তু অবরুদ্ধ ছিল না তাদের বিবেক। অনেক সাংবাদিকই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অধিকৃত সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। গোয়েন্দা নজরদারিও ছিল অনেকের ওপর। তবে স্বাধীনতাপ্রত্যাশী এই সাংবাদিকদের অনেকেই সুযোগ পেলেই আভাসে-ইঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সংবাদপত্রে।
স্বাধীনতা-উত্তরকালে সত্তর দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল কিছুটা কম। তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অস্থিরতা ছিল ঠিকই। বিরোধী মতবাদ বিকশিত হওয়ার প্রবণতাও ছিল। সংবাদপত্রও তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। নানা আইন-কানুনের বেড়াজাল মোকাবিলা করে সংবাদপত্র নিজেকে শৃঙ্খল মুক্ত রাখতে চেয়েছে।
আশির দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বাধীনতা-উত্তর যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আশির দশক ছিল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর। প্রায় পুরো দশকই রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপুল গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এই দশকের রাজনীতির প্রবণতা। দিনের পর দিন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ রাজপথে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। রাজনীতিতে জনসাধারণের ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।
পুরো সময়টাতেই সংবাদপত্র রাজনীতির সহযাত্রী ছিল। শুধু তাই না, এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সংবাদপত্র এতটাই একাত্ম হয়েছিল যে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করে সরকার। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা এরশাদ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন। এর ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একটানা আট দিন দেশে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা।
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ বেশ কিছু আইন সংশোধন করা হয়। এতে সংবাদপত্র অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। দেশে ইলেট্রনিক মিডিয়ারও প্রসার ঘটতে থাকে। অনেক প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল চালু হয়। এই সব টেলিভিশন চ্যানেলে টকশো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। টকশোতে চলমান রাজনৈতিক ঘটনা ও বিষয় অগ্রাধিকার পায়। অনেক টকশোতে দর্শক-শ্রোতা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগও পায়।
ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের কারণে মুদ্রিত সংবাদপত্রের পাশাপাশি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এখন দেশের জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলোও নিউজ পোর্টাল চালু করেছে। এই সব নিউজ পোর্টালের কনটেন্টের বিশাল অংশ জুড়েই থাকে রাজনৈতিক খবর ও তার বিশ্লেষণ। পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করেই সংবাদপত্র ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিশাল অংশ জুড়ে প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক খবর।
সন্দেহ নেই, গণমাধ্যম ও রাজনীতির ইতিহাস সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। গণমাধ্যম যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল সবসময়, আছেও। সাম্প্রতিক সময়েও তার নজির দেখা গেছে।
আদিকাল থেকেই গণমাধ্যম ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে অবহিত করেছে। সচেতন করেছে। গণমাধ্যমই রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তাপ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। জনসম্পৃক্ততা তৈরি করেছে। দাবি আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছে।
অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহল সবসময় নিজেদের অন্যায়-অবিচার আড়াল করতে চেয়েছে। অপতৎপরতা যেন ফাঁস না হয়, সে জন্য গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে। এ জন্য নানা কৌশল ব্যবহার করেছে। কিন্তু গণমাধ্যম কোনো না কোনোভাবে সত্য প্রকাশ করেছে। দেশের মানুষকে তা অবহিত করেছে।
ঐতিহাসিকভাবেই গণমাধ্যম, রাজনীতি ও দেশের জনসাধারণ একই সূত্রে গাঁথা। এই তিনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে নিরন্তর। এই ত্রিমুখী মিথষ্ক্রিয়া হয়তো চলতেই থাকবে।
লেখক: সাংবাদিক ও গণমাধ্যম গবেষক; সাবেক পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

কখনো কি ভেবে দেখেছেন, গণমাধ্যমের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ? দেশের জনসাধারণের সঙ্গে গণমাধ্যম ও রাজনীতির সম্পর্ক কতটা নিবিড়? আমরা তো সবসময় রাজনীতির আবহের মধ্যেই বসবাস করি। আর গণমাধ্যম তো এখন প্রতি মুহূর্তেই হাতের নাগালের মধ্যে। যখন-তখন গণমাধ্যমের বিশাল তথ্যভাণ্ডারে ডুব দিতে পারি। তাই হয়তো বিষয়টি আমাদের ভাবায় না।
আমরা না ভাবলেও গণমাধ্যম কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বাহন হয়ে কাজ করে সবসময়। যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামকে প্রাণবন্তও রাখে। সংবাদপত্র ও নিউজ পোর্টাল প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক খবর ও খবরের বিশ্লেষণ প্রকাশ করে। সংবাদপত্রের মতামত প্রকাশের পাতায় পাঠক বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেদের চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরে। নিউজ পোর্টালের পাঠক কমেন্ট বক্সে তাদের অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
টেলিভিশন চ্যানেলগুলোও ক্রমাগত রাজনীতির বিভিন্ন খবর এবং বিশ্লেষণমূলক অনুষ্ঠান ও টকশো প্রচার করে। টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে দর্শক-শ্রোতারা তাদের মতামত প্রকাশ করে। রাজনৈতিক ঘটনার খবর ও বিশ্লেষণ দিনের পর দিন গণমাধ্যমে প্রতিফলিত হলে একসময় তা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। জনসাধারণকে তা প্রভাবিত করতে থাকে। জনমতের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনমত গঠনে ভূমিকা রাখে।
পেছনে ফিরে তাকালেও গণমাধ্যম ও রাজনীতির আন্তঃসম্পর্কের নজির চোখে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু হয় দেড় শ বছর আগে। এ অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’ প্রকাশিত হয় ১৮৪৭ সালে, রংপুর থেকে। বাংলা এই সাপ্তাহিকটি টিকে ছিল প্রায় এক দশক। এটি প্রকাশিত হয়েছিল এমন একসময় যখন সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ক্রমশ রাজনীতিমুখী হতে শুরু করেছে। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়টিতে পত্রিকাটির প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল রাজনীতি। তবে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যর্থতার পর গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের রোষানলে পড়ে ‘রঙ্গপুর বার্তাবহ’। আইনি মারপ্যাচে পড়ে প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এই সংবাদপত্রের।
বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংবাদপত্র ‘ঢাকা নিউজ’। ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল ইংরেজি এই সাপ্তাহিকটি ঢাকা থেকে আত্মপ্রকাশ করে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা রাখে। ‘ঢাকা নিউজ’ প্রায় বছর ধরে সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছিল। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে সিপাহিরা রাজনৈতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত হয়। আসন্ন বিপ্লবের জন্যে নিজেদের সংগঠিত করে।
ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ‘ঢাকা প্রকাশ’। আত্মপ্রকাশ করে ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ। প্রায় এক শ বছর ধরে প্রকাশিত হয় এই সংবাদপত্র। সে সময় ঢাকার প্রভাবশালী এই সংবাদপত্রের পাতা উলটালে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আঁচ করা যায়।
আরেকটি প্রাচীন সংবাদপত্র ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’। প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ সালে কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। এ সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নিজেই লিখেছেন— ‘যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল তখন রাজনীতিময় প্রস্তাব গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রক্ষার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার হইয়া বাহুলারূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল।’
পুরোনো আরেকটি সংবাদপত্র ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’। ১৮৬৮ সালে যশোরের চরমাগুরা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদপত্রও জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ ছিল। শুরু থেকেই সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছিল নির্ভীকভাবে। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ জনসাধারণকে ইংরেজ মুখাপেক্ষী না থেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে সবসময়।
উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল ‘ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বরে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সে সময়ের সংবাদপত্রের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে রাজনীতি আর ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর তীব্র ব্রিটিশবিরোধিতা শুরু হয়। এর প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে।
বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পর বাংলাদেশে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দুটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়— একটি প্রকাশ্য স্বাদেশি আন্দোলন, আরেকটি গোপন সশস্ত্র তৎপরতা। দুটি আন্দোলনই সমকালীন সংবাদপত্রের ব্যাপক সমর্থন পায়। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতিকে উপজীব্য করে সাংবাদিকতায় একটি নতুন ধারার সংযোজন ঘটে।
পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্র রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময়ের প্রভাবশালী সংবাদপত্রের মধ্যে ছিল— দৈনিক আজাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ, দৈনিক পাকিস্তান, ইত্তেহাদ, জিন্দেগী, ইনসাফ, পাকিস্তান অবজারভার ও মর্নিং নিউজ। দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৫২ সালে এ আন্দোলন পূর্ণতা পায়।
ভাষা আন্দোলনে সব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি এক ছিল না। সব সংবাদপত্র এই আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। কারওভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কেউ ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু পরবর্তী সময় সংবাদপত্র সরকারবিরোধী রাজনৈতিক ধারা গড়ে তোলায় সহযোগী হয়ে উঠে। একসময় সরকারবিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে সংবাদপত্র। এ সব আন্দোলন-সংগ্রামে সরকার সমর্থক কিছু সংবাদপত্র ছাড়া সব সংবাদপত্রই জোরালো ভূমিকা রেখেছে। সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রবহমান রেখেছে। শুধু সংবাদ পরিবেশনই না, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশেও সাহসী হয়ে উঠেছিল।
১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে রাজনীতি শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। জাতীয় পরিষদ ভেঙে দেওয়া হয়। স্থগিত করা হয় সংবিধান। রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। সেই সঙ্গে কালাকানুনের মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবে বিধিনিষেধের মাঝেও সুযোগ পেলেই সরকারবিরোধী রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা তুলে ধরার চেষ্টা করত সংবাদপত্র।
বছর চারেক পরে সামরিক শাসন শিথিল হলে সীমিত রাজনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয়। এ সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্ব দিতে থাকে। মাঝে-মাঝে সরকারের বেঁধে দেওয়া গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ছয়দফা আন্দোলনকে বেশির ভাগ সংবাদপত্রই উৎসাহিত করেছিল। ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা থেকে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো খুবই গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়।
এ সময় সংবাদপত্রের রাজনৈতিক কলাম ও অভিমত রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সপক্ষে জোরালো অবস্থান নেওয়ায় স্বৈরাচারী আইয়ূব সরকারের রোষানলে পড়ে অনেক সংবাদপত্র। দৈনিক ইত্তেফাককে ১৯৬৬ সালের ১৭ জুন বন্ধ করে দেয় আইয়ূব সরকার। দীর্ঘ আড়াই বছরেরও বেশি সময় সংবাদপত্রটির প্রকাশনা বন্ধ ছিল।
ষাটের দশকের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। ওই বছরের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সরকারবিরোধী গণআন্দোলন তীব্র হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। গণঅভ্যুত্থানের খবর ফলাও করে তুলে ধরা হয় সে সময়ের প্রভাবশালী দৈনিক আজাদ, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার, এমনকি সরকারি ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন দৈনিক পাকিস্তানসহ সব সংবাদপত্রে। গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি পুনরায় প্রকাশনা শুরু করে দৈনিক ইত্তেফাক।
১৯৭০ সালে সামরিক শাসনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। কিন্তু নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি আসতেই শুরু হয় পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। এক পর্যায়ে বাংলাদেশব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। সংবাদপত্রগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করে আন্দোলনের খবর। দিনের পর দিন এই আন্দোলনকে প্রাণবন্ত রাখে সংবাদপত্র।
১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের ভেতরে ও বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে সংবাদপত্র। তবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান সংবাদপত্রগুলো হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সাংবাদিকদের পেশাগত জীবন। কিন্তু অবরুদ্ধ ছিল না তাদের বিবেক। অনেক সাংবাদিকই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অধিকৃত সংবাদপত্রে কাজ করেছেন। গোয়েন্দা নজরদারিও ছিল অনেকের ওপর। তবে স্বাধীনতাপ্রত্যাশী এই সাংবাদিকদের অনেকেই সুযোগ পেলেই আভাসে-ইঙ্গিতে মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সংবাদপত্রে।
স্বাধীনতা-উত্তরকালে সত্তর দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল কিছুটা কম। তবে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অস্থিরতা ছিল ঠিকই। বিরোধী মতবাদ বিকশিত হওয়ার প্রবণতাও ছিল। সংবাদপত্রও তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। নানা আইন-কানুনের বেড়াজাল মোকাবিলা করে সংবাদপত্র নিজেকে শৃঙ্খল মুক্ত রাখতে চেয়েছে।
আশির দশকের রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্বাধীনতা-উত্তর যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আশির দশক ছিল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক আন্দোলনমুখর। প্রায় পুরো দশকই রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপুল গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল এই দশকের রাজনীতির প্রবণতা। দিনের পর দিন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ রাজপথে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। রাজনীতিতে জনসাধারণের ব্যাপক সক্রিয় অংশগ্রহণের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে নব্বইয়ের গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে।
পুরো সময়টাতেই সংবাদপত্র রাজনীতির সহযাত্রী ছিল। শুধু তাই না, এরশাদবিরোধী আন্দোলনে সংবাদপত্র এতটাই একাত্ম হয়েছিল যে ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে সংবাদপত্রে আন্দোলনের খবর প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ আরোপ করে সরকার। এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা এরশাদ পদত্যাগ না করা পর্যন্ত অবিরাম ধর্মঘট শুরু করেন। এর ফলে ২৮ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। একটানা আট দিন দেশে কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে এটি নজিরবিহীন ঘটনা।
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ বেশ কিছু আইন সংশোধন করা হয়। এতে সংবাদপত্র অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। দেশে ইলেট্রনিক মিডিয়ারও প্রসার ঘটতে থাকে। অনেক প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল চালু হয়। এই সব টেলিভিশন চ্যানেলে টকশো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। টকশোতে চলমান রাজনৈতিক ঘটনা ও বিষয় অগ্রাধিকার পায়। অনেক টকশোতে দর্শক-শ্রোতা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগও পায়।
ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের কারণে মুদ্রিত সংবাদপত্রের পাশাপাশি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এখন দেশের জনপ্রিয় গণমাধ্যম। মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলোও নিউজ পোর্টাল চালু করেছে। এই সব নিউজ পোর্টালের কনটেন্টের বিশাল অংশ জুড়েই থাকে রাজনৈতিক খবর ও তার বিশ্লেষণ। পাঠকের আগ্রহ বিবেচনা করেই সংবাদপত্র ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের বিশাল অংশ জুড়ে প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক খবর।
সন্দেহ নেই, গণমাধ্যম ও রাজনীতির ইতিহাস সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। গণমাধ্যম যুগ যুগ ধরে দেশের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল সবসময়, আছেও। সাম্প্রতিক সময়েও তার নজির দেখা গেছে।
আদিকাল থেকেই গণমাধ্যম ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহলের অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশকে গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষকে অবহিত করেছে। সচেতন করেছে। গণমাধ্যমই রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের উত্তাপ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। জনসম্পৃক্ততা তৈরি করেছে। দাবি আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেছে।
অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহল সবসময় নিজেদের অন্যায়-অবিচার আড়াল করতে চেয়েছে। অপতৎপরতা যেন ফাঁস না হয়, সে জন্য গণমাধ্যমের কণ্ঠ রোধ করতে চেয়েছে। এ জন্য নানা কৌশল ব্যবহার করেছে। কিন্তু গণমাধ্যম কোনো না কোনোভাবে সত্য প্রকাশ করেছে। দেশের মানুষকে তা অবহিত করেছে।
ঐতিহাসিকভাবেই গণমাধ্যম, রাজনীতি ও দেশের জনসাধারণ একই সূত্রে গাঁথা। এই তিনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলছে নিরন্তর। এই ত্রিমুখী মিথষ্ক্রিয়া হয়তো চলতেই থাকবে।
লেখক: সাংবাদিক ও গণমাধ্যম গবেষক; সাবেক পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
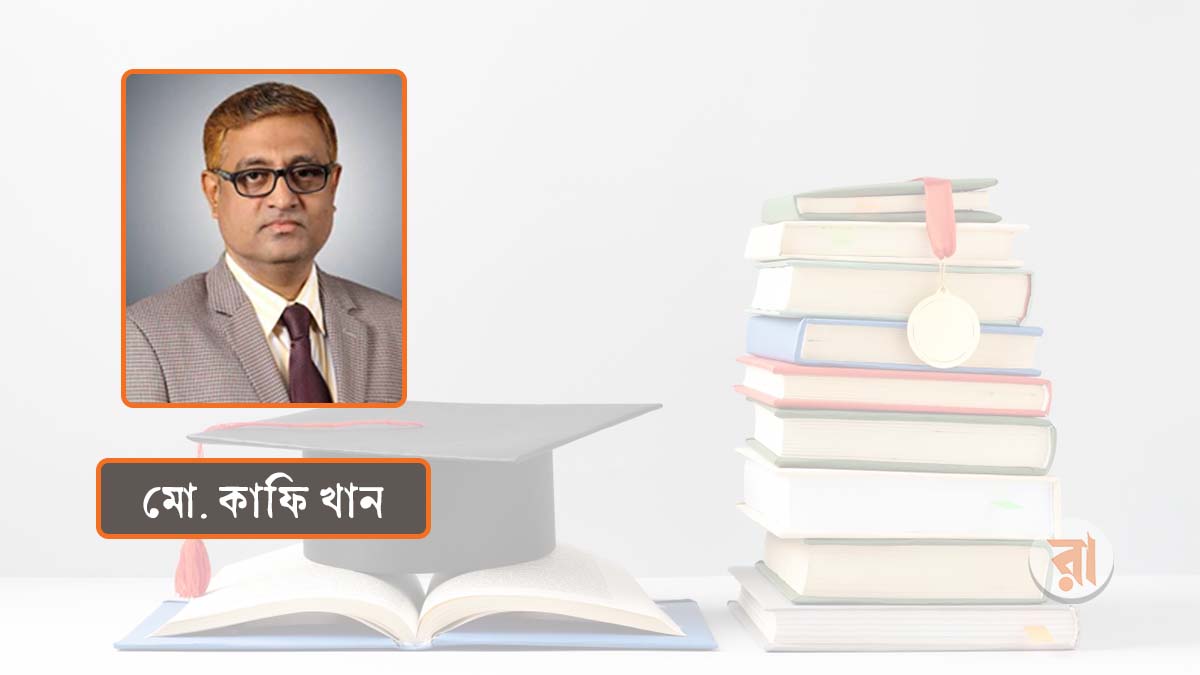
আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই একাডেমিক মেরিটোক্রেসিকে (বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি, মূল্যায়ন ও নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে শুধু যোগ্যতা ও কাজের মানের ভিত্তিতে, ব্যক্তিগত পরিচয়, রাজনৈতিক প্রভাব বা তদবিরের ভিত্তিতে নয়) যথাযথভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয় না।
৪ দিন আগে
একজন উপদেষ্টার কাছ থেকে আমরা আশা করি নীতিগত সততা, সংস্কারের সাহস এবং মেধাবীদের পাশে দাঁড়ানোর দৃঢ়তা। কিন্তু এখানে দেখা গেল উল্টো চিত্র— সংস্কারের প্রস্তাবকে শাস্তি দিয়ে দমন করা হলো। নীরবতা এখানে নিরপেক্ষতা নয়; নীরবতা এখানে পক্ষ নেওয়া। আর সেই পক্ষটি দুর্নীতির সুবিধাভোগীদের।
৫ দিন আগে
কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বা সংস্কার অনিবার্য। সেই সংস্কারের স্পিরিট বা চেতনা আমি এখন বিএনপির রাজনীতির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। তাই দেশের এ বাস্তবতায় জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র পুনর্প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বিএনপির সঙ্গেই পথ চলাকে আমি শ্রেয় মনে করেছি এবং যোগদানের সিদ্ধান
৫ দিন আগে
বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত থাকা সত্ত্বেও কক্সবাজার আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে এখনো পিছিয়ে। বছরে ৩০-৪০ লাখ দেশীয় পর্যটক এলেও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা নগণ্য। তুলনায় থাইল্যান্ড বছরে প্রায় চার কোটি বিদেশি পর্যটক থেকে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি আয় করে। আর মালদ্বীপ মাত্র ২০ লাখ পর্যটক থেকেই তার জিডিপ
৭ দিন আগে