
এ কে এম মাহফুজুর রহমান

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও চিকিৎসক সরবরাহের মধ্যে রয়েছে তীব্র বৈষম্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হাজারে চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ০.৬৭, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ২.৩ থেকে অনেক নিচে। প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ এমবিবিএস স্নাতক তৈরি হলেও মানগত ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ঘটছে না।
অনেক মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী–শিক্ষক অনুপাত ২০:১, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মানের দ্বিগুণ। ২০২৪ সালের বিএমঅ্যান্ডডিসি জরিপে দেখা যায়, ৩৫% বেসরকারি কলেজে মৌলিক বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। দুর্বল বেডসাইড প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ তত্ত্বাবধানের অভাবে নতুন ডাক্তাররা বাস্তব অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকেন।
প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকলেও নিয়োগ ও বণ্টনে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। ২০২৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৩,৫০০ নতুন পদ ও বিপিএসসি’র মাধ্যমে আরও ২,০০০ ডাক্তার নিয়োগের ঘোষণা দিলেও প্রশাসনিক জটিলতায় বহু পদ শূন্য রয়ে গেছে। নিয়োগে গড়ে ৪-৬ মাস বিলম্ব হয়। এতে নতুন ডাক্তাররা পোস্টিংয়ের অপেক্ষায় থাকেন, আর গ্রামীণ হাসপাতালগুলো চিকিৎসকশূন্য থেকে যায়। একইসঙ্গে, দক্ষ চিকিৎসকদের ঘনত্ব শহরে বাড়লেও গ্রামে তা মারাত্মকভাবে কম। জেলাস্তরের মাত্র ৪০% ডাক্তার গত বছর অনুমোদিত CME (Continuing Medical Education) প্রোগ্রামে অংশ নিতে পেরেছেন, ফলে গ্রামীণ চিকিৎসকরা আধুনিক জ্ঞানে পিছিয়ে থাকেন।
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যয়ের বড় বোঝা বহন করেন রোগীরাই। মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৩–৭৪% আসে সরাসরি রোগীর পকেট থেকে, যা বিশ্বে অন্যতম বেশি। বিপরীতে, সরকারি ব্যয় দাঁড়িয়েছে জিডিপির মাত্র ০.৭%, আর মাথাপিছু স্বাস্থ্য খরচ বছরে মাত্র ৩৫ মার্কিন ডলার, যার কেবল ২০% সরকার বহন করে।
২০২০ সালে পরিবারগুলো ওষুধে ব্যয় করেছে ৩৪,৪০০ কোটি টাকা (৬৫%) এবং ডায়াগনস্টিকে ব্যয় করেছে ৬,২৪০ কোটি টাকা (১১.৭%)। এর ফলে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ (জনসংখ্যার ৩.৭%) ২০২২ সালে চিকিৎসা খরচের কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে।
ডায়াগনস্টিক ও ওষুধ খাত প্রয়োজনীয় হলেও এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট। অনেক সময় ডাক্তাররা রোগী পাঠিয়ে ১০-৫০% কমিশন নেন, ফলে অতিরিক্ত পরীক্ষা করানো হয়। একটি পরিবার প্রায়ই ৭,৫০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত টেস্টে ব্যয় করে, যার প্রায় ৩০% অপ্রয়োজনীয়। ওষুধের অতি-প্রেসক্রিপশন ব্যয় আরও বাড়ায়, যেখানে রোগীর পকেট খরচের অর্ধেকেরও বেশি ওষুধে ব্যয় হয়।
২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শিশু রোগীদের ডায়াগনস্টিক খরচ আড়াই গুণ বেড়েছে। এই অতি-ব্যয় পরিবারকে আর্থিক চাপে ফেলছে এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা কমাচ্ছে।
চিকিৎসাক্ষেত্রে এই বাণিজ্যিক প্রভাব এক গভীর নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে ৬০% ডাক্তার কোনো না কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রচারণা বা সুবিধা গ্রহণ করেছেন। রোগীরা অভিযোগ করেন—চিকিৎসকেরা তাড়াহুড়ো করে দেখেন, অপ্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন দেন, আর ওষুধ কোম্পানির সাথে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেন না। এতে রোগীর মনে ধারণা তৈরি হচ্ছে যে ডাক্তাররা রোগীর স্বার্থ নয়, নিজেদের আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দেন।
এর ফলে অনেকেই আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা এড়িয়ে যান, চিকিৎসা বিলম্বিত করেন কিংবা ভেজাল বিকল্প চিকিৎসার দিকে ঝুঁকেন, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ।
তবে সব দিক অন্ধকার নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে চালু হয়েছে সিমুলেশন ল্যাব, কাঠামোবদ্ধ মেন্টরশিপ, Objective Structured Clinical Examination (OSCE) এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা।
এর ফলে লাইসেন্স পরীক্ষায় পাশের হার এখন ৯০% এর বেশি, প্রক্রিয়াগত দক্ষতা ৩০% বেড়েছে, আর রোগ নির্ণয়ের গতি বেড়েছে ২৫%। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, সঠিক বিনিয়োগ ও কাঠামোগত সংস্কার হলে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা বিশ্বমানের হতে পারে।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতকে টেকসই করতে এখন জরুরি সাহসী পদক্ষেপ। প্রথমত, Pharmaceutical Marketing Code হালনাগাদ ও কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। কমিশনভিত্তিক রেফারেল নিষিদ্ধ এবং ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন পর্যবেক্ষণ চালু করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ এলাকায় সেবা নিশ্চিত করতে পোস্টিংকে বাসস্থান, ভাতা ও পোস্টগ্রাজুয়েট সুযোগের সাথে যুক্ত করতে হবে। সবচেয়ে জরুরি হলো, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির ০.৭% থেকে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে কমপক্ষে ২% করতে হবে, এবং পকেট খরচ (OOP) ৭৪% থেকে নামিয়ে ৫০% এর নিচে আনতে হবে।
স্বচ্ছ নীতি, নৈতিক নেতৃত্ব ও আধুনিক প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ এমন এক প্রজন্মের ডাক্তার তৈরি করতে পারবে, যারা শুধু সংখ্যায় নয়, দক্ষতা, সততা ও মানবিকতার মাধ্যমে রোগীর আস্থা পুনর্গঠন করবে এবং সারাদেশে ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।
লেখক: উপ পরিচালক (ফ্যাকাল্টি এইচআর), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি

প্রায় ১৮ কোটি মানুষের দেশে স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা ও চিকিৎসক সরবরাহের মধ্যে রয়েছে তীব্র বৈষম্য। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি হাজারে চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ০.৬৭, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ২.৩ থেকে অনেক নিচে। প্রতিবছর প্রায় ১২,০০০ এমবিবিএস স্নাতক তৈরি হলেও মানগত ঘাটতির কারণে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি ঘটছে না।
অনেক মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী–শিক্ষক অনুপাত ২০:১, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত মানের দ্বিগুণ। ২০২৪ সালের বিএমঅ্যান্ডডিসি জরিপে দেখা যায়, ৩৫% বেসরকারি কলেজে মৌলিক বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। দুর্বল বেডসাইড প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্নশিপ তত্ত্বাবধানের অভাবে নতুন ডাক্তাররা বাস্তব অভিজ্ঞতায় পিছিয়ে থাকেন।
প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকলেও নিয়োগ ও বণ্টনে বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। ২০২৫ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৩,৫০০ নতুন পদ ও বিপিএসসি’র মাধ্যমে আরও ২,০০০ ডাক্তার নিয়োগের ঘোষণা দিলেও প্রশাসনিক জটিলতায় বহু পদ শূন্য রয়ে গেছে। নিয়োগে গড়ে ৪-৬ মাস বিলম্ব হয়। এতে নতুন ডাক্তাররা পোস্টিংয়ের অপেক্ষায় থাকেন, আর গ্রামীণ হাসপাতালগুলো চিকিৎসকশূন্য থেকে যায়। একইসঙ্গে, দক্ষ চিকিৎসকদের ঘনত্ব শহরে বাড়লেও গ্রামে তা মারাত্মকভাবে কম। জেলাস্তরের মাত্র ৪০% ডাক্তার গত বছর অনুমোদিত CME (Continuing Medical Education) প্রোগ্রামে অংশ নিতে পেরেছেন, ফলে গ্রামীণ চিকিৎসকরা আধুনিক জ্ঞানে পিছিয়ে থাকেন।
বাংলাদেশে স্বাস্থ্য ব্যয়ের বড় বোঝা বহন করেন রোগীরাই। মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের প্রায় ৭৩–৭৪% আসে সরাসরি রোগীর পকেট থেকে, যা বিশ্বে অন্যতম বেশি। বিপরীতে, সরকারি ব্যয় দাঁড়িয়েছে জিডিপির মাত্র ০.৭%, আর মাথাপিছু স্বাস্থ্য খরচ বছরে মাত্র ৩৫ মার্কিন ডলার, যার কেবল ২০% সরকার বহন করে।
২০২০ সালে পরিবারগুলো ওষুধে ব্যয় করেছে ৩৪,৪০০ কোটি টাকা (৬৫%) এবং ডায়াগনস্টিকে ব্যয় করেছে ৬,২৪০ কোটি টাকা (১১.৭%)। এর ফলে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ (জনসংখ্যার ৩.৭%) ২০২২ সালে চিকিৎসা খরচের কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে।
ডায়াগনস্টিক ও ওষুধ খাত প্রয়োজনীয় হলেও এ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক প্রবণতা ক্রমশ স্পষ্ট। অনেক সময় ডাক্তাররা রোগী পাঠিয়ে ১০-৫০% কমিশন নেন, ফলে অতিরিক্ত পরীক্ষা করানো হয়। একটি পরিবার প্রায়ই ৭,৫০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত টেস্টে ব্যয় করে, যার প্রায় ৩০% অপ্রয়োজনীয়। ওষুধের অতি-প্রেসক্রিপশন ব্যয় আরও বাড়ায়, যেখানে রোগীর পকেট খরচের অর্ধেকেরও বেশি ওষুধে ব্যয় হয়।
২০০৯ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে শিশু রোগীদের ডায়াগনস্টিক খরচ আড়াই গুণ বেড়েছে। এই অতি-ব্যয় পরিবারকে আর্থিক চাপে ফেলছে এবং স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা কমাচ্ছে।
চিকিৎসাক্ষেত্রে এই বাণিজ্যিক প্রভাব এক গভীর নৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। জরিপে দেখা যায়, গত এক বছরে ৬০% ডাক্তার কোনো না কোনো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির প্রচারণা বা সুবিধা গ্রহণ করেছেন। রোগীরা অভিযোগ করেন—চিকিৎসকেরা তাড়াহুড়ো করে দেখেন, অপ্রয়োজনীয় প্রেসক্রিপশন দেন, আর ওষুধ কোম্পানির সাথে সম্পর্ক প্রকাশ্যে আনেন না। এতে রোগীর মনে ধারণা তৈরি হচ্ছে যে ডাক্তাররা রোগীর স্বার্থ নয়, নিজেদের আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দেন।
এর ফলে অনেকেই আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা এড়িয়ে যান, চিকিৎসা বিলম্বিত করেন কিংবা ভেজাল বিকল্প চিকিৎসার দিকে ঝুঁকেন, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ।
তবে সব দিক অন্ধকার নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। সেখানে চালু হয়েছে সিমুলেশন ল্যাব, কাঠামোবদ্ধ মেন্টরশিপ, Objective Structured Clinical Examination (OSCE) এবং গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা।
এর ফলে লাইসেন্স পরীক্ষায় পাশের হার এখন ৯০% এর বেশি, প্রক্রিয়াগত দক্ষতা ৩০% বেড়েছে, আর রোগ নির্ণয়ের গতি বেড়েছে ২৫%। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে, সঠিক বিনিয়োগ ও কাঠামোগত সংস্কার হলে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষা বিশ্বমানের হতে পারে।
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতকে টেকসই করতে এখন জরুরি সাহসী পদক্ষেপ। প্রথমত, Pharmaceutical Marketing Code হালনাগাদ ও কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। কমিশনভিত্তিক রেফারেল নিষিদ্ধ এবং ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন পর্যবেক্ষণ চালু করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ এলাকায় সেবা নিশ্চিত করতে পোস্টিংকে বাসস্থান, ভাতা ও পোস্টগ্রাজুয়েট সুযোগের সাথে যুক্ত করতে হবে। সবচেয়ে জরুরি হলো, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যয় জিডিপির ০.৭% থেকে বাড়িয়ে ধীরে ধীরে কমপক্ষে ২% করতে হবে, এবং পকেট খরচ (OOP) ৭৪% থেকে নামিয়ে ৫০% এর নিচে আনতে হবে।
স্বচ্ছ নীতি, নৈতিক নেতৃত্ব ও আধুনিক প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ এমন এক প্রজন্মের ডাক্তার তৈরি করতে পারবে, যারা শুধু সংখ্যায় নয়, দক্ষতা, সততা ও মানবিকতার মাধ্যমে রোগীর আস্থা পুনর্গঠন করবে এবং সারাদেশে ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে।
লেখক: উপ পরিচালক (ফ্যাকাল্টি এইচআর), নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
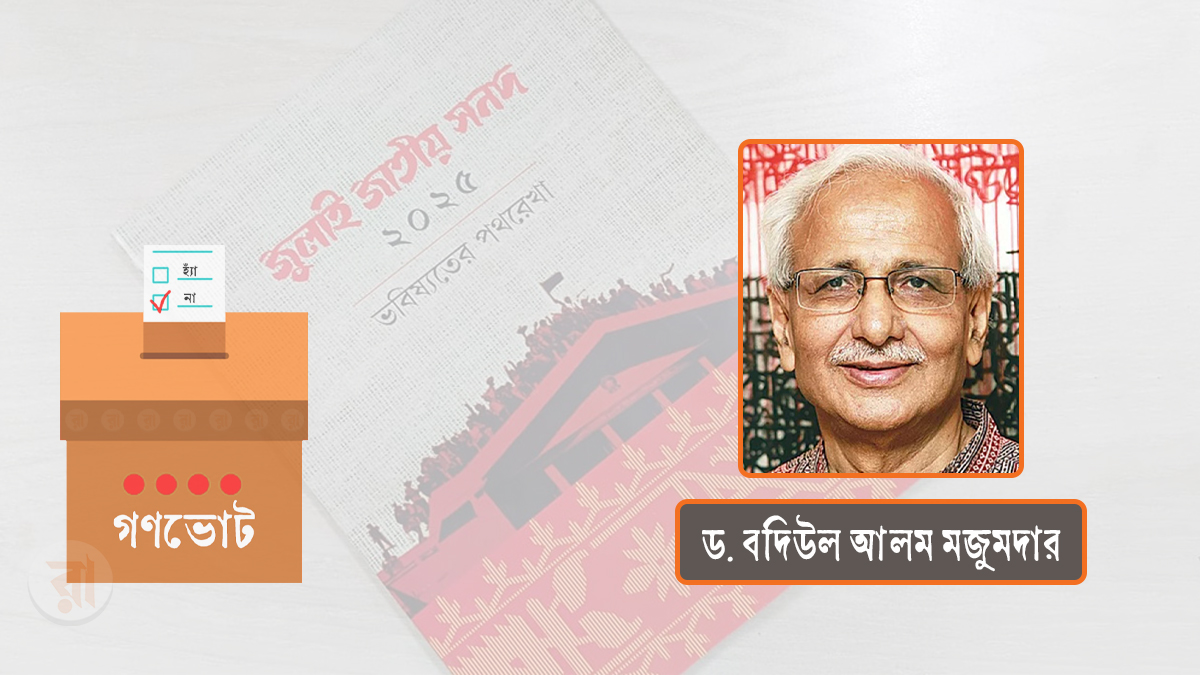
‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল, যাতে দেশে বিদ্যমান সক্রিয় প্রায় সব দল সই করেছে। যেহেতু সংবিধান হলো ‘উইল অব দ্য পিপল’ বা জনগণের চরম অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি, তাই জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে জনগণের সম্মতি বা গণভোট আয়ো
৫ দিন আগে
ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে যুক্ত থেকেও নিজেদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন অবস্থান নিয়েছে (European Council on Foreign Relations, ২০২৩)। এ অভিজ্ঞতা দেখায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কতটা জরুরি।
৫ দিন আগে
এই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকেই আসে ‘নতুন বাংলাদেশে’র ধারণা। এটি কোনো সাময়িক রাজনৈতিক স্লোগান নয়; এটি একটি নৈতিক অঙ্গীকার, একটি সামাজিক চুক্তি— যেখানে রাষ্ট্র হবে মানুষের সেবক, প্রভু নয়।
৬ দিন আগে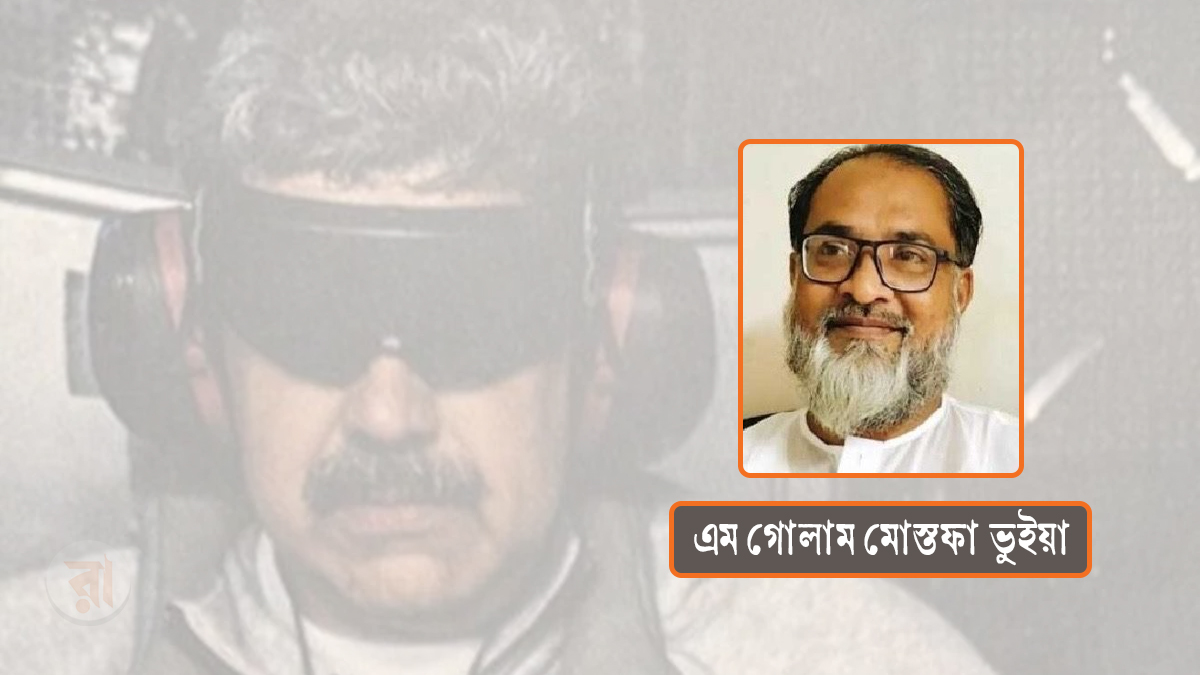
আন্তর্জাতিক আইনের কোনো তোয়াক্কা না করে, আইনকে পদদলিত করে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে গেছে, সেই দৃশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতিরই নগ্ন বহির্প্রকাশ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।
৭ দিন আগে