
মনিরুজ্জামান

ঢাকা জেলা ও মহানগরে মোট নির্বাচনী আসন ২০টি। এসব আসনে ১৫৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ১১। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে মোট ১৬টি আসন, সেখানে নারী প্রার্থী মাত্র একজন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এই তথ্যপ্রমাণ থেকে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান স্পষ্ট বোঝা যায়।
বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতিতে তারা পিছিয়ে পড়েছেন। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী হলেও রাজনীতির প্রতি নারীদের আগ্রহ তেমন বাড়েনি।
আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠতিব্য নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনে প্রার্থী এক হাজার ৮৯৫ জন। কিন্তু নারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র মাত্র ৯২, তাদের মধ্যে ২৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বিবেচনায় নিলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে ৭ দশমিক ৬০ শতাংশ ও বিরোধীদল জাতীয় পার্টি ৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ পদে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। আর স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর সংখ্যা ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করেছে।
অথচ রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব ৩৩ শতাংশ থাকার কথা। ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ে কমিটিতে নারী নেতৃত্ব ৩৩ শতাংশ করাসহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায় রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু বাধ্য-বাধকতার মেয়াদ ২০২০ সালে শেষ হলেও তখন পর্যন্ত দেশের নিবন্ধিত কোনও রাজনৈতিক দলই সেই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনও সময় আরও ১০ বছর বাড়িয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২’র সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধনী এনেছে। ২০২১ সালে নির্বাচন কমিশন ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে।
যদিও নির্বাচন কমিশন বলেছে, ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার শর্ত থাকলেও এটি বাধ্যবাধকতা নয়, তবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন উল্লেখ করে ইসি বলেছে, তারা এটা কারও ওপর চাপিয়ে দিতে চায় না।
সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের এই কথায় তুষ্ট নন। তারা বলছেন, আরপিওর (গণপ্রতিনিধিত্ব আইন) বিধান রাজনৈতিক দলগুলো মানে নি, নির্বাচন কমিশনও এটা মানার জন্য চাপ দেয়নি। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনেরও সদিচ্ছা নিয়ে তাদের প্রশ্ন রয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বরাবরই নারী সংগঠনগুলোর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল। তাদের প্রস্তাবনা ছিল সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকলেও এরা যেন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসেন—দলের হয়ে না। সেটাও কার্যকর হয়নি।
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নারীবান্ধব রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে থাকেন নারী নেত্রীরা। তাদের মতে, রাজনীতিতে শুধু কর্মী হিসেবে থাকলে হবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকা।
নারীদের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। সংসার ও সন্তান সামলানোর চাপ থাকে মূলত নারীর ওপর। তাছাড়া রাজনীতি করতে আজকাল পেশিশক্তি ও অর্থের দরকার হয়, সেখানেও নারীরা পিছিয়ে থাকে। আবার যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের ‘মহিলা সংগঠনের’ ভার দিয়ে ক্যারিয়ার আটকে দেওয়া হয়।
অনেক সময় দলের ভেতর থেকেই নারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হন। সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং ধর্মীয় রীতিও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের বড় অন্তরায়।
রাজনীতিতে নারীর এই অবস্থা দেখা গেলেও শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি রয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রকাশিত ‘মাস্টার কার্ড ইনডেক্স অব উইমেন অন্ট্রাপ্রেনারস’ (এমআইডব্লিউই) জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে উদ্যোক্তার ৩১ দশমিক ৬ শতাংশই নারী।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসের শেষে ব্যাংক খাতে মোট জনবলের ১৬ দশমিক ৩২ শতাংশ নারী।
সরকারি হিসেবে, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কয়েক বছর আগে লিঙ্গসমতা ফিরে এসেছে, এখন শিক্ষার এই দুটি স্তরে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। গত নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৮০ দশমিক ৫৭ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠিত না হলেও বেশ অগ্রগতি আছে।
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সেটি যত তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাবো ততই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হতে থাকবে। তবে নারী নেত্রীরা এও মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো সদিচ্ছার বিষয়টি যেমন আছে, তেমনি নারীদের এগিয়ে আসার ব্যাপারও কিন্তু আছে। সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নারীরা রাজনীতিতে জোরেসোরে এগিয়ে আসবেন, সেটিও প্রত্যাশা।

ঢাকা জেলা ও মহানগরে মোট নির্বাচনী আসন ২০টি। এসব আসনে ১৫৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ১১। বন্দরনগরী চট্টগ্রামে মোট ১৬টি আসন, সেখানে নারী প্রার্থী মাত্র একজন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা সব মিলিয়ে ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এই তথ্যপ্রমাণ থেকে রাজনীতিতে নারীর অবস্থান স্পষ্ট বোঝা যায়।
বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজনীতিতে তারা পিছিয়ে পড়েছেন। এমনকি দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী হলেও রাজনীতির প্রতি নারীদের আগ্রহ তেমন বাড়েনি।
আগামী ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠতিব্য নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনে প্রার্থী এক হাজার ৮৯৫ জন। কিন্তু নারী প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র মাত্র ৯২, তাদের মধ্যে ২৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বিবেচনায় নিলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগে ৭ দশমিক ৬০ শতাংশ ও বিরোধীদল জাতীয় পার্টি ৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ পদে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। আর স্বতন্ত্র নারী প্রার্থীর সংখ্যা ৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। বিএনপিসহ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করেছে।
অথচ রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব ৩৩ শতাংশ থাকার কথা। ২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলের সব পর্যায়ে কমিটিতে নারী নেতৃত্ব ৩৩ শতাংশ করাসহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি নিয়ে ২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন পায় রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু বাধ্য-বাধকতার মেয়াদ ২০২০ সালে শেষ হলেও তখন পর্যন্ত দেশের নিবন্ধিত কোনও রাজনৈতিক দলই সেই শর্ত পূরণ করতে পারেনি। নির্বাচন কমিশনও সময় আরও ১০ বছর বাড়িয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২’র সংশ্লিষ্ট ধারায় সংশোধনী এনেছে। ২০২১ সালে নির্বাচন কমিশন ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে।
যদিও নির্বাচন কমিশন বলেছে, ৩৩ শতাংশ নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করার শর্ত থাকলেও এটি বাধ্যবাধকতা নয়, তবে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এটা বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন উল্লেখ করে ইসি বলেছে, তারা এটা কারও ওপর চাপিয়ে দিতে চায় না।
সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা নির্বাচন কমিশনের এই কথায় তুষ্ট নন। তারা বলছেন, আরপিওর (গণপ্রতিনিধিত্ব আইন) বিধান রাজনৈতিক দলগুলো মানে নি, নির্বাচন কমিশনও এটা মানার জন্য চাপ দেয়নি। সেক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনেরও সদিচ্ছা নিয়ে তাদের প্রশ্ন রয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে বরাবরই নারী সংগঠনগুলোর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল। তাদের প্রস্তাবনা ছিল সংরক্ষিত মহিলা আসন থাকলেও এরা যেন সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে আসেন—দলের হয়ে না। সেটাও কার্যকর হয়নি।
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নারীবান্ধব রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে থাকেন নারী নেত্রীরা। তাদের মতে, রাজনীতিতে শুধু কর্মী হিসেবে থাকলে হবে না। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকা।
নারীদের রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে আরো কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে। সংসার ও সন্তান সামলানোর চাপ থাকে মূলত নারীর ওপর। তাছাড়া রাজনীতি করতে আজকাল পেশিশক্তি ও অর্থের দরকার হয়, সেখানেও নারীরা পিছিয়ে থাকে। আবার যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের ‘মহিলা সংগঠনের’ ভার দিয়ে ক্যারিয়ার আটকে দেওয়া হয়।
অনেক সময় দলের ভেতর থেকেই নারীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হন। সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা এবং ধর্মীয় রীতিও রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের বড় অন্তরায়।
রাজনীতিতে নারীর এই অবস্থা দেখা গেলেও শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে অগ্রগতি রয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে প্রকাশিত ‘মাস্টার কার্ড ইনডেক্স অব উইমেন অন্ট্রাপ্রেনারস’ (এমআইডব্লিউই) জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশে বর্তমানে উদ্যোক্তার ৩১ দশমিক ৬ শতাংশই নারী।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, চলতি বছরের জুন মাসের শেষে ব্যাংক খাতে মোট জনবলের ১৬ দশমিক ৩২ শতাংশ নারী।
সরকারি হিসেবে, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কয়েক বছর আগে লিঙ্গসমতা ফিরে এসেছে, এখন শিক্ষার এই দুটি স্তরে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। গত নভেম্বর মাসে প্রকাশিত এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৭৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী ছিল ৮০ দশমিক ৫৭ শতাংশ। উচ্চশিক্ষায় লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠিত না হলেও বেশ অগ্রগতি আছে।
রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সেটি যত তাড়াতাড়ি আমরা দেখতে পাবো ততই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ দৃশ্যমান হতে থাকবে। তবে নারী নেত্রীরা এও মনে করেন যে, রাজনৈতিক দলগুলো সদিচ্ছার বিষয়টি যেমন আছে, তেমনি নারীদের এগিয়ে আসার ব্যাপারও কিন্তু আছে। সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নারীরা রাজনীতিতে জোরেসোরে এগিয়ে আসবেন, সেটিও প্রত্যাশা।
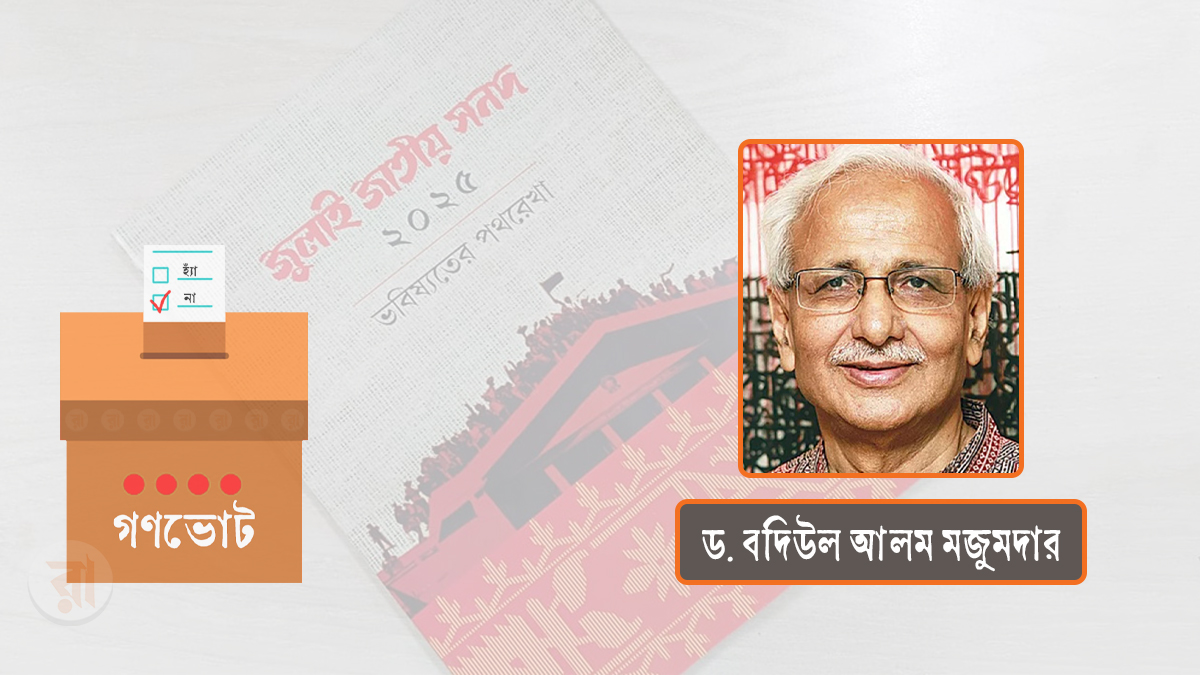
‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত একটি রাজনৈতিক সমঝোতার দলিল, যাতে দেশে বিদ্যমান সক্রিয় প্রায় সব দল সই করেছে। যেহেতু সংবিধান হলো ‘উইল অব দ্য পিপল’ বা জনগণের চরম অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি, তাই জুলাই সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবগুলো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে জনগণের সম্মতি বা গণভোট আয়ো
৫ দিন আগে
ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগে যুক্ত থেকেও নিজেদের রাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন অবস্থান নিয়েছে (European Council on Foreign Relations, ২০২৩)। এ অভিজ্ঞতা দেখায়, অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কতটা জরুরি।
৬ দিন আগে
এই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকেই আসে ‘নতুন বাংলাদেশে’র ধারণা। এটি কোনো সাময়িক রাজনৈতিক স্লোগান নয়; এটি একটি নৈতিক অঙ্গীকার, একটি সামাজিক চুক্তি— যেখানে রাষ্ট্র হবে মানুষের সেবক, প্রভু নয়।
৭ দিন আগে