
অরুণাভ বিশ্বাস

বাংলার প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে মহাস্থানগড়। আজকের দিনেও উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রত্ননগরীর ধ্বংসাবশেষ যেন আমাদের নিয়ে যায় হাজার বছর আগের ইতিহাসে। বলা হয়, মহাস্থানগড়ই হলো বাংলার প্রাচীনতম নগরী, যার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গড়ে ওঠে। এখানে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরীর রাজধানী ছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননকাজে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো থেকে জানা যায়, এটি ছিল এক সুসংগঠিত নগররাষ্ট্র, যেখানে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল বহু আগে থেকেই।
মহাস্থানগড়ের নামকরণের পেছনেও রয়েছে ইতিহাসের গন্ধ। "মহাস্থান" শব্দের অর্থ হলো মহৎ স্থান, আর "গড়" মানে দুর্গ। সত্যিই এটি ছিল এক শক্তিশালী দুর্গনগরী, যার চারদিকে উঁচু প্রাচীর ও প্রবেশপথ ছিল। নগরীর ভেতরে ছিল প্রাসাদ, প্রশাসনিক ভবন, ধর্মীয় স্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের বসবাসের জায়গা। এই নগরকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি ও লোককথা প্রচলিত আছে। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেন উনিশ শতকে।
১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম প্রথম মহাস্থানগড় পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, “এটি বাংলার প্রাচীন রাজধানীগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড একসঙ্গে বিকশিত হয়েছিল।” কানিংহ্যামের মতে, এই শহরটি কেবল বাংলার নয়, সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।
খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মউর্য সম্রাট অশোক এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠান। করতোয়া নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই নগরী তখন বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেরই মিলনস্থল হয়ে ওঠে। মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া ব্রাহ্মী লিপির শিলালিপি প্রমাণ করে যে, অশোক এখানে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম চালাতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই নগর ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন নগরায়ণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যঁ ফ্রাঁসোয়া শোয়ার (Jean François Sureau) মহাস্থানগড়ে খননকাজে অংশ নেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “এই নগরী ছিল সুপরিকল্পিত নগর রাষ্ট্রের নিদর্শন। এর প্রাচীর, রাস্তা ও জলাধারের কাঠামো দেখে বোঝা যায় যে, এখানে উন্নত প্রকৌশলবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছিল।” তাঁর মতে, মহাস্থানগড়ের সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের পতালিপুত্র বা তক্ষশীলার তুলনা টানা যায়।
গবেষকরা দেখিয়েছেন, মহাস্থানগড় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেছে। মউর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশ—প্রত্যেকেই তাদের শাসনকালে এই নগরকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাল যুগে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশাল বিকাশ ঘটে এখানে। একই সময়ে মহাস্থানগড়ে হিন্দু ধর্মেরও প্রবল প্রভাব ছিল। এ কারণে শহরটি ছিল এক বহুধর্মীয় মিলনকেন্দ্র।
ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ জন মার্শালও মহাস্থানগড় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “বাংলার অতীত বোঝার জন্য মহাস্থানগড় একটি অপরিহার্য স্থান। এর প্রতিটি ইট, প্রতিটি ভগ্নাবশেষ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।” তাঁর মতে, যদি নিয়মিত খননকাজ চালানো হয়, তবে মহাস্থানগড় থেকে আরও অনেক অমূল্য তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।
মহাস্থানগড়ের ভেতরে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রত্ননিদর্শন। মুদ্রা, মূর্তি, মৃৎপাত্র, শিলালিপি, এমনকি মানুষের ব্যবহৃত দৈনন্দিন জিনিসপত্রও এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে, শহরটি ছিল এক সমৃদ্ধ নগরী, যেখানে বাণিজ্য ও কৃষি দুটোই সমানতালে চলত। করতোয়া নদীর কারণে নদীপথে বাণিজ্য সহজ হয়েছিল।
ফরাসি ইতিহাসবিদ আন্দ্রে উইঙ্ক মন্তব্য করেছেন, “মহাস্থানগড় শুধু একটি শহর ছিল না, এটি ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানকার মানুষরা শিক্ষায়, শিল্পে ও আধ্যাত্মিকতায় অত্যন্ত উন্নত ছিল।” তাঁর মতে, মহাস্থানগড় দক্ষিণ এশিয়ার এক প্রাচীনতম শহর হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক গবেষণা ও খননকাজ চালানো হয়। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন স্থাপনা আবিষ্কার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধবিহার, হিন্দু মন্দির, মসজিদ এবং বিশাল জলাধারের ধ্বংসাবশেষ। এসব প্রমাণ করে, মহাস্থানগড় যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল।
আজ মহাস্থানগড়কে ঘিরে পর্যটন শিল্পও বিকশিত হয়েছে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে ভ্রমণে আসে। বিদেশি গবেষকরা নিয়মিত এখানে আসেন এবং নতুন তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও উঠেছে বহুবার।
তবে মহাস্থানগড় নিয়ে কিছু বিতর্কও রয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন, এটি ছিল প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরীর রাজধানী, আবার অনেকে বলেন এটি অন্য কোনো নগররাষ্ট্রের কেন্দ্র হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদই একমত যে, মহাস্থানগড় বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্থান।
আমেরিকান গবেষক জর্জ ফ্ল্যাশম্যান মন্তব্য করেছিলেন, “যদি মহাস্থানগড়ের মতো নগরী পশ্চিমা বিশ্বে পাওয়া যেত, তবে সেটিকে ঘিরে আজ হাজারো বই লেখা হতো। অথচ এশিয়ায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও আন্তর্জাতিকভাবে তা এখনো পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি।” তাঁর এই মন্তব্য আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, মহাস্থানগড়ের মতো ঐতিহাসিক নগরীকে আমরা কতটুকু মূল্য দিচ্ছি।
সবশেষে বলা যায়, মহাস্থানগড় কেবল একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়, এটি হলো বাংলার প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে আমরা দেখতে পাই হাজার বছরের ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের অনন্য মেলবন্ধন। মহাস্থানগড় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই মাটির ইতিহাস কত সমৃদ্ধ, আর সেই ইতিহাস রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।

বাংলার প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে মহাস্থানগড়। আজকের দিনেও উত্তরবঙ্গের বগুড়ায় করতোয়া নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা এই প্রত্ননগরীর ধ্বংসাবশেষ যেন আমাদের নিয়ে যায় হাজার বছর আগের ইতিহাসে। বলা হয়, মহাস্থানগড়ই হলো বাংলার প্রাচীনতম নগরী, যার ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গড়ে ওঠে। এখানে প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরীর রাজধানী ছিল বলে ধারণা করা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদদের খননকাজে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো থেকে জানা যায়, এটি ছিল এক সুসংগঠিত নগররাষ্ট্র, যেখানে বাণিজ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল বহু আগে থেকেই।
মহাস্থানগড়ের নামকরণের পেছনেও রয়েছে ইতিহাসের গন্ধ। "মহাস্থান" শব্দের অর্থ হলো মহৎ স্থান, আর "গড়" মানে দুর্গ। সত্যিই এটি ছিল এক শক্তিশালী দুর্গনগরী, যার চারদিকে উঁচু প্রাচীর ও প্রবেশপথ ছিল। নগরীর ভেতরে ছিল প্রাসাদ, প্রশাসনিক ভবন, ধর্মীয় স্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের বসবাসের জায়গা। এই নগরকে ঘিরে বহু কিংবদন্তি ও লোককথা প্রচলিত আছে। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেন উনিশ শতকে।
১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম প্রথম মহাস্থানগড় পরিদর্শন করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, “এটি বাংলার প্রাচীন রাজধানীগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড একসঙ্গে বিকশিত হয়েছিল।” কানিংহ্যামের মতে, এই শহরটি কেবল বাংলার নয়, সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।
খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মউর্য সম্রাট অশোক এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দূত পাঠান। করতোয়া নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই নগরী তখন বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ধর্মেরই মিলনস্থল হয়ে ওঠে। মহাস্থানগড় থেকে পাওয়া ব্রাহ্মী লিপির শিলালিপি প্রমাণ করে যে, অশোক এখানে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কার্যক্রম চালাতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন, এই নগর ছিল দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন নগরায়ণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।
বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যঁ ফ্রাঁসোয়া শোয়ার (Jean François Sureau) মহাস্থানগড়ে খননকাজে অংশ নেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “এই নগরী ছিল সুপরিকল্পিত নগর রাষ্ট্রের নিদর্শন। এর প্রাচীর, রাস্তা ও জলাধারের কাঠামো দেখে বোঝা যায় যে, এখানে উন্নত প্রকৌশলবিদ্যা প্রয়োগ করা হয়েছিল।” তাঁর মতে, মহাস্থানগড়ের সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের পতালিপুত্র বা তক্ষশীলার তুলনা টানা যায়।
গবেষকরা দেখিয়েছেন, মহাস্থানগড় দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে থেকেছে। মউর্য, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজবংশ—প্রত্যেকেই তাদের শাসনকালে এই নগরকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পাল যুগে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশাল বিকাশ ঘটে এখানে। একই সময়ে মহাস্থানগড়ে হিন্দু ধর্মেরও প্রবল প্রভাব ছিল। এ কারণে শহরটি ছিল এক বহুধর্মীয় মিলনকেন্দ্র।
ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ জন মার্শালও মহাস্থানগড় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “বাংলার অতীত বোঝার জন্য মহাস্থানগড় একটি অপরিহার্য স্থান। এর প্রতিটি ইট, প্রতিটি ভগ্নাবশেষ ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে।” তাঁর মতে, যদি নিয়মিত খননকাজ চালানো হয়, তবে মহাস্থানগড় থেকে আরও অনেক অমূল্য তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।
মহাস্থানগড়ের ভেতরে পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের প্রত্ননিদর্শন। মুদ্রা, মূর্তি, মৃৎপাত্র, শিলালিপি, এমনকি মানুষের ব্যবহৃত দৈনন্দিন জিনিসপত্রও এখানে উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলো প্রমাণ করে, শহরটি ছিল এক সমৃদ্ধ নগরী, যেখানে বাণিজ্য ও কৃষি দুটোই সমানতালে চলত। করতোয়া নদীর কারণে নদীপথে বাণিজ্য সহজ হয়েছিল।
ফরাসি ইতিহাসবিদ আন্দ্রে উইঙ্ক মন্তব্য করেছেন, “মহাস্থানগড় শুধু একটি শহর ছিল না, এটি ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানকার মানুষরা শিক্ষায়, শিল্পে ও আধ্যাত্মিকতায় অত্যন্ত উন্নত ছিল।” তাঁর মতে, মহাস্থানগড় দক্ষিণ এশিয়ার এক প্রাচীনতম শহর হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ।
বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে ব্যাপক গবেষণা ও খননকাজ চালানো হয়। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন স্থাপনা আবিষ্কার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধবিহার, হিন্দু মন্দির, মসজিদ এবং বিশাল জলাধারের ধ্বংসাবশেষ। এসব প্রমাণ করে, মহাস্থানগড় যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল।
আজ মহাস্থানগড়কে ঘিরে পর্যটন শিল্পও বিকশিত হয়েছে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে ভ্রমণে আসে। বিদেশি গবেষকরা নিয়মিত এখানে আসেন এবং নতুন তথ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও উঠেছে বহুবার।
তবে মহাস্থানগড় নিয়ে কিছু বিতর্কও রয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন, এটি ছিল প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন নগরীর রাজধানী, আবার অনেকে বলেন এটি অন্য কোনো নগররাষ্ট্রের কেন্দ্র হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদই একমত যে, মহাস্থানগড় বাংলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্থান।
আমেরিকান গবেষক জর্জ ফ্ল্যাশম্যান মন্তব্য করেছিলেন, “যদি মহাস্থানগড়ের মতো নগরী পশ্চিমা বিশ্বে পাওয়া যেত, তবে সেটিকে ঘিরে আজ হাজারো বই লেখা হতো। অথচ এশিয়ায় এর গুরুত্ব যথেষ্ট হলেও আন্তর্জাতিকভাবে তা এখনো পুরোপুরি স্বীকৃতি পায়নি।” তাঁর এই মন্তব্য আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে, মহাস্থানগড়ের মতো ঐতিহাসিক নগরীকে আমরা কতটুকু মূল্য দিচ্ছি।
সবশেষে বলা যায়, মহাস্থানগড় কেবল একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়, এটি হলো বাংলার প্রাচীন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে আমরা দেখতে পাই হাজার বছরের ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের অনন্য মেলবন্ধন। মহাস্থানগড় আমাদের মনে করিয়ে দেয়, এই মাটির ইতিহাস কত সমৃদ্ধ, আর সেই ইতিহাস রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার।

নুসরাত বলেন, ‘মানুষ ভাবে, নুসরাত মানেই বিতর্ক। কিন্তু আমি তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। যারা সমালোচনা করে, তারা জানেই না আমার ভিতরে কী চলছিল। অনেকে যা বলে, তার অনেকটাই সত্যি নয়, অর্ধসত্য।’
১ দিন আগে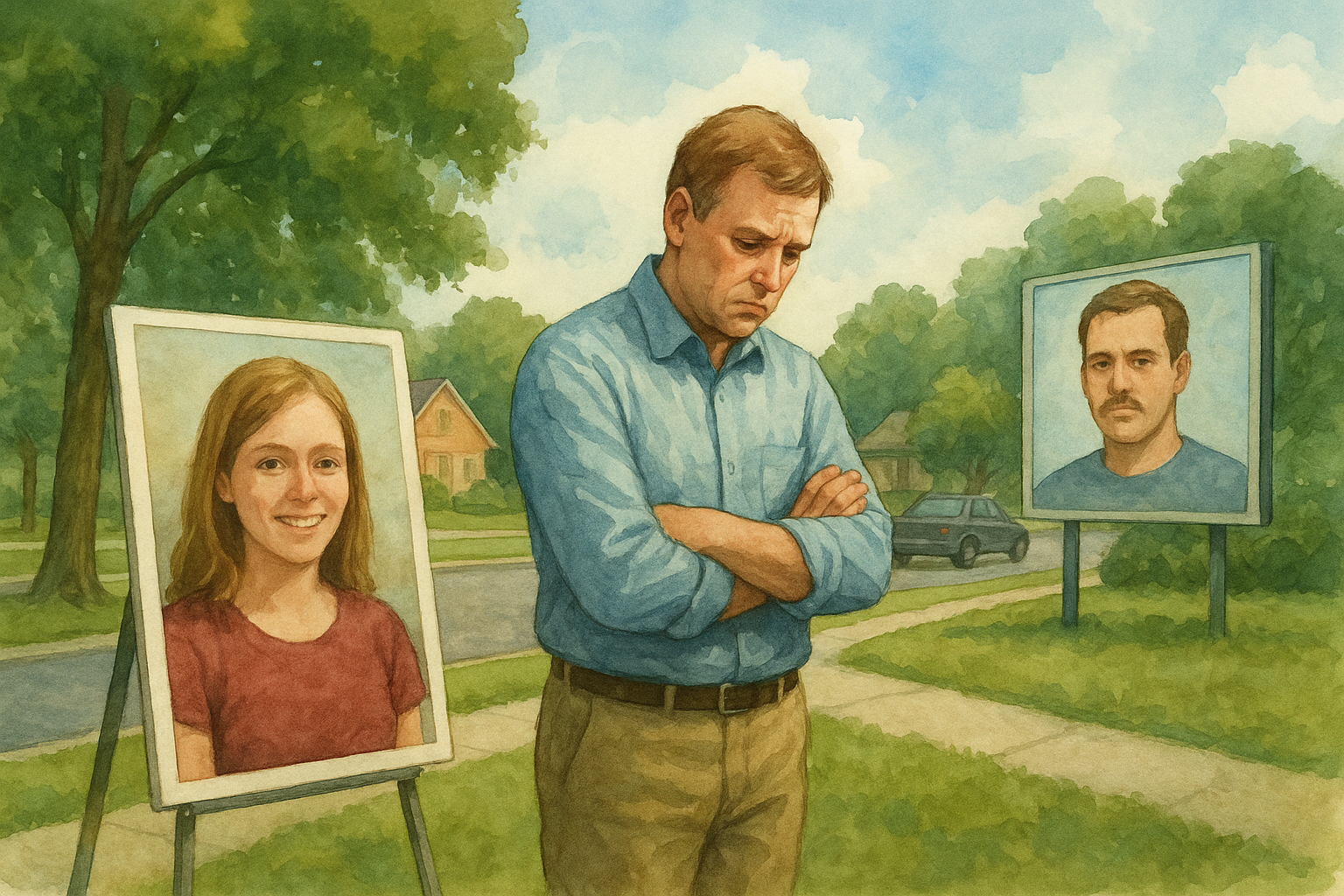
অ্যালি পড়ালেখার পাশাপাশি স্থানীয় এক সুইমিং পুলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। তার সঙ্গে ছোট ভাইও একই কাজ করত। বাসা থেকে হাঁটতে হাঁটতে তিন-চার মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায় সেখানে। ২০০২ সালের ১৮ জুনও প্রতিদিনের মতো কাজে গিয়েছিলেন অ্যালি। সেদিন আবহাওয়া ভালো ছিল না, তাই খুব বেশি লোক সাঁতার কাটতে আসেননি। ফলে কাজও
১ দিন আগে
কলকাতার মাটিতে জন্ম হলেও, তার হৃদয় ও আত্মা ছিল বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। শৈশব থেকেই জ্ঞানের প্রতি অদম্য তৃষ্ণা ও সমাজের প্রতি গভীর দায়বদ্ধতা তাঁকে এক অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রী হয়েও তিনি কেবল বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি; জ্ঞানের প্রতিটি শাখা
১ দিন আগে
সাধারণভাবে মাথা ব্যথাকে কয়েকটি ভাগে ফেলা হয়। যেমন টেনশন হেডেক, মাইগ্রেন, সাইনাসজনিত ব্যথা, কিংবা ক্লাস্টার হেডেক। তবে এর বাইরেও রয়েছে নানা ভৌতিক ও মানসিক কারণ, যা মানুষের মাথা ব্যথাকে অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়।
১ দিন আগে