
স ম গোলাম কিবরিয়া
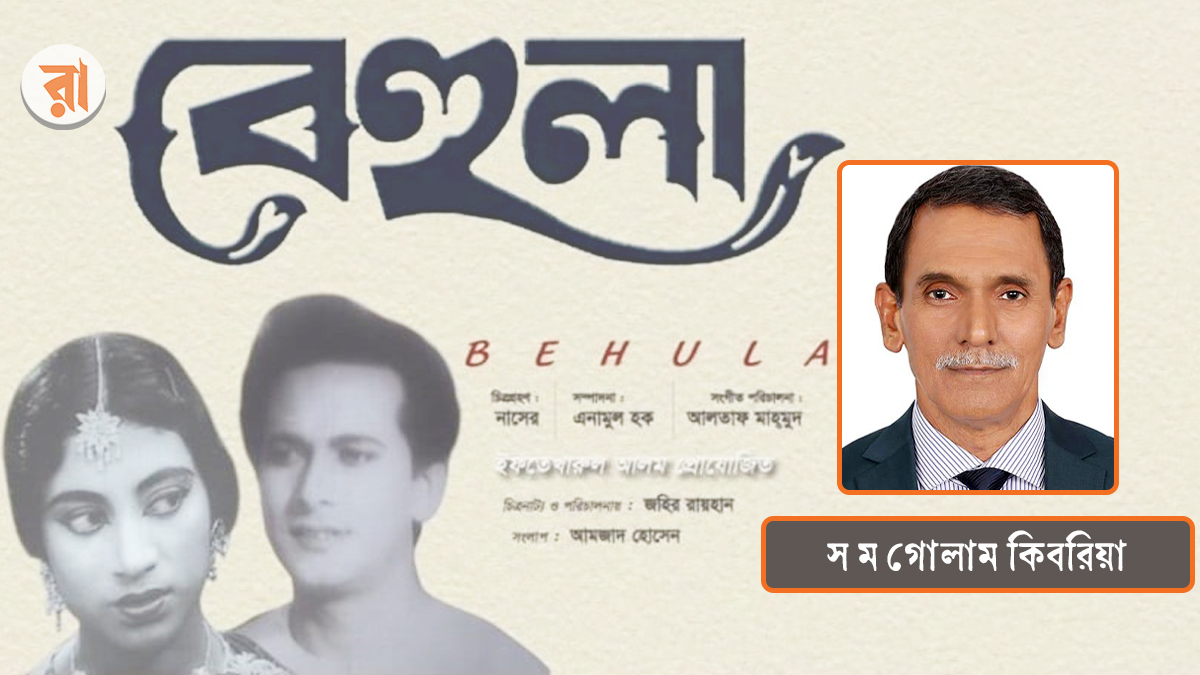
প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানের বেহুলা কি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র? নাকি বাংলা লোককাহিনী নির্ভর নিছক একটি বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র? চলচ্চিত্রটি ব্যাপক দর্শকের হৃদয় ছুঁয়েছিল, হয়েছিল দর্শকপ্রিয়।
বাঙালি সনাতন নারী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র বেহুলা। এ চরিত্রে বাঙালি রমণীর শাশ্বত পতিভক্তির অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গ সহনশীল ও কোমলস্বভাব নারীদের মধ্যেও যে একটি সুপ্ত বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল, তারও প্রকাশ ঘটেছে বেহুলা চরিত্রে। সব প্রলোভন, ভয় ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট জয় করে বাঙালি নারী জীবনের পরম সম্পদ পতি লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন বেহুলা। সাধারণভাবে বেহুলা চরিত্রে রাজনীতি দৃশ্যমান নয়।
বেহুলা চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। বছর কয়েক আগে পেশাগত কারণে সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামানের চলচ্চিত্র ক্যামেরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখতে যাই বসুন্ধরায়।
ব্যক্তিগত জীবনে স্থপতি রাশেদ জামান ভালো লাগা থেকেই সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে জড়িয়ে আছেন, হলিউডের চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শেখানোর জন্য ক্লাস নিয়েছেন অনেক দিন। বেহুলা চলচ্চিত্রের চিত্রধারণে ব্যবহার করা ক্যামেরাটি তার সংগ্রহে রয়েছে। তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেখতে পাই ক্যামেরাটি। সেই থেকেই বেহুলা চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার আগ্রহ।

বেহুলা চলচ্চিত্রের চিত্রায়নে ব্যবহৃত বিশেষ ক্যামেরা, যেটি সংরক্ষণে রেখেছেন সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামান। সেই ক্যামরার সঙ্গে লেখক স ম গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত
চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, চলচ্চিত্র অনন্য সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল। সমাজের বাস্তবতা, মানুষের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম চলচ্চিত্র শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে।
ইতিহাসের নানা বাঁক, শোষণ ও মুক্তির কাহিনি কিংবা রাজনৈতিক দর্শনও প্রতিফলিত হয় চলচ্চিত্রে। তাই সেই দর্শন সহজেই পৌঁছে যায় মানুষের কাছে। চলচ্চিত্র যেমন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। এ কারণেই বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রকে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম।
জহির রায়হানের ‘বেহুলা’ তেমনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। প্রচলিত লোককাহিনী ও হিন্দু পুরানকে ভিত্তি করে জহির রায়হান নির্মাণ করেছেন একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছিল দেশের সমকালীন রাজনীতির চালচিত্র। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ আর নিপীড়নের চিত্র রূপকভাবে তুল ধরেছেন তিনি।
‘বেহুলা’ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৬৬ সালে। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক জহির রায়হান নিজেই। সংলাপ রচনা করেছেন আমজাদ হোসেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন আলতাফ মাহমুদ। প্রযোজক ইফতেখারুল আলম।
১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। ১৯৫৬ সালে আন্দোলনের একধরনের নিষ্পত্তি হলেও শাসকদের কূটচাল শেষ হয় না। ১৯৪৮ সালে ভাষার ওপর আঘাত ছিল মূলত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াস। শাসকদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে সমাজসচেতন চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান বুঝে ছিলেন। আর সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই আশ্রয় নেন বাঙালি সংস্কৃতির লোককাহিনী মনসামঙ্গল কাব্য উপখ্যানের।
বাংলার প্রচলিত লোককাহিনী ও হিন্দু পুরাণ মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের ঘটনা প্রধান উপাখ্যান এই সিনেমার। মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য মনসামঙ্গল। এই আখ্যানটি আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে।
কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের ওপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগ। মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগে হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। বেহুলা-লখিন্দরের করুণ উপাখ্যানটি মানবিক আবেদনের কারণে আজও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়। আর এই জনপ্রিয় উপাখ্যানটিকে কেন্দ্র করে জহির রায়হান তুলে ধরেন সমকালীন রাষ্ট্রীয় অনাচার।
বেহুলা ময়ূর নাচ শেখে। মনসা দেবীর চোখে এটা অপরাধ। তাই সে বেহুলাকে অভিশাপ দেয়, যেন বাসর রাতেই বেহুলার সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়। কালনাগের বিষে প্রাণ হারায় বেহুলার স্বামী।
মনসা হলেন সাপের দেবী। স্বর্পকুলের সবাই মনসার হুকুম মেনে চলে। সাপের শত্রু ময়ূর, কারণ সাপকে খেয়ে ফেলে ময়ূর। মনসার দুই চোখের বিষ ময়ূর, তাই ময়ূর নাচ শেখাও অপরাধ। সেই ময়ূর নাচ শিখেছে কি না বেহুলা!
এদিকে চাঁদ সওদাগর মনসাকে ঘৃণা করেন। কারণ তাঁর পাঁচ পুত্র সাপের দংশনে প্রাণ হারায়। চাঁদ সওদাগরের শেষ পুত্র লখিন্দর। সে ময়ূর পোষে। সাই সওদাগরের কন্যা বেহুলার বিয়ে হবে লখিন্দরের সাথে। লখিন্দরই বেহুলকে ময়ূর নাচ শেখায়।
সাই সওদাগর মনসা দেবীর পূজ করে। তার রাজ্যের সবাই মনসা দেবীর ভক্ত। লখিন্দর একদিন ময়ূর নিয়ে সাই সওদাগরের রাজ্যে আসে। তাকে ময়ূর নিয়ে প্রবেশে করতে দেখে সবাই অবাক হয়। লখিন্দরের সঙ্গে আনা ময়ুর একটি সাপকে মেরেও ফেলে।
এ খবর সাই সওদাগরের কানে যায়। স্বর্গের মনসা দেবীর কাছেও এ খবর পৌঁছে যায়। তখন সাই সওদাগর লখিন্দরকে দরবারে ডেকে আনে। সাইদাগর লাখিন্দরকে জানায় তার রাজ্যে সাপ হত্যা মহাঅন্যায়, ময়ুর পোষা নিষিদ্ধ।
এদিকে চাঁদ সওদাগর ও সাই সওদাগর দুজন পুরনো বন্ধু। অনেক আগেই লখিন্দরের সঙ্গে সাই সওদাগরের একমাত্র আদরের কন্যা বেহুলার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে। সাই সওদাগর যখন জানতে পারেন, লখিন্দর তার বন্ধু চাঁদ সওদাগরের ছেলে তখন লখিন্দরকে ক্ষমা করে দেয়।
কিন্তু মনসা দেবী কোনোভাবেই এই বিয়ে হতে দিতে চায় না। কূটচাল চেলে সে বেহুলা অসতী বলে অভিযোগ আনে। অভিযোগ প্রমাণ করতে এবং অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কথা বলে মনসা দেবী মধ্যরাতে বেহুলাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে অমৃত সুধার বদলে বেহুলার মুখে সুরা ঢেলে দেয়। সুরা পান করে রাতভর শ্মশান ঘাটে পড়ে থাকে বেহুলা। অগ্নিপরীক্ষায় বিজয় হয় বেহুলার। সিদ্ধান্ত হয়— বিয়ে হবে বেহুলা-লখিন্দরের।
লখিন্দরকে সাপের দংশন থেকে রক্ষা করতে চাঁদ সওদাগর লোহা দিয়ে তাদের বাসরঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে কোনো ছিদ্র থাকবে না। সেভাবেই তৈরি করা হয় বাসরঘর, যেন সূঁচ প্রবেশ করার মতো ছিদ্রও না থাকে। তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ধোঁয়া দিয়ে পরীক্ষাও করা হয় সেই লোহার বাসরঘর।
কিন্তু মনসার কূটচাল থেমে থাকে না। বাসরঘরের কারিগরকে নির্বংশ করার ভয় দেখায় মনসা। ভয়ে পেয়ে কারিগর বিয়ের আগের দিন গোপনে লোহার ঘরে ছিদ্র করে দেয়। সেই ছিদ্র দিয়ে কালনাগ লোহার বাসরঘরে ঢুকে পড়ে।
বিয়ের পর বাসর ঘরে লখিন্দর ঘুমিয়ে আছে, বেহুলা আছে পাহারায়। হঠাৎ কালনাগ দেখতে পেয়ে বেহুলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। লখিন্দরকে দংশন করে দ্রুতই কালনাগ পালিয়ে যায়। চাঁদ সওদাগর তার শেষ সন্তান লখিন্দরকেও হারায়, আর বেহুলা হারায় স্বামী। স্বৈরিণী মনসা স্বর্গে বসে বিজয়ের হাসি হাসে।
কলনাগের দংশনে মৃত লখিন্দরকে কলার ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আশা— জলের গুণে যদি বিষ কেটে যায়, যদি লখিন্দর ফিরে পায় প্রাণ! বেহুলাও আশা ছাড়ে না। সেও ভেলায় করে লখিন্দরকে নিয়ে নদীর জলে ভাসতে থাকে। একসময় লখিন্দর পচে-গলে যায়, শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকে ভেলায়।
ওদিকে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রপুরীর এক নারীর সহায়তায় বেহুলা স্বর্গে দেবরাজের দরবারে হাজির হয়। তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে দংশনের জন্য ইন্দ্ররাজের কাছে বিচার চায়। ঘটনার বিবরণ শুনে দেবতারা বেহুলার প্রতি রুষ্ট হয়। জানতে চায়— কেন তারা মনসার পুজো করে না?
বেহুলা ইন্দ্রের সামনেই সাফ জবাব দেয়, পুজো কি জোর করে পাওয়া যায়? কেউ যদি ভালো না বাসে, তখন কি জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায়? পুজো না পেলেই কি তার ক্ষতি করতে হবে? এ কেমন দেবী?
ইন্দ্রপুরীর দেবতারা শর্তসাপেক্ষে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। শর্ত দেওয়া হয়, বেহুলা দেবতাদের মন জয় করতে পারলে ফেরত পাবে স্বামীর প্রাণ। ইন্দ্রপুরির দেবতাদের দেওয়া শর্তে বেহুলা রাজি হয়। যে নাচের কারণে স্বামীর প্রাণ নিয়েছে মনসা, লখিন্দরের শেখানো সেই ময়ূর নাচ শুরু করে।
শেষ পর্যন্ত ময়ূর নাচে বেহুলা জয় করে নেয় ইন্দ্রপুরীর দেবতাদের মন। ফিরিয়ে আনে লখিন্দরের প্রাণ। এভাবেই এগিয়ে যায় চলচ্চিত্রের কাহিনী। আর মনসা দেবী, লখিন্দর, বেহুলাকে চলচ্চিত্রকার তুলে ধরেন রাজনৈতিক আবরণে।
বাংলা চলচ্চিত্রের অসাধারণ কীর্তি বেহুলা, একটি অনন্য রূপক চলচ্চিত্র বেহুলা। স্বৈরাশাসক আয়ুব খানের শাসনামলে নির্মিত চলচ্চিত্রটিতে নিষ্ঠুর মনসা দেবীকে তুলে ধরা হয়েছে সামরিক একনায়কের প্রতীক রূপে।
সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা কূটকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সবাইকে তার অনুগত করে তোলার চেষ্টা চালান। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের অনুগত না হলেই তার ওপর নেমে আসত নির্যাতন ও প্রাণনাশ।
বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় নিষিদ্ধ হয় রবীন্দ্রসংগীত, বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় অলিখিত বিধিনিষেধ চলতে থাকে। জহির রায়হান এই চলচ্চিত্রে মনসা দেবী চরিত্রটি স্বৈরশাসকের প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, যিনি পূজা না পেলে বা আনুগত্য না মানলে প্রাণ কেড়ে নেন।
বেহুলা নাচ শেখার কারণে পতি হারায়। এই নাচ শেখা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার প্রতীক, যা আইয়ুবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা। যে ময়ূর নাচ শেখার কারণে বেহুলার পতি প্রাণ হারায়, সেই নাচই পতির প্রাণ ফিরে পাওয়ার শক্তি হয়ে ওঠে, যেন সাংস্কৃতিক চর্চাই বাঙালি ফিরে পায় মুক্তির দিশারী রূপে। শেষ পর্যন্ত সেই নাচেই মিলে মুক্তি, জয়ী হয় প্রতিরোধ।
নায়ক হিসেবে রাজ্জাকের প্রথম চলচ্চিত্র বেহুলা। এতে বেহুলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুচন্দা। লোককাহিনীভিত্তিক হলেও ছবিতে ফুটে ওঠে নারীর চিরন্তন আবেগ, আত্মত্যাগ ও অদম্য ভালোবাসা।
বেহুলা তাই কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়। এটি বাংলা সংস্কৃতির, নারীর আত্মত্যাগ এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক কালজয়ী দলিল।
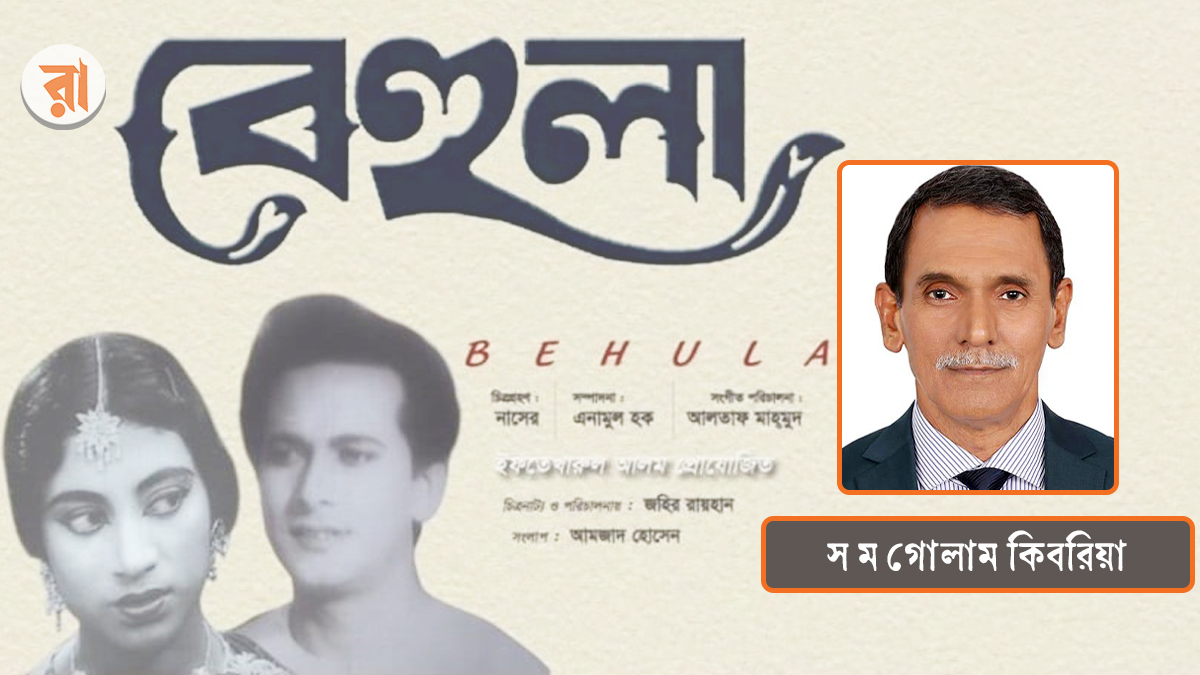
প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানের বেহুলা কি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র? নাকি বাংলা লোককাহিনী নির্ভর নিছক একটি বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র? চলচ্চিত্রটি ব্যাপক দর্শকের হৃদয় ছুঁয়েছিল, হয়েছিল দর্শকপ্রিয়।
বাঙালি সনাতন নারী সমাজের অন্যতম আদর্শ চরিত্র বেহুলা। এ চরিত্রে বাঙালি রমণীর শাশ্বত পতিভক্তির অসাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। একইসঙ্গ সহনশীল ও কোমলস্বভাব নারীদের মধ্যেও যে একটি সুপ্ত বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল, তারও প্রকাশ ঘটেছে বেহুলা চরিত্রে। সব প্রলোভন, ভয় ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট জয় করে বাঙালি নারী জীবনের পরম সম্পদ পতি লখিন্দরকে বাঁচিয়ে তোলেন বেহুলা। সাধারণভাবে বেহুলা চরিত্রে রাজনীতি দৃশ্যমান নয়।
বেহুলা চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার পেছনে একটা কারণ রয়েছে। বছর কয়েক আগে পেশাগত কারণে সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামানের চলচ্চিত্র ক্যামেরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেখতে যাই বসুন্ধরায়।
ব্যক্তিগত জীবনে স্থপতি রাশেদ জামান ভালো লাগা থেকেই সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে জড়িয়ে আছেন, হলিউডের চলচ্চিত্রেও কাজ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শেখানোর জন্য ক্লাস নিয়েছেন অনেক দিন। বেহুলা চলচ্চিত্রের চিত্রধারণে ব্যবহার করা ক্যামেরাটি তার সংগ্রহে রয়েছে। তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দেখতে পাই ক্যামেরাটি। সেই থেকেই বেহুলা চলচ্চিত্র নিয়ে লেখার আগ্রহ।

বেহুলা চলচ্চিত্রের চিত্রায়নে ব্যবহৃত বিশেষ ক্যামেরা, যেটি সংরক্ষণে রেখেছেন সিনেমাটোগ্রাফার রাশেদ জামান। সেই ক্যামরার সঙ্গে লেখক স ম গোলাম কিবরিয়া। ছবি: সংগৃহীত
চলচ্চিত্র শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, চলচ্চিত্র অনন্য সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক দলিল। সমাজের বাস্তবতা, মানুষের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-সংগ্রাম চলচ্চিত্র শক্তিশালীভাবে তুলে ধরে।
ইতিহাসের নানা বাঁক, শোষণ ও মুক্তির কাহিনি কিংবা রাজনৈতিক দর্শনও প্রতিফলিত হয় চলচ্চিত্রে। তাই সেই দর্শন সহজেই পৌঁছে যায় মানুষের কাছে। চলচ্চিত্র যেমন জীবনের প্রতিচ্ছবি, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। এ কারণেই বিশ্বজুড়ে চলচ্চিত্রকে বলা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম।
জহির রায়হানের ‘বেহুলা’ তেমনি একটি অনবদ্য সৃষ্টি। প্রচলিত লোককাহিনী ও হিন্দু পুরানকে ভিত্তি করে জহির রায়হান নির্মাণ করেছেন একটি রাজনৈতিক চলচ্চিত্র। এই চলচ্চিত্রে ফুটে উঠেছিল দেশের সমকালীন রাজনীতির চালচিত্র। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ আর নিপীড়নের চিত্র রূপকভাবে তুল ধরেছেন তিনি।
‘বেহুলা’ চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ১৯৬৬ সালে। এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক জহির রায়হান নিজেই। সংলাপ রচনা করেছেন আমজাদ হোসেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন আলতাফ মাহমুদ। প্রযোজক ইফতেখারুল আলম।
১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। ১৯৫৬ সালে আন্দোলনের একধরনের নিষ্পত্তি হলেও শাসকদের কূটচাল শেষ হয় না। ১৯৪৮ সালে ভাষার ওপর আঘাত ছিল মূলত বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার প্রয়াস। শাসকদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে সমাজসচেতন চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান বুঝে ছিলেন। আর সেই বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই আশ্রয় নেন বাঙালি সংস্কৃতির লোককাহিনী মনসামঙ্গল কাব্য উপখ্যানের।
বাংলার প্রচলিত লোককাহিনী ও হিন্দু পুরাণ মনসামঙ্গল কাব্যের বেহুলা-লখিন্দরের ঘটনা প্রধান উপাখ্যান এই সিনেমার। মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য মনসামঙ্গল। এই আখ্যানটি আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে।
কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের ওপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগ। মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগে হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। বেহুলা-লখিন্দরের করুণ উপাখ্যানটি মানবিক আবেদনের কারণে আজও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়। আর এই জনপ্রিয় উপাখ্যানটিকে কেন্দ্র করে জহির রায়হান তুলে ধরেন সমকালীন রাষ্ট্রীয় অনাচার।
বেহুলা ময়ূর নাচ শেখে। মনসা দেবীর চোখে এটা অপরাধ। তাই সে বেহুলাকে অভিশাপ দেয়, যেন বাসর রাতেই বেহুলার সিঁথির সিঁদুর মুছে যায়। কালনাগের বিষে প্রাণ হারায় বেহুলার স্বামী।
মনসা হলেন সাপের দেবী। স্বর্পকুলের সবাই মনসার হুকুম মেনে চলে। সাপের শত্রু ময়ূর, কারণ সাপকে খেয়ে ফেলে ময়ূর। মনসার দুই চোখের বিষ ময়ূর, তাই ময়ূর নাচ শেখাও অপরাধ। সেই ময়ূর নাচ শিখেছে কি না বেহুলা!
এদিকে চাঁদ সওদাগর মনসাকে ঘৃণা করেন। কারণ তাঁর পাঁচ পুত্র সাপের দংশনে প্রাণ হারায়। চাঁদ সওদাগরের শেষ পুত্র লখিন্দর। সে ময়ূর পোষে। সাই সওদাগরের কন্যা বেহুলার বিয়ে হবে লখিন্দরের সাথে। লখিন্দরই বেহুলকে ময়ূর নাচ শেখায়।
সাই সওদাগর মনসা দেবীর পূজ করে। তার রাজ্যের সবাই মনসা দেবীর ভক্ত। লখিন্দর একদিন ময়ূর নিয়ে সাই সওদাগরের রাজ্যে আসে। তাকে ময়ূর নিয়ে প্রবেশে করতে দেখে সবাই অবাক হয়। লখিন্দরের সঙ্গে আনা ময়ুর একটি সাপকে মেরেও ফেলে।
এ খবর সাই সওদাগরের কানে যায়। স্বর্গের মনসা দেবীর কাছেও এ খবর পৌঁছে যায়। তখন সাই সওদাগর লখিন্দরকে দরবারে ডেকে আনে। সাইদাগর লাখিন্দরকে জানায় তার রাজ্যে সাপ হত্যা মহাঅন্যায়, ময়ুর পোষা নিষিদ্ধ।
এদিকে চাঁদ সওদাগর ও সাই সওদাগর দুজন পুরনো বন্ধু। অনেক আগেই লখিন্দরের সঙ্গে সাই সওদাগরের একমাত্র আদরের কন্যা বেহুলার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে। সাই সওদাগর যখন জানতে পারেন, লখিন্দর তার বন্ধু চাঁদ সওদাগরের ছেলে তখন লখিন্দরকে ক্ষমা করে দেয়।
কিন্তু মনসা দেবী কোনোভাবেই এই বিয়ে হতে দিতে চায় না। কূটচাল চেলে সে বেহুলা অসতী বলে অভিযোগ আনে। অভিযোগ প্রমাণ করতে এবং অভিশাপ থেকে মুক্ত করার কথা বলে মনসা দেবী মধ্যরাতে বেহুলাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে অমৃত সুধার বদলে বেহুলার মুখে সুরা ঢেলে দেয়। সুরা পান করে রাতভর শ্মশান ঘাটে পড়ে থাকে বেহুলা। অগ্নিপরীক্ষায় বিজয় হয় বেহুলার। সিদ্ধান্ত হয়— বিয়ে হবে বেহুলা-লখিন্দরের।
লখিন্দরকে সাপের দংশন থেকে রক্ষা করতে চাঁদ সওদাগর লোহা দিয়ে তাদের বাসরঘর তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে কোনো ছিদ্র থাকবে না। সেভাবেই তৈরি করা হয় বাসরঘর, যেন সূঁচ প্রবেশ করার মতো ছিদ্রও না থাকে। তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ধোঁয়া দিয়ে পরীক্ষাও করা হয় সেই লোহার বাসরঘর।
কিন্তু মনসার কূটচাল থেমে থাকে না। বাসরঘরের কারিগরকে নির্বংশ করার ভয় দেখায় মনসা। ভয়ে পেয়ে কারিগর বিয়ের আগের দিন গোপনে লোহার ঘরে ছিদ্র করে দেয়। সেই ছিদ্র দিয়ে কালনাগ লোহার বাসরঘরে ঢুকে পড়ে।
বিয়ের পর বাসর ঘরে লখিন্দর ঘুমিয়ে আছে, বেহুলা আছে পাহারায়। হঠাৎ কালনাগ দেখতে পেয়ে বেহুলার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। লখিন্দরকে দংশন করে দ্রুতই কালনাগ পালিয়ে যায়। চাঁদ সওদাগর তার শেষ সন্তান লখিন্দরকেও হারায়, আর বেহুলা হারায় স্বামী। স্বৈরিণী মনসা স্বর্গে বসে বিজয়ের হাসি হাসে।
কলনাগের দংশনে মৃত লখিন্দরকে কলার ভেলায় করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আশা— জলের গুণে যদি বিষ কেটে যায়, যদি লখিন্দর ফিরে পায় প্রাণ! বেহুলাও আশা ছাড়ে না। সেও ভেলায় করে লখিন্দরকে নিয়ে নদীর জলে ভাসতে থাকে। একসময় লখিন্দর পচে-গলে যায়, শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকে ভেলায়।
ওদিকে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্রপুরীর এক নারীর সহায়তায় বেহুলা স্বর্গে দেবরাজের দরবারে হাজির হয়। তার স্বামীকে অন্যায়ভাবে দংশনের জন্য ইন্দ্ররাজের কাছে বিচার চায়। ঘটনার বিবরণ শুনে দেবতারা বেহুলার প্রতি রুষ্ট হয়। জানতে চায়— কেন তারা মনসার পুজো করে না?
বেহুলা ইন্দ্রের সামনেই সাফ জবাব দেয়, পুজো কি জোর করে পাওয়া যায়? কেউ যদি ভালো না বাসে, তখন কি জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায়? পুজো না পেলেই কি তার ক্ষতি করতে হবে? এ কেমন দেবী?
ইন্দ্রপুরীর দেবতারা শর্তসাপেক্ষে লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে রাজি হয়। শর্ত দেওয়া হয়, বেহুলা দেবতাদের মন জয় করতে পারলে ফেরত পাবে স্বামীর প্রাণ। ইন্দ্রপুরির দেবতাদের দেওয়া শর্তে বেহুলা রাজি হয়। যে নাচের কারণে স্বামীর প্রাণ নিয়েছে মনসা, লখিন্দরের শেখানো সেই ময়ূর নাচ শুরু করে।
শেষ পর্যন্ত ময়ূর নাচে বেহুলা জয় করে নেয় ইন্দ্রপুরীর দেবতাদের মন। ফিরিয়ে আনে লখিন্দরের প্রাণ। এভাবেই এগিয়ে যায় চলচ্চিত্রের কাহিনী। আর মনসা দেবী, লখিন্দর, বেহুলাকে চলচ্চিত্রকার তুলে ধরেন রাজনৈতিক আবরণে।
বাংলা চলচ্চিত্রের অসাধারণ কীর্তি বেহুলা, একটি অনন্য রূপক চলচ্চিত্র বেহুলা। স্বৈরাশাসক আয়ুব খানের শাসনামলে নির্মিত চলচ্চিত্রটিতে নিষ্ঠুর মনসা দেবীকে তুলে ধরা হয়েছে সামরিক একনায়কের প্রতীক রূপে।
সামরিক শাসন জারি করে আইয়ুব খান দেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ ও বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের নানা কূটকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সবাইকে তার অনুগত করে তোলার চেষ্টা চালান। স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের অনুগত না হলেই তার ওপর নেমে আসত নির্যাতন ও প্রাণনাশ।
বাঙালি সংস্কৃতি ধ্বংসের চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় নিষিদ্ধ হয় রবীন্দ্রসংগীত, বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় অলিখিত বিধিনিষেধ চলতে থাকে। জহির রায়হান এই চলচ্চিত্রে মনসা দেবী চরিত্রটি স্বৈরশাসকের প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন, যিনি পূজা না পেলে বা আনুগত্য না মানলে প্রাণ কেড়ে নেন।
বেহুলা নাচ শেখার কারণে পতি হারায়। এই নাচ শেখা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার প্রতীক, যা আইয়ুবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা। যে ময়ূর নাচ শেখার কারণে বেহুলার পতি প্রাণ হারায়, সেই নাচই পতির প্রাণ ফিরে পাওয়ার শক্তি হয়ে ওঠে, যেন সাংস্কৃতিক চর্চাই বাঙালি ফিরে পায় মুক্তির দিশারী রূপে। শেষ পর্যন্ত সেই নাচেই মিলে মুক্তি, জয়ী হয় প্রতিরোধ।
নায়ক হিসেবে রাজ্জাকের প্রথম চলচ্চিত্র বেহুলা। এতে বেহুলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুচন্দা। লোককাহিনীভিত্তিক হলেও ছবিতে ফুটে ওঠে নারীর চিরন্তন আবেগ, আত্মত্যাগ ও অদম্য ভালোবাসা।
বেহুলা তাই কেবল একটি চলচ্চিত্র নয়। এটি বাংলা সংস্কৃতির, নারীর আত্মত্যাগ এবং স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক কালজয়ী দলিল।

পাঁচবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। বিবিসির জরিপে সর্বকালের সেরা ২০ বাংলা গানের মধ্যে তিনটি গানের রচয়িতা গুণী এই গীতিকবি। গানগুলো হচ্ছে ‘জয় বাংলা বাংলার জয়’, ‘একতারা তুই দেশের কথা বল’ ও ‘একবার যেতে দে না’।
৮ দিন আগে
টিমোথি শালামে, চ্যাপেল রোন ও প্যাট্রিক মাহোমসের নামে তৈরি এআইভিত্তিক চ্যাটবট শিশু-কিশোরদের সঙ্গে যৌন, মাদক ও আত্মহত্যাসংক্রান্ত অনুপযুক্ত আলাপ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই চ্যাটবটগুলো টেক্সটের মাধ্যমে এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তৈরি কণ্ঠ ব্যবহার করে, যেগুলো তারকাদের মতো শোনানোর জন্য প্রশিক্ষিত ছিল
৮ দিন আগে
চলচ্চিত্র ছেড়ে দেবো করতে করতেই পাহাড়ি সান্যালের হাত ধরে অভিনয় করেন ‘বসু পরিবার’ ছবিতে। ১৯৫২ সালের সে ছবিটি বেশ নজর কাড়ে অনেকের। ১৯৫৩ সালে মুক্তি পায় ‘সাড়ে চুয়াত্তর’। সুচিত্রা সেনের বিপরীতে উত্তমের এই ছবিটি বক্স অফিসে ব্লকবাস্টার! উত্তম কুমারের চলচ্চিত্র জগতে প্রতিষ্ঠারও সূচনা তার সঙ্গে।
১০ দিন আগে
আগুন মানুষের জীবনে যেমন আশীর্বাদ, তেমনি কখনও কখনও হয়ে ওঠে অভিশাপ। রান্না, আলো বা উষ্ণতা—এসবের জন্য আগুন অপরিহার্য। কিন্তু সামান্য অসাবধানতা আগুনকে পরিণত করতে পারে ভয়ংকর বিপর্যয়ে। রান্নাঘরে চুলার গ্যাস লিক হয়ে বিস্ফোরণ, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট, কিংবা শিল্পকারখানার দুর্ঘটনা—এমন অসংখ্য ঘটনায় মানুষ দগ্ধ হ
১১ দিন আগে