
অরুণাভ বিশ্বাস

খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে গ্রীসের অ্যাথেন্স নগররাষ্ট্র আর পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়েছিল যেটি ইতিহাসে ‘ব্যাটল অব ম্যারাথন’ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ অনেকের মতে শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না, এটি ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। আজকের আধুনিক বিশ্বে আমরা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, এবং গণভিত্তিক শাসনব্যবস্থার কথা বলি—সেই ধারণাগুলোর সূচনার পথ তৈরি করেছিল এই যুদ্ধ।
ঘটনার পেছনের ইতিহাসটাও বেশ নাটকীয়। পারস্য সম্রাট দরিয়ুস তখন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, যার ক্ষমতা পশ্চিমে ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার সাম্রাজ্যের এক কোণে ছিল ছোট ছোট স্বাধীন গ্রীক নগররাষ্ট্র, যেমন—অ্যাথেন্স, স্পার্টা, থিবস। এই নগররাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতাকে খুব গুরুত্ব দিত এবং পারস্যের মতো একচ্ছত্র শাসনের বিরুদ্ধে ছিল।
সমস্যার শুরু যখন পারস্যের অধীনে থাকা আয়োনীয় (বর্তমান তুরস্কের উপকূলীয় অঞ্চল) কিছু গ্রিক নগররাষ্ট্র বিদ্রোহ করে এবং অ্যাথেন্স তাদের সাহায্য করে। দরিয়ুস এটাকে নিজের সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেন এবং অ্যাথেন্সকে শিক্ষা দিতে একটি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন। সেই অভিযানেই পারস্য বাহিনী এসে পৌঁছে ম্যারাথনের সমতলে।
পারস্য সেনা সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০, আর অ্যাথেন্সের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১০,০০০। সংখ্যায় এত কম হয়েও অ্যাথেন্স কেন লড়াই করল? কারণ, তারা জানত—পরাজিত হলে কেবল শহর ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে তাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বিশ্বাস, আর সংস্কৃতিও।
ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল একটি সমতল ভূমি, যার একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে সমুদ্র। পারস্যরা চেয়েছিল সমুদ্রপথে দ্রুত এগিয়ে অ্যাথেন্স আক্রমণ করতে। কিন্তু অ্যাথেন্সের সেনাপতিরা (বিশেষ করে মিলটিয়াডেস) কৌশলে সিদ্ধান্ত নেন—শত্রুদের এখানেই থামাতে হবে। তারা সৈন্যদের ঘন ত্রিভুজাকারে সাজিয়ে, পারস্যদের দিক থেকে একটু দুর্বল মধ্যভাগ রেখে, একধরনের চক্রাকারে ঘিরে ধরার পরিকল্পনা করেন।
যুদ্ধের দিন অ্যাথেনীয় সেনারা দৌড়ে এগিয়ে এসে পারস্য বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরনের আক্রমণ সে সময়ের পারস্য সেনারা কল্পনাও করেনি। দ্রুততার সঙ্গে হামলা এবং দুই পাশ থেকে ঘিরে ধরার কৌশলে পারস্য বাহিনী ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা পিছু হটে জাহাজে ওঠার চেষ্টা করে। অনেকেই ডুবে মারা যায়। অনুমান করা হয়, পারস্যের প্রায় ৬,০০০ সৈন্য নিহত হয়, আর অ্যাথেন্সের মাত্র ১৯২ জন।
এই জয়ের পর একটি মিথ কিংবদন্তি হয়ে যায়, যা আজও মানুষের মুখে মুখে। বলা হয়, এক সৈন্য, যার নাম ছিল ফিডিপিডেস, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অ্যাথেন্স শহরে দৌড়ে গিয়ে ‘নিকো’-অর্থাৎ ‘আমরা জয়ী হয়েছি’ বলেই মারা যান। এই গল্প থেকেই আধুনিক ‘ম্যারাথন দৌড়’-এর উৎপত্তি, যার দৈর্ঘ্য এখন ৪২.১৯৫ কিলোমিটার।
ব্যাটল অব ম্যারাথনের গুরুত্ব শুধু অ্যাথেন্সকে রক্ষা করা নয়, এর মাধ্যমে গ্রিকরা দেখিয়ে দেয় যে সংগঠিত হয়ে, কৌশল খাটিয়ে, সাহসের সঙ্গে বড় শত্রুকেও হারানো যায়। এই জয় ইউরোপের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
এই যুদ্ধের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টম হল্যান্ড বলেন,“যদি পারস্য ম্যারাথনে জয়ী হতো, তাহলে হয়তো গ্রিসের ক্ল্যাসিক যুগই আসতো না, থাকত না সক্রেটিস, প্লেটো, কিংবা আমাদের চেনা গণতন্ত্র।”
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল কার্টলেজ, যিনি প্রাচীন গ্রিসের উপর বিশেষজ্ঞ, বলেন, “ম্যারাথন এমন এক যুদ্ধ, যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার শৈশবেই রক্ষা করেছিল।”
তবে কেউ কেউ এটাও মনে করেন যে ম্যারাথনের বিজয়কাহিনি কিছুটা অতিরঞ্জিত, কারণ স্পার্টা ও অন্যান্য গ্রিক নগররাষ্ট্র পরবর্তীতে পারস্যের বিরুদ্ধে আরও বড় বড় যুদ্ধ করেছে। তবে ইতিহাসবিদরা একমত যে এই যুদ্ধ একটি মনস্তাত্ত্বিক জয়ের নাম, যা অ্যাথেন্সকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এবং ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চিন্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
এই যুদ্ধের পর অ্যাথেন্সে গণতন্ত্র আরও মজবুত হয়। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে জনগণের শক্তি থাকলে তাতেই বিজয় সম্ভব। কেবল রাজার বা অভিজাতদের নয়, সাধারণ মানুষের ভোট, মতামত আর অংশগ্রহণও যে গুরুত্বপূর্ণ—এই ধারণা আরও বেশি রূপ নেয়।
ব্যাটল অব ম্যারাথনের আরেকটি প্রভাব ছিল সাহিত্যে ও শিল্পে। গ্রীক নাট্যকাররা এই যুদ্ধের বীরত্বগাথা নিয়ে নাটক রচনা করেন, ভাস্কররা ভাস্কর্য নির্মাণ করেন, এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যুদ্ধটি হয়ে ওঠে গৌরবের প্রতীক। এমনকি, রোমানরাও এই যুদ্ধের বীরত্বকে তাদের নিজস্ব পরিচয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।
ম্যারাথনের যুদ্ধ তাই শুধু একটি যুদ্ধ ছিল না—এটি ছিল একটি আদর্শের প্রতিরক্ষা। এটি ছিল একটি সমাজের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এবং এটি ছিল একটি বার্তা যে, যত বড় শত্রুই হোক না কেন, আত্মবিশ্বাস, ঐক্য, কৌশল আর জনগণের শক্তি থাকলে জয় সম্ভব।
আজ যখন আমরা ম্যারাথনের নাম শুনি, তখন আমরা শুধু দৌড় প্রতিযোগিতার কথা মনে করি। কিন্তু এই নামের পেছনে আছে রক্ত, ত্যাগ, বিশ্বাস আর একটি সভ্যতার বেঁচে থাকার গল্প। সেই গল্প আমাদের শেখায়—স্বাধীনতা শুধু শব্দ নয়, এটি অর্জন করতে হয় লড়াই করে, আর ধরে রাখতে হয় ঐক্য দিয়ে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে গ্রীসের অ্যাথেন্স নগররাষ্ট্র আর পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়েছিল যেটি ইতিহাসে ‘ব্যাটল অব ম্যারাথন’ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ অনেকের মতে শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না, এটি ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রক্ষার লড়াই। আজকের আধুনিক বিশ্বে আমরা যে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, এবং গণভিত্তিক শাসনব্যবস্থার কথা বলি—সেই ধারণাগুলোর সূচনার পথ তৈরি করেছিল এই যুদ্ধ।
ঘটনার পেছনের ইতিহাসটাও বেশ নাটকীয়। পারস্য সম্রাট দরিয়ুস তখন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, যার ক্ষমতা পশ্চিমে ভারত থেকে শুরু করে পূর্বে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। তার সাম্রাজ্যের এক কোণে ছিল ছোট ছোট স্বাধীন গ্রীক নগররাষ্ট্র, যেমন—অ্যাথেন্স, স্পার্টা, থিবস। এই নগররাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বাধীনতাকে খুব গুরুত্ব দিত এবং পারস্যের মতো একচ্ছত্র শাসনের বিরুদ্ধে ছিল।
সমস্যার শুরু যখন পারস্যের অধীনে থাকা আয়োনীয় (বর্তমান তুরস্কের উপকূলীয় অঞ্চল) কিছু গ্রিক নগররাষ্ট্র বিদ্রোহ করে এবং অ্যাথেন্স তাদের সাহায্য করে। দরিয়ুস এটাকে নিজের সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হিসেবে দেখেন এবং অ্যাথেন্সকে শিক্ষা দিতে একটি সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন। সেই অভিযানেই পারস্য বাহিনী এসে পৌঁছে ম্যারাথনের সমতলে।
পারস্য সেনা সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০, আর অ্যাথেন্সের সৈন্য সংখ্যা মাত্র ১০,০০০। সংখ্যায় এত কম হয়েও অ্যাথেন্স কেন লড়াই করল? কারণ, তারা জানত—পরাজিত হলে কেবল শহর ধ্বংস হবে না, ধ্বংস হবে তাদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বিশ্বাস, আর সংস্কৃতিও।
ম্যারাথনের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল একটি সমতল ভূমি, যার একপাশে পাহাড় আর অন্যপাশে সমুদ্র। পারস্যরা চেয়েছিল সমুদ্রপথে দ্রুত এগিয়ে অ্যাথেন্স আক্রমণ করতে। কিন্তু অ্যাথেন্সের সেনাপতিরা (বিশেষ করে মিলটিয়াডেস) কৌশলে সিদ্ধান্ত নেন—শত্রুদের এখানেই থামাতে হবে। তারা সৈন্যদের ঘন ত্রিভুজাকারে সাজিয়ে, পারস্যদের দিক থেকে একটু দুর্বল মধ্যভাগ রেখে, একধরনের চক্রাকারে ঘিরে ধরার পরিকল্পনা করেন।
যুদ্ধের দিন অ্যাথেনীয় সেনারা দৌড়ে এগিয়ে এসে পারস্য বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ ধরনের আক্রমণ সে সময়ের পারস্য সেনারা কল্পনাও করেনি। দ্রুততার সঙ্গে হামলা এবং দুই পাশ থেকে ঘিরে ধরার কৌশলে পারস্য বাহিনী ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা পিছু হটে জাহাজে ওঠার চেষ্টা করে। অনেকেই ডুবে মারা যায়। অনুমান করা হয়, পারস্যের প্রায় ৬,০০০ সৈন্য নিহত হয়, আর অ্যাথেন্সের মাত্র ১৯২ জন।
এই জয়ের পর একটি মিথ কিংবদন্তি হয়ে যায়, যা আজও মানুষের মুখে মুখে। বলা হয়, এক সৈন্য, যার নাম ছিল ফিডিপিডেস, তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অ্যাথেন্স শহরে দৌড়ে গিয়ে ‘নিকো’-অর্থাৎ ‘আমরা জয়ী হয়েছি’ বলেই মারা যান। এই গল্প থেকেই আধুনিক ‘ম্যারাথন দৌড়’-এর উৎপত্তি, যার দৈর্ঘ্য এখন ৪২.১৯৫ কিলোমিটার।
ব্যাটল অব ম্যারাথনের গুরুত্ব শুধু অ্যাথেন্সকে রক্ষা করা নয়, এর মাধ্যমে গ্রিকরা দেখিয়ে দেয় যে সংগঠিত হয়ে, কৌশল খাটিয়ে, সাহসের সঙ্গে বড় শত্রুকেও হারানো যায়। এই জয় ইউরোপের স্বাধীনচেতা মনোভাবকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
এই যুদ্ধের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ টম হল্যান্ড বলেন,“যদি পারস্য ম্যারাথনে জয়ী হতো, তাহলে হয়তো গ্রিসের ক্ল্যাসিক যুগই আসতো না, থাকত না সক্রেটিস, প্লেটো, কিংবা আমাদের চেনা গণতন্ত্র।”
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পল কার্টলেজ, যিনি প্রাচীন গ্রিসের উপর বিশেষজ্ঞ, বলেন, “ম্যারাথন এমন এক যুদ্ধ, যা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তার শৈশবেই রক্ষা করেছিল।”
তবে কেউ কেউ এটাও মনে করেন যে ম্যারাথনের বিজয়কাহিনি কিছুটা অতিরঞ্জিত, কারণ স্পার্টা ও অন্যান্য গ্রিক নগররাষ্ট্র পরবর্তীতে পারস্যের বিরুদ্ধে আরও বড় বড় যুদ্ধ করেছে। তবে ইতিহাসবিদরা একমত যে এই যুদ্ধ একটি মনস্তাত্ত্বিক জয়ের নাম, যা অ্যাথেন্সকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে এবং ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক চিন্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
এই যুদ্ধের পর অ্যাথেন্সে গণতন্ত্র আরও মজবুত হয়। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে জনগণের শক্তি থাকলে তাতেই বিজয় সম্ভব। কেবল রাজার বা অভিজাতদের নয়, সাধারণ মানুষের ভোট, মতামত আর অংশগ্রহণও যে গুরুত্বপূর্ণ—এই ধারণা আরও বেশি রূপ নেয়।
ব্যাটল অব ম্যারাথনের আরেকটি প্রভাব ছিল সাহিত্যে ও শিল্পে। গ্রীক নাট্যকাররা এই যুদ্ধের বীরত্বগাথা নিয়ে নাটক রচনা করেন, ভাস্কররা ভাস্কর্য নির্মাণ করেন, এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যুদ্ধটি হয়ে ওঠে গৌরবের প্রতীক। এমনকি, রোমানরাও এই যুদ্ধের বীরত্বকে তাদের নিজস্ব পরিচয়ের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।
ম্যারাথনের যুদ্ধ তাই শুধু একটি যুদ্ধ ছিল না—এটি ছিল একটি আদর্শের প্রতিরক্ষা। এটি ছিল একটি সমাজের ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এবং এটি ছিল একটি বার্তা যে, যত বড় শত্রুই হোক না কেন, আত্মবিশ্বাস, ঐক্য, কৌশল আর জনগণের শক্তি থাকলে জয় সম্ভব।
আজ যখন আমরা ম্যারাথনের নাম শুনি, তখন আমরা শুধু দৌড় প্রতিযোগিতার কথা মনে করি। কিন্তু এই নামের পেছনে আছে রক্ত, ত্যাগ, বিশ্বাস আর একটি সভ্যতার বেঁচে থাকার গল্প। সেই গল্প আমাদের শেখায়—স্বাধীনতা শুধু শব্দ নয়, এটি অর্জন করতে হয় লড়াই করে, আর ধরে রাখতে হয় ঐক্য দিয়ে।
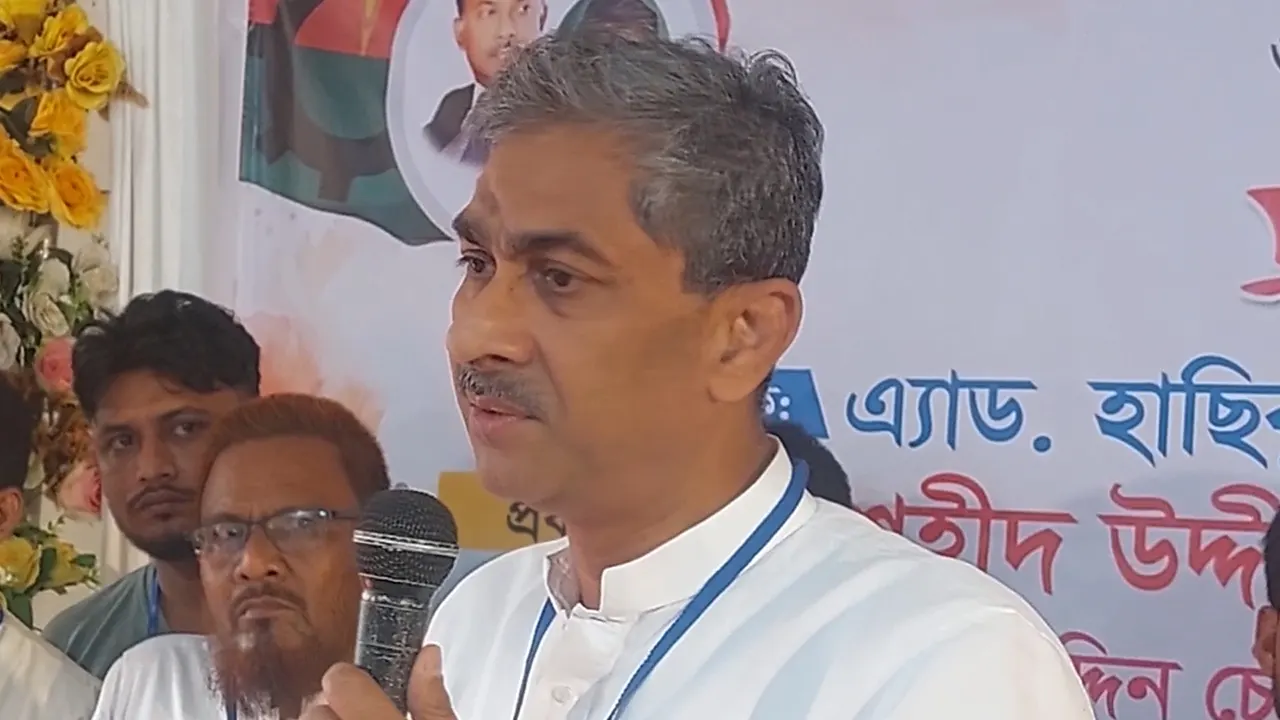
তিনি জানান, টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি'র প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঙ্গে তিনিও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন করতে সমন্বয় এবং সকল প্রস্তুতি তদরকি করছেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই নিয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার।
১৭ ঘণ্টা আগে
এর আগে, গতকাল (শনিবার) বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
আযাদ বলেন, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চান। জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা এবং নির্বাচনী অনিয়মের তদন্তের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন।
১৯ ঘণ্টা আগে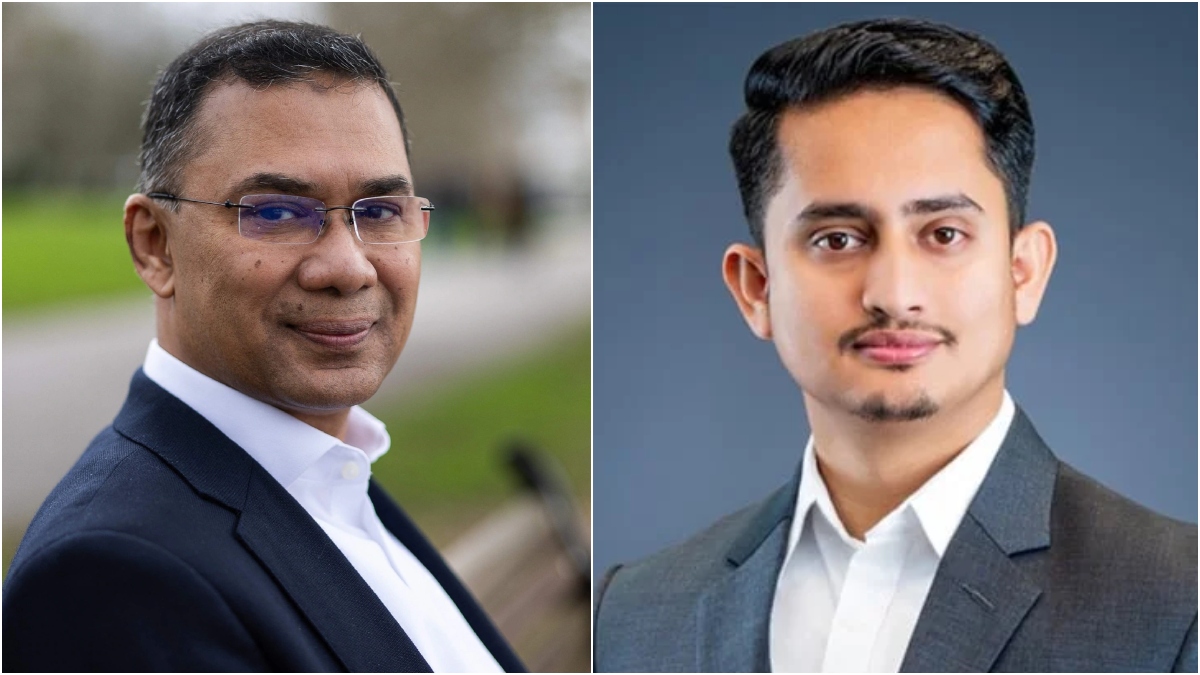
ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।
২১ ঘণ্টা আগে