
অরুণাভ বিশ্বাস

বাংলার ইতিহাসে ইশা খাঁ একটি চিরভাস্বর নাম। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল বারো ভূঁইয়ার শক্ত জোট, যারা মোগল সাম্রাজ্যের অগ্রগতিকে বারবার রুখে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল তাঁর সঙ্গে সম্রাট আকবরের প্রিয় সেনানায়ক মানসিংহের যুদ্ধ, যা শুধু অস্ত্রের লড়াই ছিল না—ছিল দুই ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত: একটি ছিল সম্রাটের কেন্দ্রীয়তাবাদ, অন্যটি ছিল আঞ্চলিক স্বাধীকার ও গৌরবের প্রতীক।
ইশা খাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল ভূইঞাদের শক্ত ঘাঁটি সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চল। তিনি ছিলেন বাংলার পূর্বাঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা, যাঁর প্রতি জনসাধারণের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনী, অভিজ্ঞ সেনা এবং স্থানীয় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। অন্যদিকে মানসিংহ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। তিনি আকবরের সেনাবাহিনীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৫৯৪ সালে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাকে মোগল শাসনের অধীন আনয়ন।
১৫৯৭ সালের দিকে এই দুই নেতার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে যখন ইশা খাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন মানসিংহ এবং বারো ভূঁইয়ার শক্তি দমন করতে উদ্যোগী হন। প্রথমদিকে, মোগল সেনাবাহিনী ঢাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে এবং সেখান থেকে ভাটির দিকে অগ্রসর হয়। ইশা খাঁ বুঝতে পারেন এই আক্রমণ একটিমাত্র যুদ্ধ নয়, বরং এটি তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ওপর আঘাত।
ইশা খাঁ তাঁর বাহিনী সংগঠিত করেন সুনিপুণ কৌশলে। তিনি নদীপথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কারণ ভাটি অঞ্চলে জলাভূমি ও নদীর খাঁড়ি ছিল তাঁর পক্ষে এক বিশাল প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তিনি মানসিংহের সৈন্যদের টেনে আনেন এমন এক এলাকায়, যেখানে স্থলসেনা কার্যকরভাবে যুদ্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ শুরু হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ নৌযুদ্ধে, যেখানে ইশা খাঁর নিজস্ব নির্মিত “গজনৌকা” ও “গরুড় নৌকা” প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই যুদ্ধেই দেখা যায়, কীভাবে এক আঞ্চলিক বীর তাঁর কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্রাটের সেনানায়ককে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।
ইশা খাঁর অন্যতম শক্তি ছিল তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা। তিনি কেবল যুদ্ধেই নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি মোগলদের সঙ্গে কখনো সরাসরি সংঘর্ষে গিয়েছেন, আবার কখনো চুক্তির মাধ্যমে সময়ও কিনেছেন, যাতে নিজের শক্তি সংগঠিত করতে পারেন। ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম. ইটন তাঁর বই “দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার” ইশা খাঁ জানতেন কখন যুদ্ধ করতে হবে আর কখন আলোচনায় যেতে হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য নয়, ছিল স্বায়ত্তশাসন।”
এই যুদ্ধের শেষে মোগল বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য কিছু ভূখণ্ড মোগলদের হাতে গিয়েছিল, ইশা খাঁ নিজের প্রভাব খাটিয়ে আবারো ভাটির অঞ্চল পুনর্দখল করেন এবং কার্যত স্বাধীন শাসন বজায় রাখেন। তাঁর মৃত্যুর আগপর্যন্ত মোগল শাসকরা এই অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি।
আধুনিক ইতিহাসবিদরা ইশা খাঁকে কেবল একজন প্রাদেশিক নেতা হিসেবে নয়, বরং উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের প্রাথমিক প্রতীক হিসেবে দেখেন। ব্রিটিশ গবেষক হার্লে লিম্যান ২০২০ সালের একটি প্রবন্ধে বলেন, “মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইশা খাঁ এমন এক স্থানীয় প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন, যা পরবর্তী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়।”
ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—ইশা খাঁ কখনো নিজেকে সম্রাটের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেননি। তিনি ‘আকবর বাদশাহ’কে খোলা মনে শ্রদ্ধা জানাতেন, এমনকি তার নামে খুতবা পড়ানো হত। কিন্তু স্থানীয় শাসনের অধিকার নিয়ে তিনি ছিলেন অনড়। এই দ্বৈত অবস্থান ছিল তার রাজনৈতিক চাতুর্যের নিদর্শন। ফরাসি ইতিহাসবিদ আঁরি দ্যুলফু তাঁর গবেষণায় বলেন, “ইশা খাঁ ছিলেন আনুগত্য ও প্রতিরোধের ভারসাম্য রক্ষায় এক দক্ষ কৌশলী। তিনি সম্রাটকে সম্মান জানাতেন, কিন্তু তাঁর সেনানায়কদের প্রতিহত করতেন।”
ইশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধ তাই কেবল একটি ঐতিহাসিক সংঘর্ষ নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রতীক। এই যুদ্ধ বাংলার মানুষকে দেখিয়েছিল, শক্তিমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো যায়, যদি নেতৃত্বে থাকে সাহস, কৌশল ও জনসমর্থন। আজও বাংলার নদী-ভূমিতে ইশা খাঁর নাম উচ্চারিত হয় গর্ব ও সম্মানের সঙ্গে।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অরুণাভ মুখোপাধ্যায় ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, ” অর্থাৎ, “ইশা খাঁ ও মানসিংহের মুখোমুখি অবস্থান কেবল একটি সামরিক ঘটনা ছিল না; এটি ছিল এক স্বতন্ত্র বাংলা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঘোষণা।”
প্রতিকূলতার মধ্যেও কিভাবে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার চেতনা টিকে থাকে, এই যুদ্ধ তার প্রমাণ। ইশা খাঁর দৃঢ়তা, তার কৌশল, তার দূরদর্শিতা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায়, বিজয় কেবল শক্তির নয়, কৌশল ও জনমানসের সমর্থনেরও। আর সেই জায়গায় ইশা খাঁ ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন ইতিহাস নির্মাতা।

বাংলার ইতিহাসে ইশা খাঁ একটি চিরভাস্বর নাম। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল বারো ভূঁইয়ার শক্ত জোট, যারা মোগল সাম্রাজ্যের অগ্রগতিকে বারবার রুখে দিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল তাঁর সঙ্গে সম্রাট আকবরের প্রিয় সেনানায়ক মানসিংহের যুদ্ধ, যা শুধু অস্ত্রের লড়াই ছিল না—ছিল দুই ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত: একটি ছিল সম্রাটের কেন্দ্রীয়তাবাদ, অন্যটি ছিল আঞ্চলিক স্বাধীকার ও গৌরবের প্রতীক।
ইশা খাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল ভূইঞাদের শক্ত ঘাঁটি সোনারগাঁও ও ভাটি অঞ্চল। তিনি ছিলেন বাংলার পূর্বাঞ্চলের অবিসংবাদিত নেতা, যাঁর প্রতি জনসাধারণের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনী, অভিজ্ঞ সেনা এবং স্থানীয় ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান তাঁকে অনন্য করে তুলেছিল। অন্যদিকে মানসিংহ জাতিতে রাজপুত ছিলেন। তিনি আকবরের সেনাবাহিনীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলার সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ১৫৯৪ সালে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাকে মোগল শাসনের অধীন আনয়ন।
১৫৯৭ সালের দিকে এই দুই নেতার মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট গড়ে ওঠে যখন ইশা খাঁর কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন মানসিংহ এবং বারো ভূঁইয়ার শক্তি দমন করতে উদ্যোগী হন। প্রথমদিকে, মোগল সেনাবাহিনী ঢাকায় ঘাঁটি স্থাপন করে এবং সেখান থেকে ভাটির দিকে অগ্রসর হয়। ইশা খাঁ বুঝতে পারেন এই আক্রমণ একটিমাত্র যুদ্ধ নয়, বরং এটি তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের ওপর আঘাত।
ইশা খাঁ তাঁর বাহিনী সংগঠিত করেন সুনিপুণ কৌশলে। তিনি নদীপথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কারণ ভাটি অঞ্চলে জলাভূমি ও নদীর খাঁড়ি ছিল তাঁর পক্ষে এক বিশাল প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। তিনি মানসিংহের সৈন্যদের টেনে আনেন এমন এক এলাকায়, যেখানে স্থলসেনা কার্যকরভাবে যুদ্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ শুরু হয় এক জাঁকজমকপূর্ণ নৌযুদ্ধে, যেখানে ইশা খাঁর নিজস্ব নির্মিত “গজনৌকা” ও “গরুড় নৌকা” প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই যুদ্ধেই দেখা যায়, কীভাবে এক আঞ্চলিক বীর তাঁর কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সম্রাটের সেনানায়ককে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন।
ইশা খাঁর অন্যতম শক্তি ছিল তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা। তিনি কেবল যুদ্ধেই নয়, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিলেন। তিনি মোগলদের সঙ্গে কখনো সরাসরি সংঘর্ষে গিয়েছেন, আবার কখনো চুক্তির মাধ্যমে সময়ও কিনেছেন, যাতে নিজের শক্তি সংগঠিত করতে পারেন। ইতিহাসবিদ রিচার্ড এম. ইটন তাঁর বই “দ্য রাইজ অব ইসলাম অ্যান্ড দ্য বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার” ইশা খাঁ জানতেন কখন যুদ্ধ করতে হবে আর কখন আলোচনায় যেতে হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য নয়, ছিল স্বায়ত্তশাসন।”
এই যুদ্ধের শেষে মোগল বাহিনী চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য কিছু ভূখণ্ড মোগলদের হাতে গিয়েছিল, ইশা খাঁ নিজের প্রভাব খাটিয়ে আবারো ভাটির অঞ্চল পুনর্দখল করেন এবং কার্যত স্বাধীন শাসন বজায় রাখেন। তাঁর মৃত্যুর আগপর্যন্ত মোগল শাসকরা এই অঞ্চলে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি।
আধুনিক ইতিহাসবিদরা ইশা খাঁকে কেবল একজন প্রাদেশিক নেতা হিসেবে নয়, বরং উপনিবেশবিরোধী মনোভাবের প্রাথমিক প্রতীক হিসেবে দেখেন। ব্রিটিশ গবেষক হার্লে লিম্যান ২০২০ সালের একটি প্রবন্ধে বলেন, “মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ইশা খাঁ এমন এক স্থানীয় প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন, যা পরবর্তী উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়।”
ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—ইশা খাঁ কখনো নিজেকে সম্রাটের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেননি। তিনি ‘আকবর বাদশাহ’কে খোলা মনে শ্রদ্ধা জানাতেন, এমনকি তার নামে খুতবা পড়ানো হত। কিন্তু স্থানীয় শাসনের অধিকার নিয়ে তিনি ছিলেন অনড়। এই দ্বৈত অবস্থান ছিল তার রাজনৈতিক চাতুর্যের নিদর্শন। ফরাসি ইতিহাসবিদ আঁরি দ্যুলফু তাঁর গবেষণায় বলেন, “ইশা খাঁ ছিলেন আনুগত্য ও প্রতিরোধের ভারসাম্য রক্ষায় এক দক্ষ কৌশলী। তিনি সম্রাটকে সম্মান জানাতেন, কিন্তু তাঁর সেনানায়কদের প্রতিহত করতেন।”
ইশা খাঁ ও মানসিংহের যুদ্ধ তাই কেবল একটি ঐতিহাসিক সংঘর্ষ নয়, এটি একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের প্রতীক। এই যুদ্ধ বাংলার মানুষকে দেখিয়েছিল, শক্তিমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো যায়, যদি নেতৃত্বে থাকে সাহস, কৌশল ও জনসমর্থন। আজও বাংলার নদী-ভূমিতে ইশা খাঁর নাম উচ্চারিত হয় গর্ব ও সম্মানের সঙ্গে।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ভারতের দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অরুণাভ মুখোপাধ্যায় ২০২৩ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, ” অর্থাৎ, “ইশা খাঁ ও মানসিংহের মুখোমুখি অবস্থান কেবল একটি সামরিক ঘটনা ছিল না; এটি ছিল এক স্বতন্ত্র বাংলা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঘোষণা।”
প্রতিকূলতার মধ্যেও কিভাবে আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার চেতনা টিকে থাকে, এই যুদ্ধ তার প্রমাণ। ইশা খাঁর দৃঢ়তা, তার কৌশল, তার দূরদর্শিতা আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায়, বিজয় কেবল শক্তির নয়, কৌশল ও জনমানসের সমর্থনেরও। আর সেই জায়গায় ইশা খাঁ ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন ইতিহাস নির্মাতা।

এর আগে, গতকাল (শনিবার) বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়।
১৫ ঘণ্টা আগে
আযাদ বলেন, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চান। জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা এবং নির্বাচনী অনিয়মের তদন্তের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন।
১৬ ঘণ্টা আগে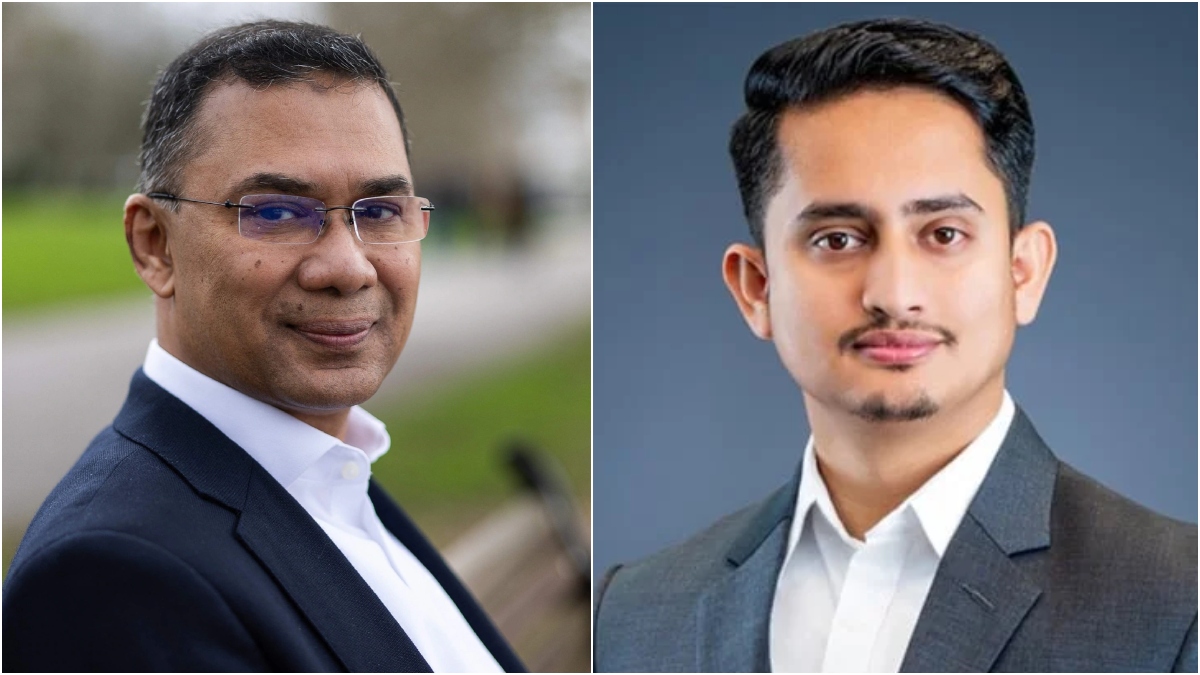
ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।
১৮ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিলুপ্ত হওয়া এ কমিটিগুলোর কোনো নেতাকর্মী যদি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কোনো প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তবে তার দায়ভার ছাত্রদল বা যুবদল বহন করবে না।
১৮ ঘণ্টা আগে