
অরুণাভ বিশ্বাস

বাংলাদেশের কুমিল্লার বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য রহস্যময় জগত, যার নাম ময়নামতি। ময়নামতির প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালে যতদূর চোখ যায় শুধু ছোট ছোট টিলা আর ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ দেখা যায়। প্রথম দর্শনে এগুলো হয়তো নিছক কিছু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এদের প্রতিটি ইট, প্রতিটি মাটির স্তর লুকিয়ে রেখেছে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার গল্প। ময়নামতি একসময় ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এক বিশাল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র, যেখানে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক সাধনা হতো, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় চলত গবেষণা। তাই ইতিহাসবিদরা ময়নামতিকে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং বাংলার সোনালি অতীতের প্রতীক হিসেবে দেখেন।
প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলো ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং সেই সময়েই ময়নামতিতে গড়ে ওঠে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মহাবিহার। ইতিহাসবিদদের মতে, এই অঞ্চল একসময় পাল রাজবংশ ও পরবর্তীতে সেন রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। পালরা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল সমর্থক, আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে শিক্ষা, ধর্ম, শিল্প ও স্থাপত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটে।
ময়নামতি আসলে ছিল এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। এখানে ভিক্ষুরা শুধু ধর্মচর্চা করতেন না, বরং দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও কাজ করতেন। ফলে একে কেবল ধর্মীয় কেন্দ্র বললে ভুল হবে, এটি ছিল এক বহুমুখী শিক্ষাকেন্দ্র।
ময়নামতির সবচেয়ে বিখ্যাত প্রত্নস্থল হলো শালবন বিহার। বিশাল চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই মঠে ছিল প্রায় ১১৫টি কক্ষ, একটি বিশাল প্রার্থনাগৃহ এবং মধ্যবর্তী আঙিনা। প্রতিটি কক্ষেই থাকতেন ভিক্ষুরা, যারা দিনরাত ধ্যান, পাঠ ও শিক্ষায় মগ্ন থাকতেন। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা ও মূর্তি প্রমাণ করে যে এটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক কেন্দ্র।
আমেরিকান গবেষক সুসান হান্টার, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার বৌদ্ধ স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, শালবন বিহার সম্পর্কে লিখেছিলেন—“শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ আমাকে সবসময় নালন্দা মহাবিহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে ময়নামতি ছোট হলেও এর শিল্পকলা ও ধর্মীয় গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়।” তাঁর মতে, শালবন বিহার আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অমূল্য রত্ন, যা প্রমাণ করে এই অঞ্চল একসময় জ্ঞানচর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল।
শুধু শালবন বিহারই নয়, ময়নামতিতে আরও বহু প্রত্নস্থল রয়েছে যেগুলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোটিলা মুরা তিনটি স্তূপ নিয়ে গঠিত, যেগুলো সম্ভবত বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হতো। আনন্দ বিহার ও চন্দ্র মুড়া মঠ ছিল বড় আকারের আবাসিক মঠ, যেখানে শত শত ভিক্ষু বাস করতেন। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত আছে—বৌদ্ধ ধর্মীয় কাহিনি থেকে শুরু করে নৃত্যরত নারী, পশুপাখি, ফুল-লতাপাতার অসাধারণ নকশা। এসব শিল্পকর্ম দেখে বোঝা যায়, সে যুগের শিল্পীরা কতটা দক্ষ ছিলেন এবং কীভাবে ধর্মীয় কাহিনি শিল্পের মাধ্যমে জনমানসে ছড়িয়ে দিতেন।
ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেভিড এন. গ্লোভার একবার মন্তব্য করেছিলেন—“ময়নামতি প্রমাণ করে যে এই অঞ্চল কোনোদিনই সভ্যতার বাইরে ছিল না। বরং এখানে যে বৌদ্ধ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় কেন্দ্র।” তাঁর ভাষায়, ময়নামতি ছিল “বৌদ্ধ সংস্কৃতির হারানো রাজধানী।”
ময়নামতির সোনালি দিন স্থায়ী হয়নি। মুসলিম শাসনামলে এসে ধীরে ধীরে এই বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলো বিলুপ্ত হতে শুরু করে। মঠগুলো পরিত্যক্ত হয়, স্তূপগুলো ভেঙে যায়, অনেক কিছুই মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ময়নামতি হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে। স্থানীয় লোককথায় কিছু গল্প বেঁচে থাকলেও ইতিহাসের পাতায় এটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।
ব্রিটিশ শাসনামলে উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ময়নামতির দিকে নজর দেন। তখন প্রথম খননকাজ শুরু হয় এবং একে একে বেরিয়ে আসে অতীতের অমূল্য সম্পদ। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শালবন বিহার পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এবং তখনই বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলাদেশের বুকে লুকিয়ে থাকা এই বিস্ময়ের কথা।
মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক স্ট্যানলি জে. ও’কনর, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পকলা নিয়ে কাজ করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন—“ময়নামতির ভাঙা ইটগুলো শুধু অতীতের নিদর্শন নয়, এগুলো আমাদের জানিয়ে দেয় পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ সভ্যতা কতটা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল।” তাঁর মতে, ময়নামতি শুধু বাংলার নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প ইতিহাসের জন্য এক অনন্য দলিল।
আজকের দিনে ময়নামতি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, এটি পর্যটনেরও বড় কেন্দ্র। প্রতি বছর দেশি-বিদেশি হাজারো মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, অনেক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই, মানুষের অবহেলা, ভাঙচুর আর অবৈধ দখলও এই সম্পদকে হুমকির মুখে ফেলেছে।
জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ড. হেলমুট লস এ বিষয়ে বলেছিলেন—“যদি ময়নামতিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তবে এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্বের জন্য গৌরবের বিষয় হবে। কারণ এটি বৌদ্ধ সভ্যতার আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”
ময়নামতির ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়, বাংলার মাটি শুধু কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলেনি, বরং এখানে একসময় মহৎ শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। এই অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল। ময়নামতি ছিল সেই প্রমাণ যে জ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম মিলেমিশে কীভাবে এক সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা তৈরি করতে পারে।
আজকের বাংলাদেশে ময়নামতির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। এটি একদিকে আমাদের ঐতিহ্য ও শেকড়ের প্রতীক, অন্যদিকে পর্যটন ও গবেষণার জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইতিহাসের ভাঙা ইট আমাদের শেখায় যে, আমরা কত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এখনকার প্রজন্মের দায়িত্ব হলো এই ঐতিহ্যকে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে সংরক্ষণ করা।
ময়নামতি আজ শুধু ধ্বংসাবশেষের স্তূপ নয়, এটি আমাদের জাতির ইতিহাসের সাক্ষ্য। এখানে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় সময় যেন থেমে গেছে। ইটের গাঁথুনিতে এখনো বাজে প্রাচীন প্রার্থনার ধ্বনি, টেরাকোটার ফলকে এখনো ভেসে ওঠে শিল্পীর ছোঁয়া। এ যেন হারানো এক সভ্যতার নিঃশব্দ আর্তি, যা আজও আমাদের ডাক দেয় অতীতকে মনে রাখতে।
একজন বাঙালি হিসেবে ময়নামতি নিয়ে গর্বিত হওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। কারণ এই ইতিহাস কেবল আমাদের শেকড় নয়, এটি গোটা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তাই ময়নামতির প্রতিটি ইট, প্রতিটি টিলা সংরক্ষণ করা মানে হলো আমাদের আত্মপরিচয় রক্ষা করা।

বাংলাদেশের কুমিল্লার বুক জুড়ে ছড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য রহস্যময় জগত, যার নাম ময়নামতি। ময়নামতির প্রান্তরে দাঁড়িয়ে দূরে তাকালে যতদূর চোখ যায় শুধু ছোট ছোট টিলা আর ভাঙাচোরা ইটের স্তূপ দেখা যায়। প্রথম দর্শনে এগুলো হয়তো নিছক কিছু প্রাচীন ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে এদের প্রতিটি ইট, প্রতিটি মাটির স্তর লুকিয়ে রেখেছে হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার গল্প। ময়নামতি একসময় ছিল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার এক বিশাল বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র, যেখানে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিক সাধনা হতো, অন্যদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখায় চলত গবেষণা। তাই ইতিহাসবিদরা ময়নামতিকে শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, বরং বাংলার সোনালি অতীতের প্রতীক হিসেবে দেখেন।
প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলো ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে এবং সেই সময়েই ময়নামতিতে গড়ে ওঠে অসংখ্য বৌদ্ধ মঠ ও মহাবিহার। ইতিহাসবিদদের মতে, এই অঞ্চল একসময় পাল রাজবংশ ও পরবর্তীতে সেন রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। পালরা নিজেরাই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল সমর্থক, আর তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে শিক্ষা, ধর্ম, শিল্প ও স্থাপত্যের অসাধারণ বিকাশ ঘটে।
ময়নামতি আসলে ছিল এক বিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। এখানে ভিক্ষুরা শুধু ধর্মচর্চা করতেন না, বরং দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, ব্যাকরণ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়েও কাজ করতেন। ফলে একে কেবল ধর্মীয় কেন্দ্র বললে ভুল হবে, এটি ছিল এক বহুমুখী শিক্ষাকেন্দ্র।
ময়নামতির সবচেয়ে বিখ্যাত প্রত্নস্থল হলো শালবন বিহার। বিশাল চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই মঠে ছিল প্রায় ১১৫টি কক্ষ, একটি বিশাল প্রার্থনাগৃহ এবং মধ্যবর্তী আঙিনা। প্রতিটি কক্ষেই থাকতেন ভিক্ষুরা, যারা দিনরাত ধ্যান, পাঠ ও শিক্ষায় মগ্ন থাকতেন। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা ও মূর্তি প্রমাণ করে যে এটি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধ এক কেন্দ্র।
আমেরিকান গবেষক সুসান হান্টার, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার বৌদ্ধ স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন, শালবন বিহার সম্পর্কে লিখেছিলেন—“শালবন বিহারের ধ্বংসাবশেষ আমাকে সবসময় নালন্দা মহাবিহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে ময়নামতি ছোট হলেও এর শিল্পকলা ও ধর্মীয় গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়।” তাঁর মতে, শালবন বিহার আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অমূল্য রত্ন, যা প্রমাণ করে এই অঞ্চল একসময় জ্ঞানচর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র ছিল।
শুধু শালবন বিহারই নয়, ময়নামতিতে আরও বহু প্রত্নস্থল রয়েছে যেগুলো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোটিলা মুরা তিনটি স্তূপ নিয়ে গঠিত, যেগুলো সম্ভবত বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হতো। আনন্দ বিহার ও চন্দ্র মুড়া মঠ ছিল বড় আকারের আবাসিক মঠ, যেখানে শত শত ভিক্ষু বাস করতেন। এখানে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন দৃশ্য অঙ্কিত আছে—বৌদ্ধ ধর্মীয় কাহিনি থেকে শুরু করে নৃত্যরত নারী, পশুপাখি, ফুল-লতাপাতার অসাধারণ নকশা। এসব শিল্পকর্ম দেখে বোঝা যায়, সে যুগের শিল্পীরা কতটা দক্ষ ছিলেন এবং কীভাবে ধর্মীয় কাহিনি শিল্পের মাধ্যমে জনমানসে ছড়িয়ে দিতেন।
ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ডেভিড এন. গ্লোভার একবার মন্তব্য করেছিলেন—“ময়নামতি প্রমাণ করে যে এই অঞ্চল কোনোদিনই সভ্যতার বাইরে ছিল না। বরং এখানে যে বৌদ্ধ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বড় কেন্দ্র।” তাঁর ভাষায়, ময়নামতি ছিল “বৌদ্ধ সংস্কৃতির হারানো রাজধানী।”
ময়নামতির সোনালি দিন স্থায়ী হয়নি। মুসলিম শাসনামলে এসে ধীরে ধীরে এই বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলো বিলুপ্ত হতে শুরু করে। মঠগুলো পরিত্যক্ত হয়, স্তূপগুলো ভেঙে যায়, অনেক কিছুই মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ময়নামতি হারিয়ে যায় মানুষের স্মৃতি থেকে। স্থানীয় লোককথায় কিছু গল্প বেঁচে থাকলেও ইতিহাসের পাতায় এটি প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়।
ব্রিটিশ শাসনামলে উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ময়নামতির দিকে নজর দেন। তখন প্রথম খননকাজ শুরু হয় এবং একে একে বেরিয়ে আসে অতীতের অমূল্য সম্পদ। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শালবন বিহার পুরোপুরি উন্মোচিত হয় এবং তখনই বিশ্ববাসী জানতে পারে বাংলাদেশের বুকে লুকিয়ে থাকা এই বিস্ময়ের কথা।
মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক স্ট্যানলি জে. ও’কনর, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার শিল্পকলা নিয়ে কাজ করেছিলেন, তিনি লিখেছিলেন—“ময়নামতির ভাঙা ইটগুলো শুধু অতীতের নিদর্শন নয়, এগুলো আমাদের জানিয়ে দেয় পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ সভ্যতা কতটা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল।” তাঁর মতে, ময়নামতি শুধু বাংলার নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়ার শিল্প ইতিহাসের জন্য এক অনন্য দলিল।
আজকের দিনে ময়নামতি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নয়, এটি পর্যটনেরও বড় কেন্দ্র। প্রতি বছর দেশি-বিদেশি হাজারো মানুষ এখানে আসেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, অনেক নিদর্শন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির ক্ষয়ক্ষতি তো আছেই, মানুষের অবহেলা, ভাঙচুর আর অবৈধ দখলও এই সম্পদকে হুমকির মুখে ফেলেছে।
জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ড. হেলমুট লস এ বিষয়ে বলেছিলেন—“যদি ময়নামতিকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তবে এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো বিশ্বের জন্য গৌরবের বিষয় হবে। কারণ এটি বৌদ্ধ সভ্যতার আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”
ময়নামতির ইতিহাস আমাদের জানিয়ে দেয়, বাংলার মাটি শুধু কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলেনি, বরং এখানে একসময় মহৎ শিক্ষাকেন্দ্রও ছিল। এই অঞ্চল দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছিল। ময়নামতি ছিল সেই প্রমাণ যে জ্ঞান, শিল্প ও ধর্ম মিলেমিশে কীভাবে এক সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা তৈরি করতে পারে।
আজকের বাংলাদেশে ময়নামতির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। এটি একদিকে আমাদের ঐতিহ্য ও শেকড়ের প্রতীক, অন্যদিকে পর্যটন ও গবেষণার জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। ইতিহাসের ভাঙা ইট আমাদের শেখায় যে, আমরা কত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। এখনকার প্রজন্মের দায়িত্ব হলো এই ঐতিহ্যকে শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে সংরক্ষণ করা।
ময়নামতি আজ শুধু ধ্বংসাবশেষের স্তূপ নয়, এটি আমাদের জাতির ইতিহাসের সাক্ষ্য। এখানে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় সময় যেন থেমে গেছে। ইটের গাঁথুনিতে এখনো বাজে প্রাচীন প্রার্থনার ধ্বনি, টেরাকোটার ফলকে এখনো ভেসে ওঠে শিল্পীর ছোঁয়া। এ যেন হারানো এক সভ্যতার নিঃশব্দ আর্তি, যা আজও আমাদের ডাক দেয় অতীতকে মনে রাখতে।
একজন বাঙালি হিসেবে ময়নামতি নিয়ে গর্বিত হওয়া আমাদেরই দায়িত্ব। কারণ এই ইতিহাস কেবল আমাদের শেকড় নয়, এটি গোটা বিশ্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। তাই ময়নামতির প্রতিটি ইট, প্রতিটি টিলা সংরক্ষণ করা মানে হলো আমাদের আত্মপরিচয় রক্ষা করা।

এর আগে, গতকাল (শনিবার) বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়।
১১ ঘণ্টা আগে
আযাদ বলেন, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চান। জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা এবং নির্বাচনী অনিয়মের তদন্তের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন।
১৩ ঘণ্টা আগে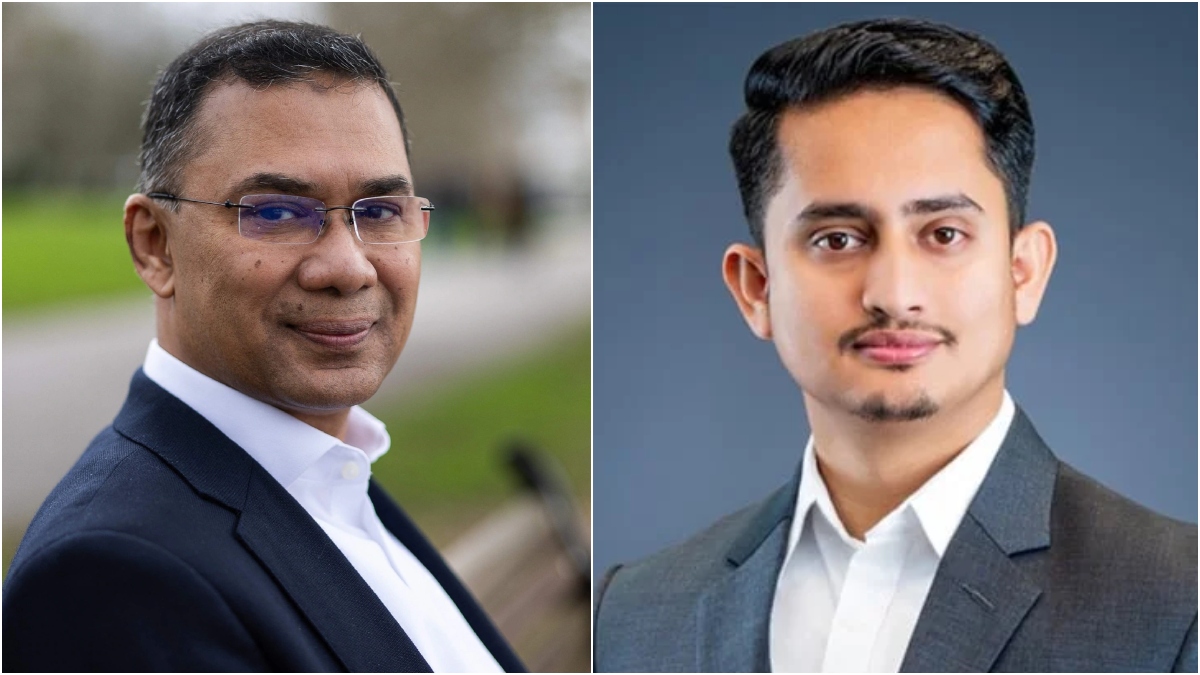
ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।
১৫ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিলুপ্ত হওয়া এ কমিটিগুলোর কোনো নেতাকর্মী যদি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কোনো প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তবে তার দায়ভার ছাত্রদল বা যুবদল বহন করবে না।
১৫ ঘণ্টা আগে