
অরুণাভ বিশ্বাস

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময় ছিল ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতক। এই সময় দেশের নানা অঞ্চলে নানা রাজ্য মাথা তুলছিল, আবার একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছিল। এই রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব মুখোমুখি হন—গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ও কান্যকুব্জ তথা উত্তর ভারতের অধিকাংশ অংশের সম্রাট হর্ষবর্ধন। তাঁদের মধ্যে যে সংঘাত হয়েছিল, তা শুধু দুই শাসকের লড়াই ছিল না, বরং ছিল সংস্কৃতি, ধর্ম, কূটনীতি ও আঞ্চলিক আধিপত্যের সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্বের পেছনে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় বিভাজন, ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিহিংসার এক গাঢ় ইতিহাস।
শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বঙ্গের গৌড় রাজ্যের এক শক্তিশালী রাজা। তিনি প্রথম স্বাধীন গৌড় শাসক হিসেবে পরিচিত যিনি নিজের সাম্রাজ্যকে শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং অঙ্গ, মগধ, উত্তর বিহার ও বর্তমান উড়িষ্যার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড় প্রথম একটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে হর্ষবর্ধন ছিলেন থানের রাজা রাজ্যবর্ধনের ভাই। রাজ্যবর্ধনের হত্যার পর হর্ষ সিংহাসনে বসেন এবং ক্রমে তিনি উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার বিস্তার ছিল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং পাঞ্জাব থেকে অসমের প্রান্তঘেঁষা অঞ্চল পর্যন্ত।
এই দুই শাসকের দ্বন্দ্ব শুরু হয় রাজ্যবর্ধনের হত্যাকে ঘিরে। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজ্যবর্ধনের হত্যার পেছনে শশাঙ্কের হাত ছিল। রাজা রাজ্যবর্ধন যখন নিজের ভগ্নিপতি, মালব দেশের রাজা দেবগুপ্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখন শশাঙ্ক সেই সুযোগে তাঁকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে হর্ষবর্ধনের মনে শশাঙ্কের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন।
এই সংঘাত শুধু দুটি শক্তির যুদ্ধ ছিল না; এর মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনও প্রবলভাবে কাজ করেছিল। হর্ষ ছিলেন একজন সহনশীল হিন্দু শাসক যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজেও বৌদ্ধ প্রভাবিত হন। বিপরীতে, শশাঙ্ক ছিলেন একনিষ্ঠ শৈব হিন্দু, যিনি বৌদ্ধদের বিরোধিতা করতেন বলে কিছু ইতিহাসবিদ দাবি করেছেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত সি ইউ কি বা “দ্য রেকর্ডস অব দ্য ওয়েস্টার্ন রিজিয়নস”-এ শশাঙ্ক সম্পর্কে লেখেন, ‘‘তিনি বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছেন, গৌতম বুদ্ধের একটি পবিত্র বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেছেন, এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেছেন।’’
ইংরেজ ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তাঁর বই আর্লি ইন্ডিয়া: ফ্রম দ্য অরিজিনস টু এ.ডি. ১৩০০–তে লেখেন, ‘‘শশাঙ্ক একদিকে যেমন একজন দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন, অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দমনেও ছিলেন কঠোর। তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের পেছনে ধর্মীয় মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।’’
তবে কিছু গবেষক এই বিবরণকে অতিরঞ্জিত মনে করেন। আমেরিকান ইতিহাসবিদ রিচার্ড সালোমন মনে করেন, ‘‘হিউয়েন সাং ছিলেন বৌদ্ধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন শৈব, তাই হিউয়েন সাং-এর বিবরণে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। শশাঙ্ক হয়তো রাজনৈতিক কারণে কিছু মঠ বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ধর্মীয় নিপীড়ক বলা অতিরঞ্জিত।’’
শশাঙ্ক ও হর্ষের দ্বন্দ্ব সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় গঙ্গা নদীর পশ্চিমে। শশাঙ্ক উত্তর ভারত পর্যন্ত নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন। এই সময় তিনি অঙ্গ ও মগধের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে এক শক্তিশালী প্রশাসন চালু করেন। অন্যদিকে হর্ষ তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসে পুরোদমে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন।
হর্ষবর্ধনের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঙ্গার পূর্ব দিকে এগোলে শশাঙ্ক তাঁর বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার বিবরণ ইতিহাসে অস্পষ্ট। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত, হর্ষবর্ধন শেষ পর্যন্ত গৌড় জয় করতে পারেননি, অন্তত শশাঙ্ক জীবিত থাকা পর্যন্ত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হর্ষবর্ধন মগধসহ অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হন।
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এফ. ই. পার্জিটার তাঁর বই দ্য ডাইনাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দান ইন্ডিয়া–তে লিখেছেন, ‘‘শশাঙ্ক ছিলেন সেই সময়ের একমাত্র শাসক যিনি হর্ষবর্ধনের আগ্রাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।’’
এই দ্বন্দ্বের আরেকটি দিক ছিল রাজনৈতিক জোট ও বিশ্বাসঘাতকতা। হর্ষ শুরুতে শশাঙ্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক চূড়ান্ত শত্রুতায় রূপ নেয়। এই ধরনের সম্পর্কের গতিবিধি প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। শশাঙ্ক হর্ষের বিরুদ্ধে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তেমন ফল পাননি। এইসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও যুদ্ধের ফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছিল।
শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে আনুমানিক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং হর্ষ সেই সুযোগে মগধসহ আরও কিছু এলাকা দখল করেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন কখনোই পুরো গৌড় দখল করতে পারেননি। শশাঙ্কের পর তাঁর উত্তরসূরি মানব রাজার আমলেই গৌড়ের পতন শুরু হয়।
ফরাসি ইতিহাসবিদ আন্দ্রে ল্যাম্বার্ট তাঁর গবেষণাপত্রে লিখেছেন, ‘‘শশাঙ্ক ও হর্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল শুধুই রাজ্য দখলের যুদ্ধ নয়; এটি ছিল সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রাজনীতির টানাপোড়েনের বহিঃপ্রকাশ। শশাঙ্ক গৌড়কে যা দিয়েছিলেন, তা চিরস্থায়ী না হলেও সেই সময়ের জন্য এক সুদৃঢ় রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল।’’
এই দ্বন্দ্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস শুধু জয়-পরাজয়ের গল্প নয়, বরং তা বহুস্তর বিশিষ্ট জটিল মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মিশ্রণ। শশাঙ্ক হয়তো হর্ষবর্ধনের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেননি, কিন্তু তিনি গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। অপরদিকে হর্ষবর্ধন তাঁর কৌশল, সহিষ্ণুতা ও সামরিক দক্ষতায় এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যা পরবর্তীতে অনেক শাসকের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।
তাঁদের দ্বন্দ্ব ইতিহাসের পাতায় কেবল যুদ্ধের কাহিনি হয়ে থাকেনি, বরং তা হয়ে উঠেছে এক যুগের প্রতিচ্ছবি—যেখানে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম, ধর্মের জন্য দ্বন্দ্ব এবং আত্মমর্যাদার জন্য আত্মত্যাগ একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। সেই ইতিহাস আজও গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হয়ে রয়ে গেছে, আর আমাদের জন্য তা এক অনন্য শিক্ষার উৎস হয়ে আছে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে অবিস্মরণীয় সময় ছিল ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতক। এই সময় দেশের নানা অঞ্চলে নানা রাজ্য মাথা তুলছিল, আবার একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করছিল। এই রাজনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দুই বিশাল ব্যক্তিত্ব মুখোমুখি হন—গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক ও কান্যকুব্জ তথা উত্তর ভারতের অধিকাংশ অংশের সম্রাট হর্ষবর্ধন। তাঁদের মধ্যে যে সংঘাত হয়েছিল, তা শুধু দুই শাসকের লড়াই ছিল না, বরং ছিল সংস্কৃতি, ধর্ম, কূটনীতি ও আঞ্চলিক আধিপত্যের সংঘর্ষ। এই দ্বন্দ্বের পেছনে রয়েছে নানা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ধর্মীয় বিভাজন, ক্ষমতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিহিংসার এক গাঢ় ইতিহাস।
শশাঙ্ক ছিলেন প্রাচীন বঙ্গের গৌড় রাজ্যের এক শক্তিশালী রাজা। তিনি প্রথম স্বাধীন গৌড় শাসক হিসেবে পরিচিত যিনি নিজের সাম্রাজ্যকে শুধু বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং অঙ্গ, মগধ, উত্তর বিহার ও বর্তমান উড়িষ্যার কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সময়েই গৌড় প্রথম একটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অন্যদিকে হর্ষবর্ধন ছিলেন থানের রাজা রাজ্যবর্ধনের ভাই। রাজ্যবর্ধনের হত্যার পর হর্ষ সিংহাসনে বসেন এবং ক্রমে তিনি উত্তর ভারতের বহু অঞ্চল জয়ের মাধ্যমে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যার বিস্তার ছিল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং পাঞ্জাব থেকে অসমের প্রান্তঘেঁষা অঞ্চল পর্যন্ত।
এই দুই শাসকের দ্বন্দ্ব শুরু হয় রাজ্যবর্ধনের হত্যাকে ঘিরে। বহু ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজ্যবর্ধনের হত্যার পেছনে শশাঙ্কের হাত ছিল। রাজা রাজ্যবর্ধন যখন নিজের ভগ্নিপতি, মালব দেশের রাজা দেবগুপ্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন, তখন শশাঙ্ক সেই সুযোগে তাঁকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে হর্ষবর্ধনের মনে শশাঙ্কের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জন্ম নেয় এবং তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতিশোধ নিতে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন।
এই সংঘাত শুধু দুটি শক্তির যুদ্ধ ছিল না; এর মধ্যে ধর্মীয় বিভাজনও প্রবলভাবে কাজ করেছিল। হর্ষ ছিলেন একজন সহনশীল হিন্দু শাসক যিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং পরবর্তীকালে নিজেও বৌদ্ধ প্রভাবিত হন। বিপরীতে, শশাঙ্ক ছিলেন একনিষ্ঠ শৈব হিন্দু, যিনি বৌদ্ধদের বিরোধিতা করতেন বলে কিছু ইতিহাসবিদ দাবি করেছেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্ত সি ইউ কি বা “দ্য রেকর্ডস অব দ্য ওয়েস্টার্ন রিজিয়নস”-এ শশাঙ্ক সম্পর্কে লেখেন, ‘‘তিনি বৌদ্ধ মঠ ধ্বংস করেছেন, গৌতম বুদ্ধের একটি পবিত্র বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেছেন, এমনকি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করেছেন।’’
ইংরেজ ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার তাঁর বই আর্লি ইন্ডিয়া: ফ্রম দ্য অরিজিনস টু এ.ডি. ১৩০০–তে লেখেন, ‘‘শশাঙ্ক একদিকে যেমন একজন দক্ষ কূটনীতিক ছিলেন, অন্যদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দমনেও ছিলেন কঠোর। তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের পেছনে ধর্মীয় মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।’’
তবে কিছু গবেষক এই বিবরণকে অতিরঞ্জিত মনে করেন। আমেরিকান ইতিহাসবিদ রিচার্ড সালোমন মনে করেন, ‘‘হিউয়েন সাং ছিলেন বৌদ্ধ এবং শশাঙ্ক ছিলেন শৈব, তাই হিউয়েন সাং-এর বিবরণে পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। শশাঙ্ক হয়তো রাজনৈতিক কারণে কিছু মঠ বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ধর্মীয় নিপীড়ক বলা অতিরঞ্জিত।’’
শশাঙ্ক ও হর্ষের দ্বন্দ্ব সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় গঙ্গা নদীর পশ্চিমে। শশাঙ্ক উত্তর ভারত পর্যন্ত নিজের কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন। এই সময় তিনি অঙ্গ ও মগধের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে এক শক্তিশালী প্রশাসন চালু করেন। অন্যদিকে হর্ষ তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসে পুরোদমে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকেন।
হর্ষবর্ধনের শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঙ্গার পূর্ব দিকে এগোলে শশাঙ্ক তাঁর বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যার বিবরণ ইতিহাসে অস্পষ্ট। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক একমত, হর্ষবর্ধন শেষ পর্যন্ত গৌড় জয় করতে পারেননি, অন্তত শশাঙ্ক জীবিত থাকা পর্যন্ত নয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হর্ষবর্ধন মগধসহ অন্যান্য পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হন।
ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এফ. ই. পার্জিটার তাঁর বই দ্য ডাইনাস্টিক হিস্ট্রি অব নর্দান ইন্ডিয়া–তে লিখেছেন, ‘‘শশাঙ্ক ছিলেন সেই সময়ের একমাত্র শাসক যিনি হর্ষবর্ধনের আগ্রাসী সাম্রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।’’
এই দ্বন্দ্বের আরেকটি দিক ছিল রাজনৈতিক জোট ও বিশ্বাসঘাতকতা। হর্ষ শুরুতে শশাঙ্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু পরে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর সেই সম্পর্ক চূড়ান্ত শত্রুতায় রূপ নেয়। এই ধরনের সম্পর্কের গতিবিধি প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে। শশাঙ্ক হর্ষের বিরুদ্ধে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তেমন ফল পাননি। এইসব কূটনৈতিক প্রচেষ্টাও যুদ্ধের ফল নির্ধারণে প্রভাব ফেলেছিল।
শশাঙ্কের মৃত্যু ঘটে আনুমানিক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর গৌড় সাম্রাজ্য দ্রুত ভেঙে পড়ে এবং হর্ষ সেই সুযোগে মগধসহ আরও কিছু এলাকা দখল করেন। কিন্তু হর্ষবর্ধন কখনোই পুরো গৌড় দখল করতে পারেননি। শশাঙ্কের পর তাঁর উত্তরসূরি মানব রাজার আমলেই গৌড়ের পতন শুরু হয়।
ফরাসি ইতিহাসবিদ আন্দ্রে ল্যাম্বার্ট তাঁর গবেষণাপত্রে লিখেছেন, ‘‘শশাঙ্ক ও হর্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছিল শুধুই রাজ্য দখলের যুদ্ধ নয়; এটি ছিল সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রাজনীতির টানাপোড়েনের বহিঃপ্রকাশ। শশাঙ্ক গৌড়কে যা দিয়েছিলেন, তা চিরস্থায়ী না হলেও সেই সময়ের জন্য এক সুদৃঢ় রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে তুলেছিল।’’
এই দ্বন্দ্ব আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস শুধু জয়-পরাজয়ের গল্প নয়, বরং তা বহুস্তর বিশিষ্ট জটিল মানবিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের মিশ্রণ। শশাঙ্ক হয়তো হর্ষবর্ধনের মতো বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেননি, কিন্তু তিনি গৌড়ের প্রথম স্বাধীন রাজা হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। অপরদিকে হর্ষবর্ধন তাঁর কৌশল, সহিষ্ণুতা ও সামরিক দক্ষতায় এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন যা পরবর্তীতে অনেক শাসকের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়।
তাঁদের দ্বন্দ্ব ইতিহাসের পাতায় কেবল যুদ্ধের কাহিনি হয়ে থাকেনি, বরং তা হয়ে উঠেছে এক যুগের প্রতিচ্ছবি—যেখানে ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম, ধর্মের জন্য দ্বন্দ্ব এবং আত্মমর্যাদার জন্য আত্মত্যাগ একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। সেই ইতিহাস আজও গবেষকদের আগ্রহের বিষয় হয়ে রয়ে গেছে, আর আমাদের জন্য তা এক অনন্য শিক্ষার উৎস হয়ে আছে।

এর আগে, গতকাল (শনিবার) বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়।
১৫ ঘণ্টা আগে
আযাদ বলেন, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চান। জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা এবং নির্বাচনী অনিয়মের তদন্তের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন।
১৬ ঘণ্টা আগে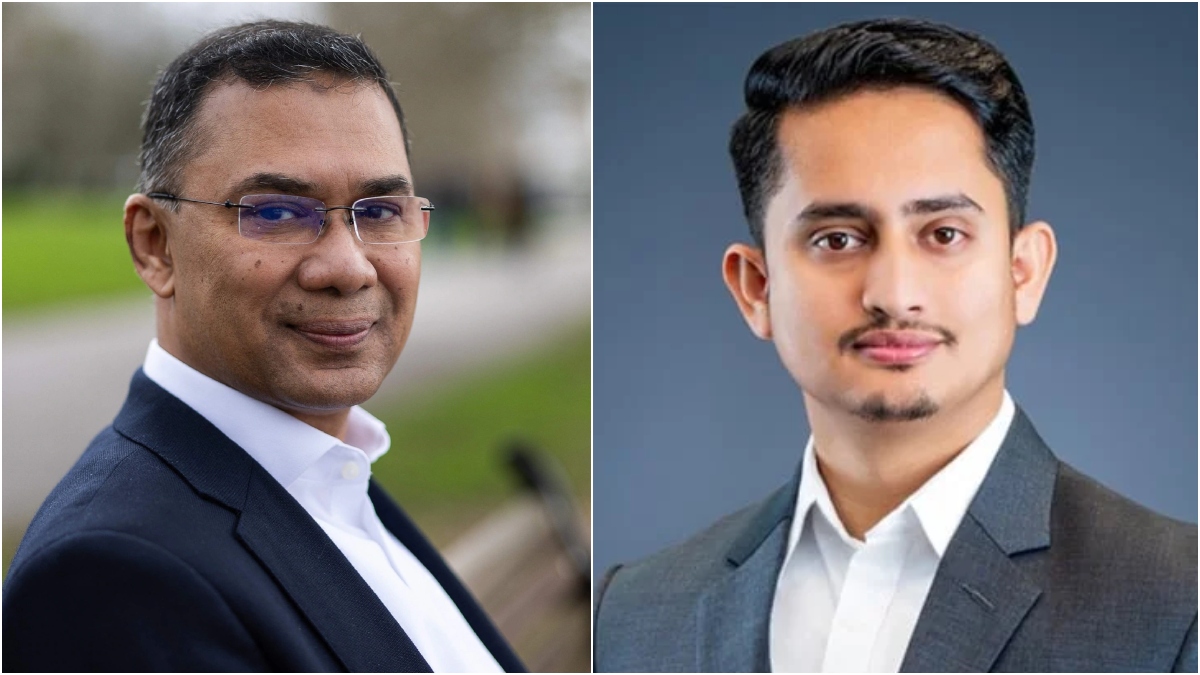
ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।
১৮ ঘণ্টা আগে
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিলুপ্ত হওয়া এ কমিটিগুলোর কোনো নেতাকর্মী যদি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কোনো প্রকার সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তবে তার দায়ভার ছাত্রদল বা যুবদল বহন করবে না।
১৮ ঘণ্টা আগে