
অরুণাভ বিশ্বাস

১৫২৭ সালের ১৭ই মার্চ, উত্তর ভারতের রাজপুতানা প্রান্তে সংঘটিত হয়েছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—খানুয়ার যুদ্ধ। এটি ছিল না শুধু দুই শত্রু পক্ষের মধ্যে একটি সাধারণ যুদ্ধ, বরং এটি ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণকারী এক মোড় ঘোরানো অধ্যায়। এই যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং রাজপুত রাজা রানা সাঙা। কিন্তু কেন হয়েছিল এই যুদ্ধ? কী ছিল পটভূমি? কে জিতেছিল, আর কীভাবে সেই জয় বদলে দিয়েছিল গোটা উপমহাদেশের ইতিহাস? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের যাত্রা আজ খানুয়ার যুদ্ধের দিকে।
যুদ্ধের পটভূমি
১৫২৬ সালের পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবর যখন ভারতে তার পা জমাতে শুরু করলেন, তখন অনেকেই তাকে সাময়িক বিজয়ী বলে ভেবেছিল। বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার ফারগানা অঞ্চলের তৈমুর বংশীয় শাসক, এবং তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর হিসেবেও দাবি করতেন। দিল্লি জয়ের পর তাঁর চোখ ছিল ভারতের গভীরে প্রবেশ করার দিকে। কিন্তু এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাবরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় রাজপুত রাজা রানা সাঙা।
রানা সাঙা ছিলেন মেওয়ার রাজ্যের ক্ষমতাধর শাসক। তিনি শুধু দক্ষ রণকৌশলী ছিলেন। ছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ রাজপুত জোটের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে রাজপুতরা ভেবেছিল, দিল্লির লোদিদের মতো বাবরকেও ভারত থেকে তাড়ানো সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাবরের মতো একজন বিদেশি মুসলিম শাসকের ভারত শাসনের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। ফলে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রবার্ট আরমস্ট্রং লিখেছেন, রানা সাঙা বাবরকে বৈধ শাসক হিসেবে নয়, বরং এক বিদেশি আক্রমণকারী হিসেবে দেখতেন, যাকে আগের তুর্কিদের মতোই তাড়ানো দরকার ছিল।
এই পরিস্থিতিতে বাবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও রানা সাঙার প্রতিরোধ—এই দুই শক্তির সংঘর্ষ ছিল অবধারিত।
যুদ্ধক্ষেত্র খানুয়া
খানুয়ার যুদ্ধ হয়েছিল আগ্রার কাছে খানুয়া নামের এক সমতল অঞ্চলে। এই অঞ্চল ছিল বাবরের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দিল্লি ও আগ্রার মাঝামাঝি এবং রানা সাঙার আগমন পথের কাছাকাছি।
বাবর এই যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করেন মধ্য এশিয়ার ধাঁচের কামান ও অশ্বারোহী সেনা। তিনি গঠন করেন "তুলঘাম" নামের এক বিশেষ যুদ্ধকৌশল, যেখানে মুজরেক কামানের মাধ্যমে শত্রুর র্যাঙ্ক ভেঙে দেওয়া হয়।
বিখ্যাত সামরিক ইতিহাসবিদ স্টিফেন ডেল তাঁর বই, ‘খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের কামান ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধশৈলীতে একটি বড় পরিবর্তন এনে দেয়, যার ফলে প্রচলিত রাজপুতদের ঘোড়সওয়ার আক্রমণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।’
রানা সাঙার বাহিনী ছিল বিশাল—তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য, এবং আরও রাজপুত জাঠ ও আফগান মিত্ররা এই যুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও সংখ্যায় তাঁরা বাবরের বাহিনী থেকে বেশি ছিল, কিন্তু তাঁদের ছিল না বাবরের মতো কামান ও গোলাবারুদের আধুনিক সরঞ্জাম।
যুদ্ধের ফলাফল
১৭ মার্চ, ১৫২৭। সকাল থেকে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রানা সাঙা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু যুদ্ধের মাঝপথে একটি তীর এসে তাঁর চোখে বিদ্ধ হয়। তিনি আহত হয়ে পড়েন, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু কামান ও গুলির আঘাতে রাজপুতদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।
যুদ্ধের শেষদিকে বাবরের বাহিনী জয়ী হয়। রানা সাঙা প্রাণে বেঁচে গেলেও পরাজয়ের গ্লানি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।
ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়নবি মন্তব্য করেন, খানুয়ার পরাজয় শুধু সামরিক নয়, আদর্শগতও ছিল—কারণ এটি রাজপুত ঐক্যের মিথ ভেঙে দিয়েছিল।
যুদ্ধের প্রভাব
খানুয়ার যুদ্ধ ছিল বাবরের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই যুদ্ধের জয় তাঁকে দিল্লি ও আগ্রা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তিনি এই যুদ্ধকে “ইসলামের জন্য জিহাদ” হিসেবে উল্লেখ করেন এবং যুদ্ধশেষে বিজয় উদযাপন করেন।
এ নিয়ে ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক পিটার জ্যাকসন লিখেছেন, ‘বাবরের এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য এক প্রকার ধর্মীয় বৈধতা এনে দেয়, যা পরবর্তী সম্রাটদেরও প্রভাবিত করে, যেমন আকবর ও আওরঙ্গজেব।’
রাজপুতদের দিক থেকে দেখলে, এটি ছিল আত্মবিশ্বাসের এক বিশাল ধাক্কা। রানা সাঙা পরে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেও আর সফল হতে পারেননি। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর সেনাবাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ।
খানুয়ার যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। এটি শুধু বাবর ও রানা সাঙার মধ্যকার সংঘর্ষ নয়, বরং ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির রূপরেখা নির্ধারণকারী এক ঘটনা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি, যা প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ভারত শাসন করবে। আর রাজপুত শক্তির ইতিহাসে এটি ছিল এক বেদনাদায়ক অধ্যায়।

১৫২৭ সালের ১৭ই মার্চ, উত্তর ভারতের রাজপুতানা প্রান্তে সংঘটিত হয়েছিল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—খানুয়ার যুদ্ধ। এটি ছিল না শুধু দুই শত্রু পক্ষের মধ্যে একটি সাধারণ যুদ্ধ, বরং এটি ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণকারী এক মোড় ঘোরানো অধ্যায়। এই যুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর এবং রাজপুত রাজা রানা সাঙা। কিন্তু কেন হয়েছিল এই যুদ্ধ? কী ছিল পটভূমি? কে জিতেছিল, আর কীভাবে সেই জয় বদলে দিয়েছিল গোটা উপমহাদেশের ইতিহাস? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের যাত্রা আজ খানুয়ার যুদ্ধের দিকে।
যুদ্ধের পটভূমি
১৫২৬ সালের পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে বাবর যখন ভারতে তার পা জমাতে শুরু করলেন, তখন অনেকেই তাকে সাময়িক বিজয়ী বলে ভেবেছিল। বাবর ছিলেন মধ্য এশিয়ার ফারগানা অঞ্চলের তৈমুর বংশীয় শাসক, এবং তিনি নিজেকে চেঙ্গিস খানের বংশধর হিসেবেও দাবি করতেন। দিল্লি জয়ের পর তাঁর চোখ ছিল ভারতের গভীরে প্রবেশ করার দিকে। কিন্তু এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বাবরের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় রাজপুত রাজা রানা সাঙা।
রানা সাঙা ছিলেন মেওয়ার রাজ্যের ক্ষমতাধর শাসক। তিনি শুধু দক্ষ রণকৌশলী ছিলেন। ছিলেন এক ঐক্যবদ্ধ রাজপুত জোটের নেতা। তাঁর নেতৃত্বে রাজপুতরা ভেবেছিল, দিল্লির লোদিদের মতো বাবরকেও ভারত থেকে তাড়ানো সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাবরের মতো একজন বিদেশি মুসলিম শাসকের ভারত শাসনের কোনো নৈতিক অধিকার নেই। ফলে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।
বিখ্যাত ইতিহাসবিদ রবার্ট আরমস্ট্রং লিখেছেন, রানা সাঙা বাবরকে বৈধ শাসক হিসেবে নয়, বরং এক বিদেশি আক্রমণকারী হিসেবে দেখতেন, যাকে আগের তুর্কিদের মতোই তাড়ানো দরকার ছিল।
এই পরিস্থিতিতে বাবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও রানা সাঙার প্রতিরোধ—এই দুই শক্তির সংঘর্ষ ছিল অবধারিত।
যুদ্ধক্ষেত্র খানুয়া
খানুয়ার যুদ্ধ হয়েছিল আগ্রার কাছে খানুয়া নামের এক সমতল অঞ্চলে। এই অঞ্চল ছিল বাবরের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি দিল্লি ও আগ্রার মাঝামাঝি এবং রানা সাঙার আগমন পথের কাছাকাছি।
বাবর এই যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। তিনি তাঁর সেনাবাহিনীতে ব্যবহার করেন মধ্য এশিয়ার ধাঁচের কামান ও অশ্বারোহী সেনা। তিনি গঠন করেন "তুলঘাম" নামের এক বিশেষ যুদ্ধকৌশল, যেখানে মুজরেক কামানের মাধ্যমে শত্রুর র্যাঙ্ক ভেঙে দেওয়া হয়।
বিখ্যাত সামরিক ইতিহাসবিদ স্টিফেন ডেল তাঁর বই, ‘খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের কামান ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধশৈলীতে একটি বড় পরিবর্তন এনে দেয়, যার ফলে প্রচলিত রাজপুতদের ঘোড়সওয়ার আক্রমণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।’
রানা সাঙার বাহিনী ছিল বিশাল—তাঁর নেতৃত্বে প্রায় ৮০,০০০ সৈন্য, এবং আরও রাজপুত জাঠ ও আফগান মিত্ররা এই যুদ্ধে অংশ নেয়। যদিও সংখ্যায় তাঁরা বাবরের বাহিনী থেকে বেশি ছিল, কিন্তু তাঁদের ছিল না বাবরের মতো কামান ও গোলাবারুদের আধুনিক সরঞ্জাম।
যুদ্ধের ফলাফল
১৭ মার্চ, ১৫২৭। সকাল থেকে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রানা সাঙা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেন, কিন্তু যুদ্ধের মাঝপথে একটি তীর এসে তাঁর চোখে বিদ্ধ হয়। তিনি আহত হয়ে পড়েন, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু কামান ও গুলির আঘাতে রাজপুতদের ঘোড়সওয়ার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।
যুদ্ধের শেষদিকে বাবরের বাহিনী জয়ী হয়। রানা সাঙা প্রাণে বেঁচে গেলেও পরাজয়ের গ্লানি ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন।
ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়নবি মন্তব্য করেন, খানুয়ার পরাজয় শুধু সামরিক নয়, আদর্শগতও ছিল—কারণ এটি রাজপুত ঐক্যের মিথ ভেঙে দিয়েছিল।
যুদ্ধের প্রভাব
খানুয়ার যুদ্ধ ছিল বাবরের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই যুদ্ধের জয় তাঁকে দিল্লি ও আগ্রা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়। তিনি এই যুদ্ধকে “ইসলামের জন্য জিহাদ” হিসেবে উল্লেখ করেন এবং যুদ্ধশেষে বিজয় উদযাপন করেন।
এ নিয়ে ওক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির গবেষক পিটার জ্যাকসন লিখেছেন, ‘বাবরের এই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করা মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য এক প্রকার ধর্মীয় বৈধতা এনে দেয়, যা পরবর্তী সম্রাটদেরও প্রভাবিত করে, যেমন আকবর ও আওরঙ্গজেব।’
রাজপুতদের দিক থেকে দেখলে, এটি ছিল আত্মবিশ্বাসের এক বিশাল ধাক্কা। রানা সাঙা পরে আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেও আর সফল হতে পারেননি। কিছু ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর সেনাবাহিনীতে বিশ্বাসঘাতকতা ছিল এই পরাজয়ের অন্যতম কারণ।
খানুয়ার যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণ। এটি শুধু বাবর ও রানা সাঙার মধ্যকার সংঘর্ষ নয়, বরং ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতির রূপরেখা নির্ধারণকারী এক ঘটনা। এই যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পেল মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি, যা প্রায় তিন শতাব্দী ধরে ভারত শাসন করবে। আর রাজপুত শক্তির ইতিহাসে এটি ছিল এক বেদনাদায়ক অধ্যায়।
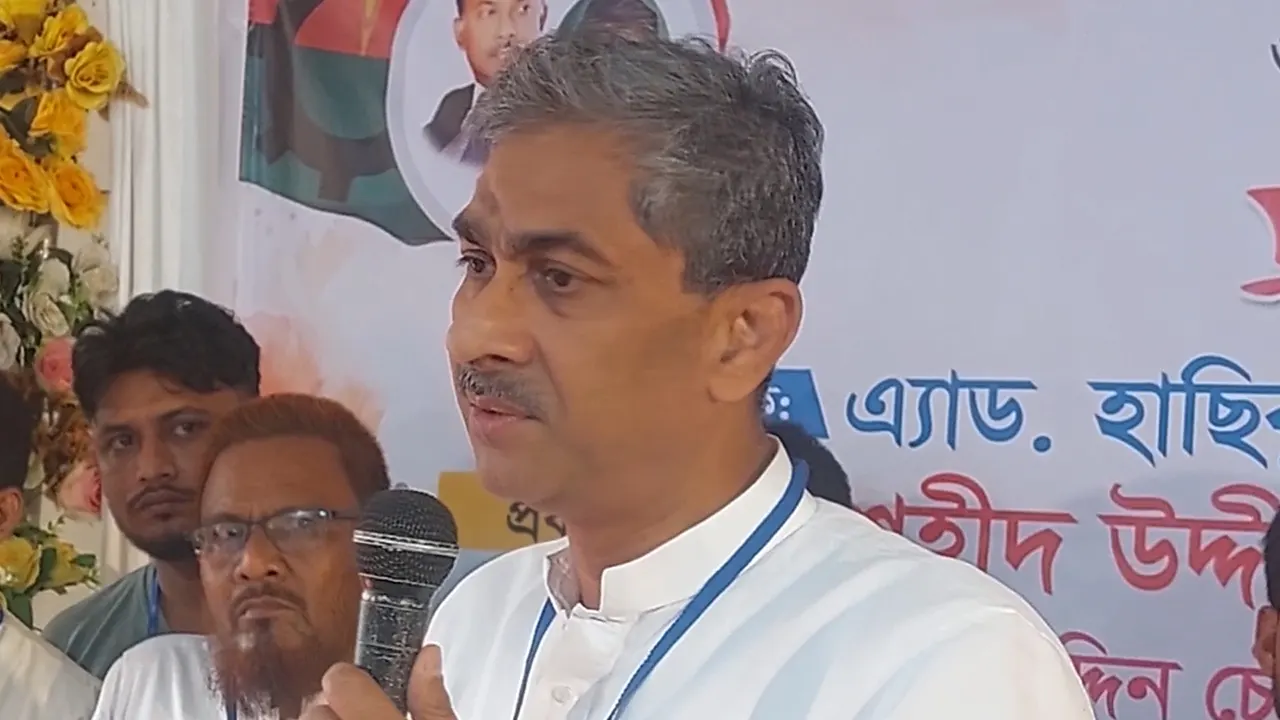
তিনি জানান, টাঙ্গাইল-৫ আসনের সংসদ সদস্য ও বিএনপি'র প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঙ্গে তিনিও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নির্বিঘ্ন করতে সমন্বয় এবং সকল প্রস্তুতি তদরকি করছেন। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে এই নিয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার।
১৭ ঘণ্টা আগে
এর আগে, গতকাল (শনিবার) বিএনপির পক্ষ থেকে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে তারেক রহমানের সাক্ষাতের বিষয়ে জানানো হয়।
১৮ ঘণ্টা আগে
আযাদ বলেন, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে চান। জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষা এবং নির্বাচনী অনিয়মের তদন্তের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন।
১৯ ঘণ্টা আগে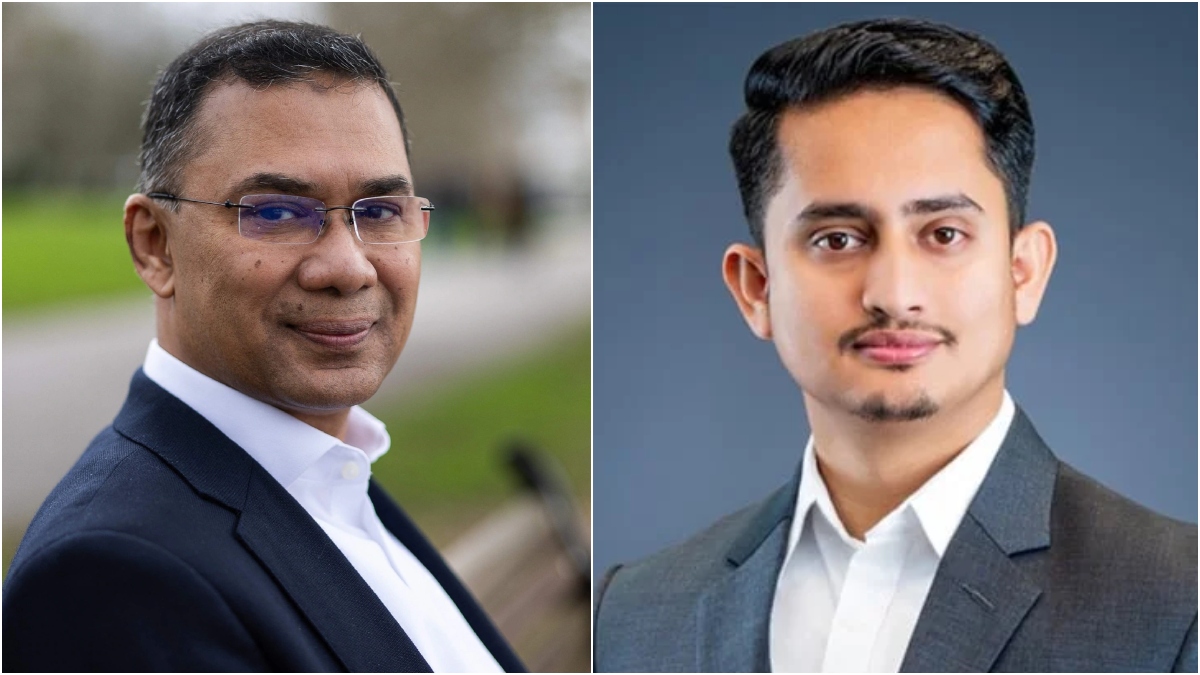
ইতিবাচক রাজনীতির সূচনা করায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম।
২১ ঘণ্টা আগে